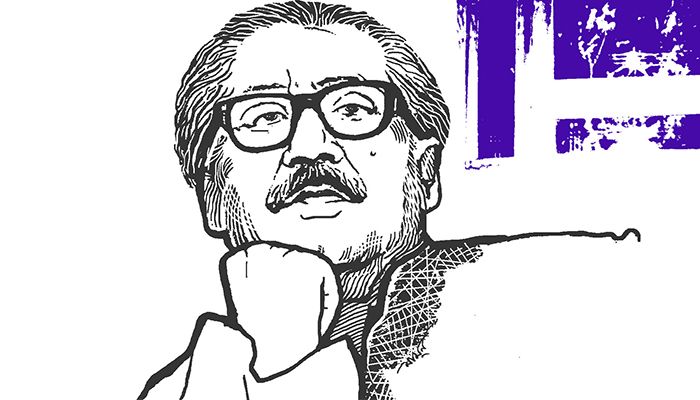
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
প্রকাশ: ২৪ জুন ২০২৪, ০৫:৪২ পিএম
আপডেট: ২৪ জুন ২০২৪, ০৬:৩৮ পিএম
প্রকাশ: ২৪ জুন ২০২৪, ০৫:৪২ পিএম
ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
আপডেট: ২৪ জুন ২০২৪, ০৬:৩৮ পিএম
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে কোনো স্মৃতিচারণ করতে হলে হৃদয়ের গভীরে শুনতে হয়, স্মৃতি তুমি বেদনা; কিন্তু এ তো শুধু বেদনা নয়, বুকের ভেতর এক গভীর ক্ষত থেকে নিয়ত রক্তক্ষরণও বটে। বেদনা দৃশ্যমান কিছু নয়, তা অনুভবের ব্যাপার। তেমনিভাবে এ রক্তক্ষরণও দেখা যায় না; যার এমন রক্তক্ষরণ হয়, অনুভূতি শুধু তার বা তাদের। কাজেই বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি মানেই বেদনা আর রক্তক্ষরণ। বঙ্গবন্ধু তো বাঙালির ইতিহাসে এক বিয়োগান্তক মহানায়কের নাম। কিছু মানুষ নামধারী হায়েনা বঙ্গবন্ধুর জীবন বিয়োগ করে তাদের জীবনে অনেক কিছু যোগ করতে চেয়েছিল।
হ্যাঁ, একুশ বছর তারা তাদের হিসেব অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিয়োগ করেছিল। তবে বাস্তবে কোনোটিই বিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধু আছেন ও থাকবেন আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল; আর বাংলাদেশ তো আজ দীপ্তি ছড়ানো অংশুমান। বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনে এমন বহুবিধ বৈচিত্র্য রয়েছে, তা তুলে ধরাটা অনেক পরিশ্রমসাধ্য এবং বিস্তর গবেষণার দাবিদার। তার এই বৈচিত্র্যের একটি অনুল্লেখিত; কিন্তু খুবই উজ্জ্বল একটি দিক হলো তার বৈশ্বিক শান্তির ভাবনা।
প্রকৃত অর্থে, শান্তির অন্বেষা সর্বজনীন ও সর্বকালীন; কিন্তু তবু সময় সময়ে কিছু মানুষের অবিমৃষ্যকারিতায় মানবিক শান্তি-স্বস্তি বিপন্ন হয়। এমন না হলে জীবনানন্দ দাস কেন লিখবেন, “মানুষ না ভেবে কাজ করে যায় শুধু/ভয়ংকরভাবে অনায়াসে।” তবে কবি যদিও বলেন, মানুষের ভাবনারহিত অনায়াস-কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে বিঘ্নিত শান্তি মানুষকে বিপর্যস্ত করে, তবু আসলে কিছু মানুষের দুর্মতিজনিত চিন্তা ও কর্ম মানবিক অশান্তির কারণ। চেঙ্গিস, হালাকু বা হিটলাররা সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাদের বিধ্বংসী শক্তির ব্যাপকতা বিশ্ববাসীর অজানা নয়।
অবশ্য মানবসৃষ্ট অশান্তির বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে কিছু মানুষের চিন্তা-লেখনী-কর্ম-উদ্যোগ ক্রিয়াশীল থাকার দৃষ্টান্তও বিরল নয়; এবং যাদের তালিকায় বঙ্গবন্ধুও যে থাকবেন তার সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ প্রতুল। বঙ্গবন্ধুর কথায় একটু পরে আসা যেতে পারে। আলোচনা শুরু হতে পারে বঙ্গবন্ধুর পূর্বসূরি (চিন্তা-চেতনার বিচারে) পশ্চিম দুনিয়ার জেরেমী বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) এবং ইমানুয়েল কান্টকে (১৭২৪-১৮০৪) নিয়ে। বেন্থাম ছিলেন ইংরেজ দার্শনিক; আর কান্ট জার্মান দার্শনিক। এ দুজনের দার্শনিক সত্তার অভিন্নতা ছিল শান্তির অন্বেষা। বেন্থাম-এর বই এ প্ল্যান ফর ইউনিভার্সাল অ্যান্ড পারপেচুয়াল পিস (১৭৭৭); এবং কান্ট-এর বই পারপেচুয়াল পিস (১৭৯৫) সংঘাত-প্রবণ ইউরোপের সামনে শান্তির বিকল্প হাজির করেছিল। তবে ইউরোপের কাছে এ দুজনের পথনির্দেশ বাস্তবতার নিরিখে স্বপ্নবিলাসের বেশি কিছু মনে হয়নি। ফলে উধাও শান্তির ইউরোপ অবলীলাক্রমে দুটো মহাসময়ের কাছে সমর্পিত হয়েছিল; কিন্তু বিদগ্ধ জনের কাছে স্বীকৃত ও সর্বজনগ্রাহ্য সত্য হলো, বেন্থাম ও কান্ট-এর শান্তি-স্বপ্ন অমর। কারণ এমন স্বপ্নের মৃত্যু নেই; কমতি নেই এমন স্বপ্নের স্বাপ্নিকের। বঙ্গবন্ধুও ছিলেন এমন শান্তি- স্বাপ্নিক। তার কথা ও কাজ তার শান্তি অন্বেষার প্রমাণ। তার জনগণলগ্ন রাজনীতির উৎসারণ হয়েছিল আর্তমানবতার প্রতি সেবামূলক প্রণোদনা থেকে। বঙ্গবন্ধুর শান্তির সংজ্ঞায়ন হয়েছিল মানুষের মানবিক পরিস্থিতি থেকে, অবিঘ্নিত মানবিকতা থেকে। শোষণ-বঞ্চনায় বিপন্ন মানুষ তাই বরাবরই তার লক্ষ্যবস্তু ছিল। তবে তার শান্তির অন্বেষা শুধু দেশের গণ্ডিতে নয়, বরং তা বিস্তৃত ছিল বিশ্বজুড়েই। ভাবতে অসুবিধা হয় না বঙ্গবন্ধু তার বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে একটি পাটাতন হিসেবে ব্যবহার করে এবং সে পাটাতনে দাঁড়িয়ে দেশে শান্তির কর্ম করেছেন, আর বিশ্বে শান্তির বাণী ছড়িয়েছেন। তবে শুধু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে নয়; ৭১-এর আগেও বাঙালি রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবের কণ্ঠেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্ববাসী শুনেছে শান্তির জোরালো বার্তা।
বঙ্গবন্ধুর বিশ্বশান্তির বার্তা উৎকীর্ণ ছিল ৭২-এর সংবিধান এবং নয়টি ভাষণ ও একটি বার্তায়। এ ছাড়া আমার দেখা নয়াচীন (২০২০) বইতে পিকিং (সে সময়ের নাম) এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনে (১৯৫২) বঙ্গবন্ধুর বিশ্বশান্তির-ধারণার তথ্য আছে। ৫৬-তে স্টকহোম শান্তি সম্মেলনে যোগ দেয়া এবং এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য কী ছিল তা জানার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুপস্থিত। তবুও বঙ্গবন্ধুর শান্তি ও বিশ্বশান্তি ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট।
১. বাংলাদেশের সংবিধান ও বিশ্বশান্তি
বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত ও বাস্তবায়িত হওয়ার পর মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া মন্তব্য করেছিল, “১৯৭২-এ বাংলাদেশের সংবিধান যখন অনুমোদিত হয় তখন এটি সমকালীন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সংবিধান যা আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে সংগ্রামরত তৃতীয় দুনিয়ার জনগণের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আকাক্সক্ষার অনুপ্রেরণা হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ ও আইনের ইতিহাস প্রণেতাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল।”১ স্বীকৃত সত্য যে, এ সংবিধানে উৎকীর্ণ সব শব্দ-বাক্যের প্রেরণামূলক দিকনির্দেশনার উৎস ছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। তার জীবন ও রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের (তার ভৌগোলিক পরিচয় যা-ই হোক না কেন) মুক্তি, স্বস্তি ও শান্তি;, আর তা রূপায়ণের রূপরেখা ছিল এ সংবিধান।২
৭২-এর সংবিধানের প্রাসঙ্গিক ২৫নং ধারার শিরোনাম “আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন”। ধারাটির সূচনা-বক্তব্য, “জাতীয় সার্বভৌমত্বও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শাস্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত-নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সব নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র
(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;
(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং
(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।”৩
উপর্যুক্ত সাংবিধানিক ধারা সম্পর্কে মন্তব্য চারটি প্রাসঙ্গিক। এক. বিশ্বশান্তির মৌল পূর্বশর্তসমূহ অনুপুঙ্খভাবে নির্দেশিত হয়েছে। দুই. বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংকট/সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের মূলনীতি যে অনুসরণীয় হবে তা বাংলাদেশ স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে সব রাষ্ট্রকে তা করার প্রণোদনা সৃষ্টি করা হয়েছে। তিন. সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ অস্ত্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংঘাতের গোড়ার কথা বলেছে। বাস্তবে নিরস্ত্রীকরণের নামে বৈষম্যমূলক অস্ত্র সীমিতকরণের উদ্যোগ দৃশ্যমান, যা যথার্থ বিশ্বশান্তিকে সুদূরপরাহত করে। চার. চূড়ান্তভাবে বলা যায়, ধারাটি বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ-অশান্ত পৃথিবীর জন্যে বিবেকী দিকনির্দেশনা ছিল। বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও সজ্ঞার আনুপূর্বিক প্রতিফলন ধারাটি। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর বিশ্বশান্তি-ভাবনা প্রক্ষেপণের পাটাতন যে ছিল বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি তার প্রমাণ এ ধারা। এটাও উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের নৈতিক অবস্থান যে শান্তিপূর্ণ তার-ও সূচক এ ২৫নং ধারা। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র নির্দেশ করলেন এভাবে, “সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বৈরিতা নয়।” বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয়তার মন্ত্র ছিল এটি। অবশ্য বিশ্বশান্তি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু-ভাবনার ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে তার ভাষণে, সে কথায় পরে আসছি।
২. আন্তর্জাতিক সামাজিক শান্তি
বঙ্গবন্ধুর শান্তি-ধারণার সামূহিক বিন্যাসের শ্রেণীকরণ করা যায়; এবং যার শুরুতে থাকতে পারে আন্তর্জাতিক সামাজিক শান্তির প্রসঙ্গ। আলজিয়ার্স ভাষণ এবং মস্কো সম্মেলনে প্রেরিত বার্তায় প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বশান্তির অন্যান্য প্রসঙ্গ ছিল, যা যথাস্থানে আলোচিত হবে। ৫-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন। ওই সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে বিশ্ব সমাজব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছিলেন, “বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত-শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।” প্রধানত পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত বিশ্বে শোষক-শোষিতভিত্তিক বৈষম্য সামাজিক বাস্তবতা; আর এমন বাস্তব সত্যের প্রতিধ্বনি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তবে এ বৈষম্য নিরসনে অনিবার্য সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান যে শোষিতের পক্ষে, এমন উক্তি ছিল বোধগম্য কারণে বেশ সাহসী প্রণোদনামূলক। কারণ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশ স্বাধীন বাংলাদেশ, আর সে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও নেতার মুখে এমন উচ্চারণ সাহসের ব্যাপার ছিল বটে! অবশ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামী অতীত, এবং সে সংগ্রামে স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এমন বক্তব্যের পটভূমি নির্মাণ করেছিল।
২৫ থেকে ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩ মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব পিস ফোর্সেস। উক্ত সম্মেলনে পাঠানো বাণীতে তিনি বলেছিলেন, “At a time when people in different parts of the world are struggling against imperialism, colonialism and racialism and are striving for political and economic emancipation, such a Congress cannot but strengthen and inspire all those committed to the cause of world peace. The oppressed people of the world must liberate themselves from exploitation and man’s injustice to man must end if the world is to enjoy a stable peace.”৪
আলজিয়ার্সে দেয়া ভাষণের উদ্ধৃত অংশ এবং উপর্যুক্ত বার্তার অন্তর্নিহিত বিষয় অভিন্ন-মানুষের ওপর মানুষের শোষণের অবসান, যা কি না সামাজিক তথা বিশ্বশান্তির প্রধান পূবশর্ত। উল্লেখ্য, মানুষের শোষণ, বঞ্চনা আর বৈষম্য অপরিবর্তিত রেখে বিশ্বশান্তির যে কোনো বয়ান যে অর্থহীন, তা বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তার এমন, দ্ব্যর্থহীন জোরালো বক্তব্য ছিল। অত্যুক্তি হবে না এমন বললে যে, এমন উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির সামাজিক ফর্মুলা নির্দেশ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, যা অবশ্য বিশ্বব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ ছিল। এমন উচ্চারণ নিহিত বার্তা স্বপ্নবিলাসী মনে হলেও তা ছিল বাস্তব প্রয়োজনসম্পৃক্ত; আর সেখানেই বঙ্গবন্ধুর অনন্য ও লক্ষণীয় কৃতিত্ব। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিশ্বশান্তির প্রণোদনা তার মনন ও চেতনার গভীরে প্রোথিত ছিল।
৩. বিশ্বশান্তি
বিশ্বশান্তির মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “আমার মতে, ভাত-কাপড় পাবার ও আদায় করে নেবার অধিকার মানুষের থাকবে, সাথে নিজের মতবাদ প্রচার করার অধিকারও মানুষের থাকা চাই। তা না হলে মানুষের জীবন বোধ হয় পাথরের মতো শুষ্ক হয়ে যায়।”৫
২-১২ অক্টোবর ১৯৫২, চীনের পিকিংয়ে (তখনকার নাম) এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩৭টি দেশ এ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এ সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৫৪-তে কারাবন্দি হিসেবে তিনি লেখেন অনেকটা স্মৃতিনির্ভর (কিছু নোটস ছিল) আমার দেখা নয়াচীন শীর্ষক একটি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনামূলক ভ্রমণ কাহিনি। তার চোখে বিপ্লবোত্তর চীনের সামগ্রিক অবস্থা বইটির বিষয়বস্তু। প্রাসঙ্গিকভাবে শুরুতেই আছে বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর জবানি। দীর্ঘ হলেও চমৎকার প্রাসঙ্গিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তার কথাগুলো উদ্ধৃত হচ্ছে
... দুনিয়ায় আজ যারাই শান্তি চায় তাদের সম্মেলনে আমরা যোগদান করতে রাজি। রাশিয়া হউক, আমেরিকা হউক, ব্রিটেন হউক, চীন হউক যে-ই শান্তির জন্য সংগ্রাম করবে তাদের সাথে আমরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে রাজি আছি, ‘আমরা শান্তি চাই।’ কারণ যুদ্ধে দুনিয়ার যে ক্ষতি হয় তা আমরা জানি ও উপলব্ধি করতে পারি; বিশেষ করে আমার দেশে-যে দেশকে পরের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। যে দেশের মানুষ না খেয়ে মরে, সামান্য দরকারি জিনিস জোগাড় করতে যাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সে দেশে যুদ্ধে যে কতখানি ক্ষতি হয় তা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে করলেই বুঝতে পারবেন কোথায় ইংরেজ যুদ্ধ করছে, আর তার জন্য আমার দেশের ৪০ লক্ষ লোক শৃগাল কুকুরের মতো না খেয়ে মরেছে। তবুও আপনারা বলবেন, আজ তো স্বাধীন হয়েছি। কথা সত্য, ‘পাকিস্তান’ নামটা পেয়েছি; আর কতটুকু স্বাধীন হয়েছি আপনারা নিজের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। যাহা হউক, পাকিস্তান গরিব দেশ, যুদ্ধ চাইতে পারে না। যুদ্ধ হলে পাকিস্তানের জনগণের সকলের চেয়ে বেশি কষ্ট হবে এই জন্য। ... তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য, পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য-যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।৬
উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে শান্তির ধারণা পোষণ করেছেন; যদিও শান্তি-গবেষকদের ধারণা ভিন্নধর্মী। তাদের কথা হলো, শান্তি ইতিবাচক ও নেতিবাচক হতে পারে। ইতিবাচক শান্তি স্বস্তিদায়ক সামগ্রিক মানবিক পরিবেশ নিশ্চিত করে যুদ্ধের আশঙ্কা ক্ষীণ করে। অন্যদিকে শুধু সংঘাত-সংঘর্ষ-যুদ্ধহীন পরিবেশ নেতিবাচক শান্তির যুদ্ধহীন পরিবেশ নেতিবাচক শান্তির দৃষ্টান্ত।৭ বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধু যুদ্ধহীন শান্তির কথা বলে আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক শান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু একই সমান্তরালে তিনি যখন যুদ্ধের কারণে আমজনতার বিপন্ন নৈমিত্তিক জীবনের কথা বলেন তখন নিঃসন্দেহে ইতিবাচক শান্তির প্রসঙ্গ উঠে আসে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণে
তৃতীয় বিশ্বের মানুষের যে নাভিশ্বাস, তার কথাও উপস্থিত এ শান্তি-ধারণায়। উপরন্তু আছে নয়াউপনিবেশবাদী বিশ্বব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের বিপন্নতার কথা। অর্থাৎ বলা চলে, বঙ্গবন্ধুর শান্তি-ধারণা ছিল সামূহিক ও সামগ্রিক।
তবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পাটাতন থেকে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বশান্তির বাণী প্রথম শ্রুত হয় জুলিও কুরি পদকপ্রাপ্তির অনুষ্ঠানে। ৭২-এর ১০ অক্টোবর হেলসিংকিতে এক ঘোষণায় দেশের নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষ তথা বিশ্বশান্তিতে বিশেষ অবদানের জন্যে বঙ্গবন্ধুকে এ পদক দেয়ার কথা ঘোষণা করে। অবশ্য ৭৩-এর ২৩ মে ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে করে বঙ্গবন্ধুকে পদক দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্যে বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করেন।৮ বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববন্ধু অভিধার যথার্থতার সপক্ষে তার একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, যা তিনি নোটবইতে লিখেছিলেন ৩০ মে ১৯৭৩, “একজন মানুষ হিসেবে আমি গোটা মানবজাতি নিয়েই চিন্তিত। একজন বাঙালি হিসেবে বাঙালিদের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। আমার এই নিরন্তর সম্পৃক্ততার পেছনে রয়েছে ভালোবাসা, চিরদিনের ভালোবাসা, এই ভালোবাসা আমার রাজনীতি ও অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।” মূল বক্তব্য ইংরেজিতে ছিল বিধায় তা-ও উদ্ধৃত করা যুক্তিসঙ্গত: “As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengalee, I am deeply involved in all that concerns Bengalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being.”
পদক গ্রহণ করার সময়ে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে বাংলাদেশভিত্তিক শান্তি-ধারণা পরিস্ফুট হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “বাংলাদেশের মানুষের কাছে শান্তি আর স্বাধীনতা একাকার হয়ে মিশে আছে। আমরা মর্মে মর্মে অনুধাবন করি বিশ্বশান্তি এবং আঞ্চলিক শান্তির অপরিহার্যতা।” উপরন্তু এমন দৈশিক চেতনার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল আপন ভাবনা : “একই সঙ্গে এটাও আমি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই, বিশ্বশান্তি আমার জীবনদর্শনের মূলনীতি। নিপীড়িত, শোষিত, শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, যে কোনো স্থানেই হোক না কেন, ওদের সাথে আমি রয়েছি।” বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ছিল, “আমরা চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক। বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে আগ্রাসী নীতির অনুসারী কতিপয় মহাশক্তির অস্ত্রসজ্জা তথা অস্ত্র প্রতিযোগিতার পর আজ এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা চাই, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত অর্থ দুনিয়ার দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করা হোক। তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুছে ফেলার কাজ অনেক সহজ সাধ্য হবে। ... আমরা সমর্থন জানাই বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও মানব কল্যাণের যে কোনো মহৎ প্রচেষ্টাকে।” প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গবন্ধু ভুলে যাননি ঘরের কাছে আঞ্চলিক শান্তির কথা। সে জন্যে খোলামেলা পাকিস্তানকে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির প্রতিবন্ধক হিসেবে বর্ণনা করে বলেছিলেন, “... পাকিস্তানের একগুঁয়ে নীতি উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ আবার নতুন করে পাকিস্তানকে সজ্জিত করে চলেছেন নতুন নতুন সমরাস্ত্রে। নিঃসন্দেহে এটা স্থায়ী যে কোনো শুভ উদ্যোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।”৯ উল্লেখ্য, নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ শান্তির প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ৭৩-এর ৩ জানুয়ারি ভিয়েতনাম অস্ত্রবিরতিকে স্বাগত জানিয়েছিল। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এ উদ্যোগ শুধু ভিয়েতনামেই নয়, বরং গোটা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় স্থায়ী শান্তির পথ সুগম করবে। অর্থাৎ শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বব্যাপি শান্তির জন্যে উদগ্রীব ছিল।
৭৩-এর জুলাই মাসে যুগোস্লোভিয়া সফরের সময়ে বঙ্গবন্ধু ও প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর যৌথ ইশতেহারে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার শান্তি প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানানো হয়েছিল; বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছিল লাওস ও ভিয়েতনামের জনগণের আত্ম-অধিকারের (self-determination) কথা। উপরন্তু মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২নং প্রস্তাবের (২২ নভেম্বর ১৯৬৭) গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
৭৩-এর ২-৩ আগস্ট কানাডায় অনুষ্ঠিত হয় কমনওয়েল্থ সরকার প্রধানদের সম্মেলন। এ সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধু বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা আর শান্তিতে বসবাস করার মধ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধান অভিন্ন স্বার্থ নিহিত আছে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা মানবজাতির জন্য হুমকি, যার মধ্যে শুধু সামগ্রিক ধ্বংস নয়, বরং বিশ্বসম্পদের ব্যাপক অপচয়ের হুমকি নিহিত আছে।” সুতরাং এমন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর শাণিত প্রশ্ন ছিল, “আমরা কি এমন কিছু করতে পারি না যাতে অস্ত্র প্রতিযোগিতার সম্পদ মানুষের কষ্ট লাঘব ও তাদের কল্যাণে স্থানান্তরিত করতে পারি? আমরা কি কমনওয়েল্থভুক্ত দেশগুলো চলমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং পারমাণবিক পরীক্ষার মাধ্যমে বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পারি না?”১০ অত্যুক্তির ঝুঁকি নিয়েও বলা যায়, এমন সম্মেলনে লোকরঞ্জক পারস্পরিক প্রীতি ও বচন বিনিময়ের বাইরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাস্তবসম্মত কিছু করণীয় নির্দেশ করেছিলেন। আমরা জানি কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তবুও শান্তির বাস্তবসম্মত বাণী শোনানোর ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর জন্যে ইতিহাস-নির্দিষ্ট স্থানটি নিশ্চিত হয়েছিল।
৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৪র্থ জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন। শোষক- শোষিত সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ-ঘোষণা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিবেক আন্দোলিত করা এ ভাষণের পর কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, “মুজিব, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত বিশ্বের এই বাঁচার সংগ্রাম আমারও সংগ্রাম।”১১ ভাষণের মূল অংশে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল, “শহীদদের [বাংলাদেশের] নামে শপথ করে বলছি যে, বাংলাদেশ সব সময় আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার যে মানুষগুলো জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত তাদেরকে সমর্থন দেবে।” প্রস্তাবনার অংশে বঙ্গবন্ধুর শান্তি-কৌশলের (strategy of peace) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অর্থাৎ শান্তির সুললিত বাণীই শুধু নয়, তা অর্জনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা উচিত-সে কথাটিই বঙ্গবন্ধু জোরালোভাবে বলেন। একই সমান্তরালে তার পুনরুক্তি ছিল, অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে এবং পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে।
শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘ ভাষণে বিশ্বশান্তি সম্পর্কে তার সামগ্রিক ধারণা ও প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪-এর ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণটি ছিল বাংলায়। রবীন্দ্রনাথের পর বঙ্গবন্ধুই প্রথম বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষার সমাদর করলেন। অবশ্য ৫২-তেও পিকিং এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন।১২
এ ভাষণ বিশ্বশান্তি সম্পর্কে অন্তত পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। প্রথমত, বিশ্বশান্তি সম্পর্কে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের নীতি-অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে। “বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম হইতেছে সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম। সেজন্যই জন্মলগ্ন হইতে বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পাশে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। ... আগ্রাসনের মাধ্যমে বেইনিভাবে ভূখণ্ড দখল, জনগণের অধিকার হরণের জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার” ইত্যাদির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান যে স্পষ্ট তা উল্লেখিত হয়। আরও উল্লেখিত হয় আলজিরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউর সফল সংগ্রামের কথা। “বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব-এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ... এই জন্য সমঝোতায় আগ্রহী, উত্তেজনা, প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকাসহ বিশ্বের যে কোনো অংশে যে কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই।”
তবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের চমকপ্রদ দিকটি ছিল জাতিসংঘকে একটি নয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো। তার দিকনির্দেশক বক্তব্যটি ছিল।
এ ধরনের ব্যবস্থায় শুধু নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করাই নয়, ইহাতে একটি স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি।
তৃতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির কথাও বলা হয়েছিল। যেমন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশের আপোষ-মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তির কাঠামো এবং দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ইহা ছাড়া আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।”
একাত্তর পরবর্তী-সময়ে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান এ উপমহাদেশে সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তঃসম্পর্কে নজির তৈরি করেছিল; কিন্তু সমস্যা ছিল পাকিস্তানকে নিয়ে। ভারত ও পাকিস্তান সাতচল্লিশের পর থেকেই বৈরী; কিন্তু একাত্তরের পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আন্তঃসম্পর্কের টানাপড়েন উপমহাদেশে শান্তির জন্যে অশনি সংকেত ছিল। এ সংকট নিরসনে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছিলেন, “পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি।” এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল, “আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষায় সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।”
চতুর্থত, এবং দক্ষিণ এশিয়ার সমান্তরালে “আমরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রতিও সমর্থন জানাই।” পঞ্চমত, “... আমরা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে শান্তি এলাকার ধারণা, যাহা এই পরিষদ অনুমোদন করিয়াছে, তাহাকে সমর্থন করি।”১৩
বঙ্গবন্ধু এ ভাষণের সমাপ্তি টেনেছিলেন অনেকটা যেন রাবীন্দ্রিক ঢংয়ে। “জনাব সভাপতি, মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই।” (রবীন্দ্রনাথের উক্তি ছিল, “মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ”)। সমাপনী বক্তব্যের শেষ দিকে বলা হয়েছিল, ‘আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে।” (রবীন্দ্রনাথের পঙ্ক্তি ছিল, “আপনা মাঝে শক্তি ধরো/নিজেরে করো জয়।”)
বঙ্গবন্ধুর জীবনে শেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ছিল জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে অনুষ্ঠিত ২০তম কমনওয়েলথ শীর্ষ বৈঠক। ২৬ এপ্রিল-৩ মে ১৯৭৫ অনুষ্ঠিত সম্মেলনটি ছিল বেশ দীর্ঘ। সুতরাং বঙ্গবন্ধু বেশ সময় নিয়ে বিস্তৃত করে শান্তির বার্তা ৩৩টি দেশের প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। তিনটি ভাষণে (২৮ এপ্রিল, ২ মে এবং ৩ মে) তিনি প্রধানত শান্তির পূর্বশর্ত হিসেবে দারিদ্র্য নিরসন ও উন্নয়নকে চিহ্নিত করেছিলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ যথার্থ ও বাস্তবমুখী।
প্রথম ভাষণে বক্তব্য ছিল মোট চারটি এক, ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য কমানোর জন্যে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকল্প নেই। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু বিষয়টি প্রথম অবতারণা করেছিলেন তার জাতিসংঘ ভাষণে। দুই. কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর পারস্পরিক সহায়তায় পল্লী উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দরিদ্র-বান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের তাগিদ। তিন. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক সংক্রান্ত। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হবে উন্নত দেশ (কমনওয়েলথভুক্ত) বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্যে পূঁজির জোগান দেয়া। চার. দারিদ্র নিরসন ও উন্নয়ন নিশ্চিত কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
দ্বিতীয় ভাষণের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল “বিশ্ববাণিজ্য ও উন্নয়ন”। অন্তর্নিহিত প্রসঙ্গ ছিল সারা বিশ্বের জন্যে বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব ছিল, উপযুক্ত কাঠামো তৈরি করে সম্পদ ও মানবসম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ প্রসঙ্গে তিনি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুনরুক্তি করেন। তিনি বেশ জোরালোভাবেই এ ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন।
তৃতীয় বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু প্রধানত দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি সংক্রান্ত পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরেন, বিশেষ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে গৃহীত উদ্যোগের ফিরিস্তি দেন। এ প্রসঙ্গে তার সমাপনী বক্তব্য ছিল, “As we believe that the interests of our people [in the subcontinent] are guaranteed at the maximum in this way.”
এ ভাষণে দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, সারা বিশ্বে শান্তি-বিঘ্নিত স্থানসমূহে মানুষের বিপন্নতা। এশিয়া ও আফ্রিকায় এমন মানুষগুলোর সংগ্রামের সাফল্যের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। উপরন্তু ভারত সহাসাগর ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শান্তির এলাকার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়।১৪
৪. দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শান্তি
সংকট ও সংঘাতপ্রবণ দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা কাঠামো হিসেবে সার্কের অভ্যুয়দয় (১৯৮৫) এক ধরনের বিমুগ্ধ বিস্ময় ছিল, অন্তত তাদের কাছে যারা অঞ্চলটি পর্যবেক্ষণ করতেন, গবেষণা করতেন এবং লিখতেন। বলা হয়, দক্ষিণ এশীয় শান্তির লক্ষ্যে সার্ক এ অঞ্চলের জন্যে প্রথম আশীর্বাদ (অবশ্য পরবর্তীকালে সার্ক নিয়ে আশাভঙ্গের অনেক কারণ ঘটেছে)। সার্কের দ্রষ্টা ও স্বাপ্নিক হিসেবে বঙ্গবন্ধু অগ্রগণ্য (যদিও তা স্বীকৃত হয় না)। ৭২-এর ৬ মার্চ ইন্দিরা গান্ধী আয়োজিত ভোজসভায় দেয়া ভাষণে (কলকাতা) বঙ্গবন্ধু কলেছিলেন, “প্রতিবেশীদের মধ্যে সংঘাতের বন্ধ্যা নীতির চিরতরে অবসান ঘটুক। আমাদের উচিত নয় আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয় করা, আমাদের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে যা ব্যবহার করা উচিত।”১৫ অন্যদিকে ৭৪-এর ৪ মার্চ কুমিল্লার দাউদকান্দিতে একটি জনসভায় তিনি বলেছিলেন, “এ উপমহাদেশে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা-আমরা শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমরা কারও সঙ্গে কোনো বিবাদে লিপ্ত হতে চাই না। আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চাই। আমাদের ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করুক তা আমি চাই না; আমরা অপরের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাই না।”১৬ বলা বাহুল্য সার্ক নামের আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত প্রণোদনার কথা বলা হয়েছিল উপর্যুক্ত দুটো ভাষণে।
ভারত মহাসাগর শান্তির এলাকার সপক্ষে বঙ্গবন্ধু তার জাতিসংঘ ভাষণে বাংলাদেশের দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত প্রয়োজন।১৭ ৭১-এ সাধারণ পরিষদে শ্রীলঙ্কা প্রস্তাবটি পেশ করে, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাব অনুসারে ভারত সহাসাগর অঞ্চলে একটি শান্তির এলাকা গঠনের কথা বলা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু বাইরের শক্তিসমূহের সামরিক উপস্থিতি-মুক্ত শান্তির এলাকার কথা বলা হলেও কালক্রমে স্থানীয় সামরিক শক্তির হুমকি থেকে মুক্ত শান্তির এলাকা ধারণাও সংযোজিত হয়েছিল। পরবর্তী বেশ ক’বছর সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি নিয়ে নিয়মিত আলোচিত হয়, এক পর্যায়ে প্রস্তাবটি উধাও হয়। বোধগম্য, বড় শক্তির (যাদের দ্বারা জাতিসংঘ প্রভাবিত ও পরিচালিত) স্বার্থের প্রতিকূলে থাকার কারণে প্রস্তাবটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি অবধারিত ছিল; এবং যার মাধ্যমে প্রথম ও তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থের আন্তঃসংঘাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। উল্লেখ্য, প্রস্তাবক রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা তৃতীয় বিশ্বের। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় মার্কিন ও সোভিয়েত পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত নৌবহরের ভয়াবহ উপস্থিতি থেকে বাংলাদেশ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তার প্রেক্ষাপটে দেশটি গোড়া থেকেই প্রস্তাবটি সমর্থন করতে শুরু করে। উপরন্তু বাংলাদেশ সংবিধানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি বাংলাদেশের নীতি-অবস্থানের কথা বলা আছে।১৮
ভারত মহাসাগরে শান্তির এলাকা সংক্রান্ত বাংলাদেশের প্রথম বক্তব্য উচ্চারিত হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফর শেষে
৭২-এর মার্চ মাসে প্রচারিত যৌথ ইশতেহারে। বলা হয়েছিল, “ভারত মহাসাগর এলাকা বড় শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সামরিক প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে;” এবং “এ এলাকায় সামরিক, বিমান ও নৌঘাঁটি নির্মাণের বিরোধিতা করা হবে।” উপরন্তু জাতিসংঘ-প্রস্তাবের দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য, বিশ্বশান্তির সপক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার ক্ষেত্রে ২৩ মে ১৯৭৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলন ও বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদান বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।
৭৩-এ মার্কিন রণতরী ‘হ্যানকক’ ভারত মহাসাগরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেলে বাংলাদেশের পররাষ্টমন্ত্রী এ এলাকায় মার্কিন দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সমালোচনামুখর হন। সে সময়ে ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, “The exercise of the American naval ships is evidently a great threat to the safety and sovereignty of all countries, including Bangladesh, along the Indian Ocean coast. By such provocation, the United States desires to reduce the Indian Ocean into such a dreadful pit of big power rivalry that might pose great challenges to our peaceful ambitions, regional integrity and nonaligned foreign policy.” একই প্রেক্ষাপটে ভারত সহাসাগরে মার্কিন নৌঘাঁটি দিয়েগো গার্সিয়া (Diego Garcia) বাংলাদেশের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। স্বয়ং বঙ্গবন্ধু উষ্মার সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, “যারা বিশ্বশান্তির কথা বলে তারাই এমন একটি এলাকায় সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছে যা শান্তির এলাকা হিসেবে গড়ে ওঠা উচিত।” ৭৪-এর মে মাসে পররাষ্ট্র্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের মস্কো সফর শেষে প্রকাশিত ইশতেহারে ঢাকা ও মস্কো ভারত মহাসাগর শান্তির এলাকা প্রস্তাব বাস্তবায়নে যৌথ ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।
ভারত মহাসাগর শান্তির এলাকা প্রস্তাব কাঠামোর আওতায়, বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের জন্যে আরও একটি প্রস্তাব পাকিস্তান ৭৪-এ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করে। প্রস্তাবটির নাম ছিল দক্ষিণ এশীয় পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা (South Asian Nuclear Weapon Free Zone)। প্রস্তাবটির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের পারমাণবিক প্রকল্প; সে কারণে ভারতের বিরোধিতা অনিবার্য ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের জন্যে বিষয়টি ছিল বেশ অস্বস্তিকর। একদিকে ভারত-বিরোধিতা অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল; অন্যদিকে বাংলাদেশের নীতি-অবস্থান ছিল শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, সারা বিশ্বে পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে। বলা যায়, বাংলাদেশ ছিল উভয় সঙ্কটে। সুতরাং বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত থেকে কৌশলমূলক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের সামনে বিকল্প কিছু ছিল না। অবশ্য ভারত মহাসাগরে শান্তির এলাকা সংক্রান্ত মূল প্রস্তাবের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন অব্যাহত থাকে।
সমাপনী বক্তব্য
বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল তৃতীয় বিশ্বের যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং সীমিত সম্পদের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে। সুতরাং আদর্শ ও বাস্তবতা মিলিয়ে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর প্রণোদনায় জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে, যা কি না আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির নামান্তর ছিল। উপরন্তু বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা-উৎসারিত উপলব্ধ সত্যের অনিবার্য প্রতিফলন ছিল তার শান্তি-অন্বেষায়। উল্লেখ্য, জাতিসংঘে ভাষণের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাইবে এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।” লক্ষণীয়, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মানুষের জন্যে শান্তি অপরিহার্য মনে করেছিলেন, তার দ্যোতনা সারা বিশ্বের সব মানুষের জন্যে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। আর সে কারণে আরও লক্ষণীয় যে, তিনি আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তির সীমিত পরিসর অতিক্রম করে মানুষের শান্তির কথা বলেছিলেন। তিনি যথার্থই বিশ্ববন্ধু ছিলেন, সর্বসাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও মিলেছে। ৩০ মে ২০২০, জাতিসংঘ ডাক প্রশাসন (UN Postal Administration) এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের (Permanent Mission of Bangladesh to the UN) যৌথ উদ্যোগে একগুচ্ছ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে। উপলক্ষ ছিল, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস ২০২০ পালন। ডাকটিকিটে আছে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, মুজিববর্ষের লোগো/বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, দুজন বাঙালি মহিলা হেলিকপ্টার পাইলটের ছবি; এবং শান্তিরক্ষীদের প্রতিকৃতি ইত্যাদি। এ উপলক্ষে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার মন্তব্য প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ, “This is a humble, yet fitting tribute to Bangabandhu’s visionary leadership and doctrine of peace which defines our foreign policy; to our commitment to UN peacekeeping; as also to our valiant and selfless peacekeepers.”১৯ বঙ্গবন্ধু শান্তি স্বপ্নের স্বাপ্নিক ছিলেন। তবে তার শান্তি শুধু দেশের মানুষের জন্য ছিল না, ছিল পৃথিবী গ্রহবাসী সব মানুষের জন্য। আর এমন শান্তির অর্থ ছিল, শোষণ-বঞ্চনামুক্ত মানুষের মানবিক জীবন। সে কারণে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববন্ধুও হতে পেরেছিলেন। এমন একটি প্রেক্ষাপটে তুলনীয় চার্চিলের প্রয়াণে সংবাদ-মাধ্যমের মন্তব্য, “Few of our great men have been more British, but also few have been more international. In every land where a trace of freedom remains, and, and perhaps in many where freedom seems to have been snuffed out, the name of Churchill evokes the admiration of the noble and silences the gibes of the petty.”
Such a man has the power to lift up the hearts men. That was his supreme gift to us in life, and it may be his legacy to us in death.”২০ এমন কথাগুলো তো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কেও প্রযোজ্য।
লেখক : বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল্স (বিইউপি)
সাম্প্রতিক দেশকাল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন
© 2024 Shampratik Deshkal All Rights Reserved. Design & Developed By Root Soft Bangladesh