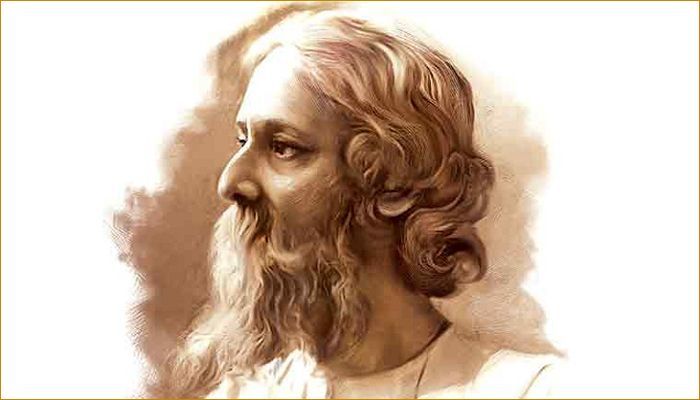
মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম
প্রকাশ: ১৭ এপ্রিল ২০২২, ০২:০৫ পিএম
আপডেট: ০৬ আগস্ট ২০২২, ১০:৫৮ এএম
এদেশের [ইউরোপের] লোক কড়া কথা হজম করতে পারে। সত্য কথা শোনবার জন্য শক্তির দরকার হয়, এদের সেই শক্তি আছে- আমাদের দেশের লোককে ক্রমাগতই মন ভোলাবার কথা বলতে হয়।
-র বী ন্দ্র না থ
If you wish to know what men will do, you must know not only, or principally, their material circumstances, but rather the whole system of their desires with their relative strengths.
Bertrand Russell
‘পরশ্রী’, ‘পরশ্রীকাতর’, ‘পরশ্রীকাতরতা’ শব্দগুলোর সঙ্গে মনে হয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় ছিল না। একজনের মানসিক কিংবা আার্থিক উন্নতির জন্য আর একজন যে জ্বলে-পুড়ে মরে, জীবনব্যাপী শব্দ সংগ্রহের মধুর আনন্দে যিনি মেতেছিলেন, এ ধারণা সম্ভবত সেই অভিধান-চিন্তকের মনে আসেনি! সেজন্য দেখা যায়, তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষ-এ শব্দ তিনটি নেই! রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় ‘পরশ্রী’ নেই, কিন্তু ‘পরশ্রীকাতর’ আছে! এখানে কী এক ফ্যাঁকড়া, দেখুন! প্রথম শব্দটি নেই, অথচ দ্বিতীয় শব্দটি তৈরি হলো! প্রথমটির জন্যই তো দ্বিতীয়টির ঘুম হারাম হয়ে যায়! তাহলে চলন্তিকা কীভাবে সম্ভব করে তুললেন এই বিপর্যয়টা? জানি না। আমাদের যুক্তিবোধ যে সর্বজনীন নয়, এ হয়তো তারই একটা ভালো দৃষ্টান্ত অবচেতন মনে রেখে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান- অবশ্য অনেক পরে রচিত। সেখানে ‘পরশ্রী’, ‘পরশ্রীকাতর’, ‘পরশ্রীকাতরতা’ পরপর তিনটি শব্দই আছে।
বাংলা শব্দভাণ্ডার একেবারে খাটো নয় বলেই ধারণা করা যায়। অথচ বাংলায় বিচিত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এত শব্দের নাগাল পাওয়া সত্ত্বেও আজও এ ভাষার একটি অভিধান সংকলিত হলো না, যাতে সকলের তৃষ্ণা মিটতে পারে। এ দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে ভাষাও একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। অথবা বলা যায় ভাষা আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। আর তাতেই আমরা আরও নানা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠি। কাজেই আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি এই ভাষা। কিন্তু উপযুক্ত আলো-বাতাস না পাওয়ায় এ ভাষার শরীর ও মনের শক্তি আজ শুকিয়ে ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে চলেছে। সত্য যে, বাংলা কেবল রসসাহিত্যের ভাষা হয়ে থাকল, জ্ঞানের ও গুণের ভাষা হতে পারল না। মানুষের মন যে শুধু সাহিত্যে বিচরণ করে না, বিজ্ঞান-দর্শনের মতো চিন্তার কঠিন ক্ষেত্রেও চলাফেরা করে- সে জ্ঞান আমাদের লেখাপড়া জানা মানুষের একেবারেই হলো না। থাক, সে অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ। মূল কথাটায় ফিরে আসা যাক।
আমাদের পরশ্রীকাতরতা যে হাল আমলের নয়, খুব পুরনো, তা শব্দটির উদ্ভবকালের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ‘পরশ্রীকাতর’ শব্দটি বাংলা গদ্যের প্রায় শৈশবকালেই তৈরি হয়েছে। প্রমাণ দেওয়া ভালো। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান-এ দেখা যায়, শব্দটি অক্ষয় দত্ত থেকে গৃহীত। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে শব্দটির উদ্ভবকাল দেখানো হয়েছে। বাংলা শব্দগুলো নাম- সাকিন অর্থাৎ ঠিকানা আজও যাচাই করা হয়নি কোনো শব্দের জন্ম কবে হয়েছে। সুলতানি আমল, মোঘল আমল, নবাবী আমল, ইংরেজ আমল- এমন নানা কালের পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আমাদের শব্দের উদ্ভব হয়েছে। আমাদের জাতির বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যে এই শব্দের ইতিহাস বিস্মৃতিও একটি। ‘পরশ্রীকাতর’ শব্দটি আরও আগের কি না, তা অবশ্যই ভালো করে যাচাই করা হয়নি। কেননা বাংলা একাডেমির এই কাজটি একেবারে প্রথম উদ্যোগ। তবুও বলা যায়, শব্দটি বেশ পুরনো। অপরের উন্নতি দেখে যে ঈর্ষার জন্ম হয়, তারই নাম পরশ্রীকাতরতা। ইংরেজিতে এর নাম দেওয়া হয়েছে Inferiority Complex।
আমরা জানি, শব্দ আমাদের প্রায়ই প্রতারণা করে, তবু মনের অধিকাংশ ভাব প্রকাশের জন্য শব্দ আমাদের সহায়ক। একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। ‘আধ্যাত্মিকতা’ কারো মাথা গরম করে তোলে, কেউ তাতে গদগদ হয়ে পড়েন। এ জন্য বলা হয়ছে, ভাষার নিজের কোনো বিশিষ্টতা নেই। মানুষের মনের নানা স্তরের ভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্যই ভাষার উদ্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ। কথাটা ভাববাদের গা ঘেঁষা হলো সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের মনোভাব যে ভাষা দিয়ে আটকানো গেল, তা স্বীকার করা ভালো। কী অর্থে ও কোনো পরিবেশে কোন শব্দ প্রযুক্ত হচ্ছে, সেটা জেনে নেওয়াই জরুরি। অপরের উন্নতিতে আমি যে কাতর, এটা প্রকাশ করা কিভাবে সম্ভব হতো যদি ভাষা আমাদের সাহায্য না করত? কাজেই ভাষা সব সময় মানুষের মনের কথা গোপন করে এমন নয়, কখনো কখনো প্রকাশও করে ফেলে।
২
রবীন্দ্রনাথ খুব কম বয়সে আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর স্বজাতি বাঙালি হিন্দু বড্ড বেশি পরশ্রীকাতর। তাঁর প্রতিভার মর্যাদা তাঁরা কোনোদিনই দিতে চায়নি। তাঁরা কেবলি তাঁকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করে এসেছে। কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের প্রাপ্য সম্মান যখন ভিন্ন জায়গা থেকে অন্যের হাত দিয়ে এলো, কেবল তখনই তাঁদের মনে হলো, তাঁর ওপর এতদিনের অবহেলা করাটা ঠিক হয়নি। এমন মুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, এই বোধোদয়টা তাঁদের উত্তেজনা।
প্রসূত, ক্ষণিকের মোহ, জোয়ারের জলের মতো ভাটার টান পড়লে এটা কেটে যাবে। ঠিক এই কারণে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে দেশবাসী যখন তাঁকে সম্মান জানাতে সমবেত হয়, তখন সে সম্মান তিনি আনন্দের সঙ্গে, প্রসন্ন মনে, বিনীতভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এই সংবর্ধনা অগ্রহণের কারণ কী? এক ঈর্ষাপরায়ণ জাতিকে তিনি কী কোনো শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন? এক গভীর অর্থে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি তো আমাদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। কিন্তু সেই শিক্ষা কি তাঁর জাতি ভালোভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল? একেবারে মৃত্যুর আগ-মুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, তাঁর জাতি মনের দিক থেকে অপরিবর্তিত থেকে গেছে!
নোবেল পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়েছিল ১৯১৩ সনের ১৩ নভেম্বর। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাবার জন্য ২৩ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে দেশের সর্বপ্রধান মান্য ও বিদ্বান লোকেরা সমবেত হয়েছিলেন। সংবর্ধনার নানা তর্পণ শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ শুরুতে বলেছিলেন, ‘আজ আমাকে সমস্ত দেশের নামে আপনারা যে-সম্মান দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসংকোচে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই।’ কারণটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেন, কবিবিশেষের কাব্যে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন। আমার কাব্য সম্বন্ধেও এই স্বভাবের নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি, একথা আমার এবং আপনাদের জানা আছে। দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেছে তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্য যে বিদেশ হ’তে আমি সম্মান লাভ করলুম তা এখন পর্যন্ত আমি নিজেই ভাল করে উপলব্ধি করতে পারিনি।
দেশের লোকের কাছ থেকে এতদিন রবীন্দ্রনাথ কেবলি ‘অপযশ ও অপমান’ লাভ করে এসেছিলেন। আজ যখন পাশ্চাত্য থেকে প্রতিভার যথার্থ সম্মান এসেছে, তখন দেশের লোকের কাছ থেকে এমন সমবেত পাঁচজন লোকের কাছ থেকে সংবর্ধনা নেবার মূল্য কী? তাই রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, ‘যে কারণেই হোক, আজ ইউরোপ আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখানকার গুণীজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই। নোবেল-প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রস বৃদ্ধি করতে পারে না।’ রবীন্দ্রনাথ বললেন, অতএব আজ যখন সমস্ত দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে আপনারা আমাকে সম্মান উপহার দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন সে সম্মান কেমন করে আমি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করব? আমার আজকের এই দিন তো চিরকাল থাকবে না। আবার ভাটার বেলা আসবে, তখন পঙ্কতলের সমস্ত দৈন্য আবার তো ধাপে ধাপে প্রকাশ হতে থাকবে।
ঠিক এই কারণে তিনি দেশবাসীর সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, তাই আমি আপনাদের কাছে করজোড়ে জানাচ্ছি- যা সত্য তা কঠিন হলেও আমি মাথায় করে নেব, কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার মায়া যা, তা স্বীকার করে নিতে আমি অক্ষম। কোনো কোনো দেশে বন্ধু ও অতিথিদের সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন, তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমি চিত্তকে দূরে রাখতে চাই।
দেশের লোকের কাছ থেকে শুধু ‘অপযশ ও অপমান’ পাওয়া থেকেই কী রবীন্দ্রনাথ উক্ত সংবর্ধনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? অনেক রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন, দেশবাসীর উল্লিখিত সংবর্ধনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতি অপেক্ষা জাতীয় আত্মাভিমানের তৃপ্তি বেশি ছিল। কবি হিসেবে দেশবাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথের একটা একান্ত চাওয়া ছিল। ১৯১৪ সনের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে রামমোহন লাইব্রেরিতে দেওয়া বক্তৃতায় সেই চাওয়ার কথাই অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেন। সেখানে তিনি বলেন, কবি যখন আপনার হৃদয়ের আনন্দে গান গেয়ে ওঠেন তখন তার সবচেয়ে বড় দুঃখ হয় যদি সে তার দেশের, তার ঘরের ভায়েদের সহানুভূতি না পায় এবং তার সবচেয়ে বড় সুখ, সবচেয়ে বড় পুরস্কার সে পায় তাদের স্বতঃউচ্ছ্বসিত প্রীতিতে। একথা বললে মিথ্যে বলা হবে যে, কবে কোনো সুদূর ভবিষ্যতে তার আদর হবে এই আশায় কবি নিশ্চিন্ত থাকে না, এরকম উপবাস করে থাকা যায় না। কবি চায় সমস্ত প্রাণ দিয়ে সহানুভূতি, প্রীতি- তার অভাবে তার কি বিপুল বেদনা তা সে ছাড়া আর কেউ বুঝে না। আমি জগতের হাত থেকে সম্মান নিতে পারি, কিন্তু আমার মার হাত থেকে, আমার ভায়ের হাত থেকে প্রাণের প্রীতি ছাড়া কিছু গ্রহণ করতে পারি না। ওই প্রীতি আমি প্রাণভরে চাই-আপনারা আমাকে তাই দিন।
নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর দেশবাসীর মনোভাব বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। সংবর্ধনা প্রত্যাখ্যানের ফল ভালো হয়নি। তাঁর প্রতি দেশবাসী আরও বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে। আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ‘নোবেল পুরস্কার- বর না শাপ’ অধ্যায়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর সমাদর যেভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন তাহাতে বাঙালির মধ্যে তাঁহার প্রতি পুরাতন যে বিদ্বেষ ছিল তাহা আরও উগ্র হইয়া উঠিল। বলিতে গেলে পরদিন হইতেই আবার আক্রমণ ও অপমান আরম্ভ হইল। শত্রুরা একথা পর্যন্ত বলিল যে, ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি আসলে ইংরেজ পীয়ারসনের, তাঁহার নিজের নয়।’ ইংরেজি জানতেন না, এ অপবাদ রবীন্দ্রনাথকে অনেক আগে থেকে হজম করতে হয়েছিল। অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সনে লেখা ‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সে-কথা গভীর বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন।
১৮৯৫ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সূচনা হয়। মাতৃভাষায় সম্মেলনের কাজ পরিচালিত না হওয়ায় তা ব্যাহত হচ্ছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ব্যাপক গণসংযোগ এবং জননেতা ও জনসাধারণের মধ্যে যেন কোনো দূরত্ব তৈরি না হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৯৭ সনের অসমাপ্ত নাটোর সম্মেলনে তিনি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়কে সঙ্গে নিয়ে এবং পরের বছর ঢাকায় এককভাবে কিছুসংখ্যক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবকের সহায়তায় অধিবেশনে ক্রমাগত ইংরেজি ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলন তখন সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত প্রবন্ধে বলেন, আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদযোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সব চেয়ে লজ্জার সেটিই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে।
নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে অবশ্য তাঁকে অপমান করবার সাহস কোনো বাঙালির হয়নি। কিন্তু দেশবাসীর নিন্দা ও বিদ্বেষ তিনি ঠেকাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এটা হয়েছে পরশ্রীকাতরতা থেকে। এই পরশ্রীকাতর মানুষের ওপর বিশ্বাস রক্ষা করা বড় কঠিন। শেষ জীবনে তিনি এই সত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন।
৩
‘রবীন্দ্রনাথের সহিত কয়েকটি দিন’ নামের একটি লেখায় পাওয়া যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শেষ ভরসার কথা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরে এই লেখাটি তৈরি করেছিলেন কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ। রচনাটি প্রকাশিত হয় ২৫ বৈশাখ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, দেশ পত্রিকায়। তখন রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যায়। কবির সেবাযত্ন করছিলেন কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। তিনি তাঁর সহকারী হিসেবে আহ্বান করে নিয়েছিলেন কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষকে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট। কমলাকান্ত ঘোষ রবীন্দ্র-সেবায় আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ৩ জুলাই ১৯৪১-এ। এই সময় তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-সমস্ত কথাবার্তা হয়, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বয়ান হচ্ছে উল্লিখিত প্রবন্ধটি।
উল্লেখ করা দরকার, উক্ত প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, কমলাকান্ত ঘোষ ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী। ‘বঙ্গীয় সরকারের রোষকবলিত’ হয়ে তিনি পাঁচ-ছয় বছর বন্দিজীবন কাটিয়েছিলেন নানা জায়গায়। পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামনে চার অধ্যায় (১৯৩৪) উপন্যাসের কথা তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘তোমরা এই বইখানি গ্রহণ করনি।’ এই বইয়ের বক্তব্য গ্রহণ না-করার কারণ কমলাকান্ত ঘোষ সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার ভাষায় উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তা শুনে মৌন থেকেছেন। তাঁর কথা খণ্ডন করে উত্তর দেননি। পরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমি একবার স্বদেশীতে খুব মেতেছিলুম। তোমরা জান কি না জানি না, সে সময় আমি নিজেকে পুরোপুরিভাবে নিয়োগ করেছিলুম- সভা সমিতি বক্তৃতাতে। কিন্তু এর পরই আমাকে সরে আসতে হ’ল। তখন দেখেছি নেতৃস্থানীয় লোকদের চরিত্রে কত আবর্জনা জড় হয়েছিল। আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপই বলব। নিজের স্বার্থ নিয়ে এমন বিশ্রী কাড়াকাড়িতে আমার মন হাঁপিয়ে উঠল- তারপর থেকে এখানেই এসে পড়েছি- লোকশিক্ষার আদর্শ নিয়ে। আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি চরিত্র গঠনের জন্য, নৈতিক নিষ্ঠার জন্য।’
রবীন্দ্রনাথ খুবই বিরক্ত ছিলেন তাঁর বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রতি। নিজের ক্ষুদ্রতা তারা কোনোদিন বুঝতে চায়নি। আত্মসমালোচনা তারা কোনোদিন সহ্য করতে পারেনি। এ সমাজের নেতৃত্বের মধ্যে তিনি এই রকম অজস্র সমস্যা ও সংকট লক্ষ্য করেছিলেন। অন্যের নিন্দা ও দোষ না খুঁজে নিজেকে গড়ে তোলার দিকেই নিজের শক্তি ব্যয় করা কর্তব্য মনে করেছিলেন তিনি। দীনেশচন্দ্র সেনকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন, ‘বিদ্বেষে কোনো সুখ নাই, কোনো শ্লাঘা নাই, এই জন্য বিদ্বেষটার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। জীবনপ্রদীপের তেল তো খুব বেশি নয়, সবই যদি রোষে, দ্বেষে হু হু শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালোবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব?’ রবীন্দ্রনাথের থেকে পাওয়া মনুষ্যত্ব উদ্বোধক এমন অভাবিতপূর্ব শিক্ষা সম্পর্কে কমলাকান্ত ঘোষ অবহিত ছিলেন। সেজন্য তিনি চার অধ্যায়-এর কথা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অতুল্য অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করে বলেছিলেন, ‘বাঙ্গালীর মনে আপনি যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছেন আপনার জীবন দিয়ে, বাঙ্গলা হয়ত এর উত্তরাধিকারিত্বের মর্যাদা রেখে চলতে পারবে। বাঙ্গালীর কালচার, বাঙ্গালীর শিক্ষাপ্রতিভা এসব নিয়ে আপনি কি মনে করেন না বাঙ্গালী জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারবে?’
রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বলেছিলেন, ‘তোমার কথা ঠিক। বড় হবার সব উপকরণই বাঙ্গালীর আছে, কিন্তু আরও একটি উপকরণ আছে যার জন্য বাঙ্গালীর বড় হবার কোনো আশা দেখি না- পরশ্রীকাতরতা, বাঙ্গালী এটা ছাড়তে পারবে বলে ভরসা হয় না।’
রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ বেলায় কেন এমন কথা মুখে এনেছিলেন? তিনি কী বাঙালি হিন্দুর কাছ থেকে এতটাই দূরে সরে এসেছিলেন? এই বেদনাবোধ থেকেই কী তিনি ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র (১৮৯৫ সনের মার্চ) ‘বঙ্গমাতা’ কবিতায় লিখেছিলেন,
‘সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।’
অন্তিম মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ এ কথাও তো আমাদের শুনিয়েছিলেন যে, ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’! তাহলে কমলাকান্তকে এমন কথা শোনালেন কীভাবে? অবশ্য সব মানুষের ওপর বিশ্বাস রক্ষা করবার কথা তিনি বলেননি। যে মানুষ কথা দিয়ে কথা রক্ষা করতে পারে না এবং না-পারার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ পর্যন্ত করে না, তাকে বিশ্বাস করা তো পুণ্যের কাজ হতে পারে না! আর সব মানুষই যে বিশ্বাস রক্ষা করতে পারবে না এবং সবাই যে পরশ্রীকাতর হবে, এটা তো কোনো কাজের কথা নয়। ঠিক এই কারণে রবীন্দ্রনাথ কমলাকান্তকে আশস্ত করেছিলেন এবং বিস্মিত ও অপ্রস্তুত করে দিয়েছিলেন এমন এক কথায় যা ছিল তাঁর কল্পনার অতীত। কমলাকান্ত লিখেছেন, ‘খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে [রবীন্দ্রনাথ] বললেন, ‘দেখো বাঙালি বড় হবে, তবে কারা জানো, বাঙ্গলার মুসলমান। এই ব্যাধিটি (পরশ্রীকাতরতা) ওদের চরিত্রে নেই, অথচ প্রতিভা তাঁদের আছে।’
এর পর কমলাকান্ত ঘোষ নিজে যা উপলব্ধি করেছিলেন এবং বাস্তব অবস্থা দেখে যা মনে করতেন, তা তাঁর নিজের ভাষায় শোনা যাক। রবীন্দ্রনাথের কথা শোনার পর তিনি চমকে গিয়ে লিখেছেন, এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। মুসলমান-সম্প্রদায় হিসাবে বাঙালি মুসলমান তাঁদের প্রতিভা গড়ে তুলবার একক পরিবেশ কখনো পেতে পারে এ কল্পনা তখনকার দিনে সুদূরপরাহত ছিল। আমায় একদিন গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে যেসব সরকারি কর্মচারীর সম্পর্কে আমরা জেনে এসেছি, তাঁরা কি রকম ব্যবহার করতেন আমাদের সঙ্গে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁকে জানিয়েছিলুম, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার আমরা পেয়েছিলুম তাঁদের যাঁদের প্রকৃত শত্রু ছিলুম আমরা- ইংরেজ জাতি। তাঁরা আমাদের সমকক্ষ হিসেবে দেখতেন। সবচেয়ে দুর্ব্যবহার পেয়েছি হিন্দু পুলিশ কর্মচারী থেকে- তাঁরাই ভাবতেন আমরা তাঁদের শত্রু। শুধু মুসলমান কর্মচারীদের ব্যবহার ছিল খুব আন্তরিকতাপূর্ণ। এমন ঘটনাও ঘটেছে কোনো কোনো মুসলমান পুলিশ কর্মচারী চাকরি বিপন্ন করেও আমাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সহানুভূতি দেখাতে ত্রুটি করেন নাই। হিন্দু কর্মচারী অনেকেই আমাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁদের চাকরির উন্নতির পথ প্রশস্ত কর্চ্ছিলেন। এ কাহিনী শুধু আমার জীবনে নয়, বাঙ্গলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে বহুলোকের অভিজ্ঞতাও এর সাক্ষ্য দেয়। [...] আজ ভারতের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের পটভূমিকায় মনে হয় সত্যদ্রষ্টা ভারতীয় ঋষির এই ভবিষ্যদ্বাণী হয়ত সাফল্যের বহু দূর নেই। রাষ্ট্রবিপ্লবে বিধ্বস্ত দেশে ঘনতিমিররজনী শেষে শান্ত ঊষায় বাঙ্গলার মুসলমান হয়ত নিজ প্রতিভায় স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে। আজ সমস্ত দেশ সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিষে সমাচ্ছন্ন। আজ মানবতা সাম্প্রদায়িকতার রুদ্ধদ্বারে প্রত্যাখ্যাত ভিখারী। যুগে যুগে সঞ্চিত মানবসভ্যতা নগ্নতায় আজ আদিম সভ্যতার স্তরে এসে পড়েছে। কিন্তু ইতিহাসের রথচক্র নতুন অধ্যায়ের সূচনা আনবেই।
রবীন্দ্রনাথের দেখা বাঙালি মুসলমান সম্পর্কিত তথ্য মিথ্যে ছিল না। তবে তাঁর দেখার পরিসর ছিল সত্যিই খুব ছোটো। অতি অল্পসংখ্যক মুসলমানের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল। তখন মুসলমান মধ্যবিত্ত সদ্য গড়ে উঠছিল। তাঁরই ভিত্তিতে তিনি এক বিরাট সিদ্ধান্ত করে বসেছিলেন। মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর এ অভিজ্ঞতাকে খুব মূল্যবান বলা যায় না। এ সমাজ অবশ্য জেগে উঠেছিল বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেরণা সে লাভ করেছিল এক চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার মোহ থেকে। রাজনীতির চালের সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ছিল তার ইন্ধন স্বরূপ। ফলে মোহভঙ্গের সময় লেগেছিল অতি অল্প।
ভারত ভেঙে কী করে অবস্থানগতভাবে দুটি ভিন্ন জিয়োগ্রাফি সমন্বিত প্রদেশ একটি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে, এটা মানব ভাবনার অতীত। অথচ তখনকার মুসলিম নেতৃত্ব তাই মেনে নিয়েছিলেন। অবশ্য হিন্দু নেতৃত্বের বিদ্বেষবিষও এই ভাগের প্রধান কারণ ছিল, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। পরে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ গড়ে তোলার দিকে বাঙালি মুসলমানের যে চারিত্র্যিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিরাট অধ্যায় তার এক নজিরবিহীন ঘটনা। তার পরের বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আজ বাঙালি হিন্দু-মুসলমান একই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতায় আমাদের জুড়ি নেই। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পরের ইতিহাস পরশ্রীকাতরতার ইতিহাস। এই ইতিহাস থেকে একটা চরম উদাহরণ দেওয়া যাক।
ভাগ্যচক্রে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় ছিলেন পাকিস্তানের জেলে। প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তাজউদ্দিন আহমদ। তখন তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বে, বাঙালির রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ইসলামাবাদ থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেই শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হন। কিছুদিন যেতে না যেতেই, খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে করেন অর্থমন্ত্রী। সেটাও তাঁকে শান্তি ও স্বস্তি দেয়নি। বিচলিত বুদ্ধির তরঙ্গে তাই তিনি অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী- এটা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ছিল এক অপরাজেয় বিস্ময়! এই বিস্ময় তাঁকে তাজউদ্দিন আহমদের কাছ থেকে তাঁর না দেখা নয় মাসের প্রকৃত ইতিহাস জানতে দেয়নি। তাজউদ্দিন আহমদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবার এই তৎপরতার পিছনে রাজনীতিসমেত আরও অনেক কারণ থাকা সম্ভব।
শেখ মুজিবুর রহমান পরশ্রীকাতরতা বিষয়ে নিজে খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর এক জায়গায় বাঙালির নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই পরশ্রীকাতরতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হল ‘আমরা মুসলমান, আর একটা হল, আমরা বাঙালি।’ পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধ হয় দুনিয়ার কোনো ভাষায়ই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, ‘পরশ্রীকাতরতা’। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে ‘পরশ্রীকাতরতা’ বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায় পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্য বাঙালি জাতির সব রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবু এরা গরিব। কারণ যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।
পরশ্রীকারতা যে ভয়ানক ব্যাধি, ঈর্ষা থেকে যার জন্ম- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে পরবর্তীকালের ইতিহাসে পাওয়া যাবে এর অগণিত নজির। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিন্দু সমাজের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন। ভরসা করতে চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজের ওপর! তাঁর শেষ ভরসা ও বিশ্বাস, আমরা রক্ষা করতে পারিনি! ভবিষ্যতের কথা আমরা কেউ জানিনে। বর্তমানের বাংলাদেশে আমাদের অভিজ্ঞতা এমন সিদ্ধান্তেই উপনীত করে।
সাম্প্রতিক দেশকাল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন
বিষয় : বাংলাভাষা শব্দভাণ্ডা রবীন্দ্রনাথ পরশ্রীকাতরতা
© 2024 Shampratik Deshkal All Rights Reserved. Design & Developed By Root Soft Bangladesh