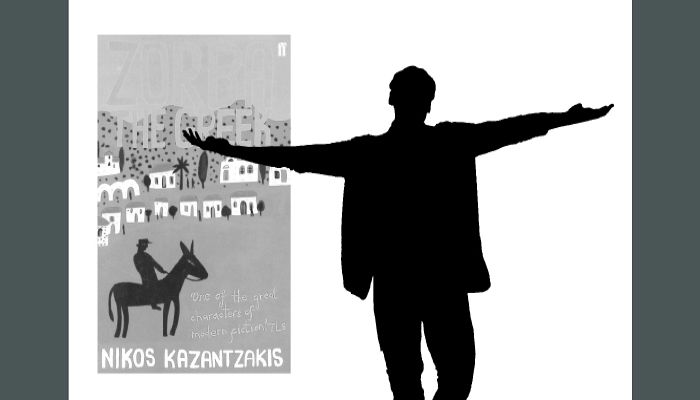
গ্রিক কবি ও ঔপন্যাসিক নিকোস কাজানজাকিসের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস ‘জোরবা দ্য গ্রিক’-এর প্রধান চরিত্র এই আলেক্সি জোরবা। এই চরিত্রের নানাবিধ কাণ্ডকারখানা মাধ্যমে লেখক মানব জীবনের প্রাঞ্জল, প্রাণোচ্ছল ও জমিন-ঘেঁষা একটি স্বাস্থ্যকর দর্শনেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন।
কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবর্জিত একটি মানুষ যে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একজন দার্শনিকের পর্যায়ে উঠতে পারে, বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অপার বিস্ময়ে পর্যালোচনা করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি অতি উন্নত ধারণা লালন করতে পারে, তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায় এই মজুর শ্রেণি থেকে আগত বিচক্ষণ লোকটির মাঝে।
গ্রিক সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র অডিসিয়াস, যে ট্রয়ের সঙ্গে এক দশক ধরে চলা যুদ্ধে অন্যান্য অনেক নৃপতির সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কাজানজাকিস তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘অডিসি: একটি আধুনিক উত্তরকাণ্ড’ মহাকাব্যে অডিসিয়াসকে আরও অনেক বৃহৎ কলেবরে জোরবার মতো একই দর্শনে বিশ্বাসী এক অমর চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। আসলে এই দুজনের যে দর্শন, তা বলতে পারি এদের নির্মাতারই দর্শন।
এই দর্শনে মানুষকে অন্য সবার সঙ্গে-জীব, বস্তু, আলো, বাতাস, জল আর মাটির সঙ্গে এক করে দেখে। এই সবকিছুই-মানুষ, পশু, জড়-অজড় বস্তু সবাইসময়ের বিরুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রাম করে শেষে রূপান্তর হয় ব্যোমে, শূন্যতায়। সময়ের বিরুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রাম করে সবাই এবং সবাই এক সময় পরিবর্তিত হয় স্রেফ চৈতন্য বা আত্মায়। কাজানজাকিসের এমন বিশ্বাস একদিকে যেমন নৈর্ব্যক্তিক, বৌদ্ধ ধর্মীয় ও নৈতিকতা-নিরপেক্ষ, অন্যদিকে তেমনি এক ধরনের দ্বান্দ্বিক মরমিবাদ হিসেবেও এর ব্যাখ্যা করা চলে।
জীবনের চালিকা শক্তিই হলো দ্বান্দ্বিকতা। দ্বান্দ্বিক না হলে গতিসঞ্চার হয় না; বিপরীতধর্মী শক্তির সংস্পর্শে না এলে তাতে আলো জ্বলে ওঠে না। এই দ্বান্দ্বিকতার মতবাদ আদি দার্শনিকদের যেমন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন, তেমনি আধুনিক যুগের দার্শনিকরাও-হেগেল, মার্কস, বারগস-তাদের চিন্তাভাবনার প্রতিপাদ্য করেছেন এই দ্বান্দ্বিকতাকেই, যা বিশ্বচরাচরে সর্বত্রই উপস্থিত থেকে জীবনকে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল রেখেছে।
কাজানজাকিসের জোরবা ও অডিসিয়াস সামাজিক মর্যাদায় দুই মেরুর বাসিন্দা হলেও জীবন ও জগৎ দর্শন এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই পথের পথিক। বুদ্ধিবিবেচনা ব্যবহার করে জীবনকে প্রচণ্ড ভালোবাসায় ভোগ ও উপভোগের উপকরণ যেমন আছে দুই চরিত্রেই, তেমনি রয়েছে মৃত্যু চিন্তা, মৃত্যু-পরবর্তী
কৃষ্ণগহ্বরের চিন্তা। হতাশায় না ডুবে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনের একেবারে তলানিসুদ্ধ পান করার আকাঙ্ক্ষায় দুই চরিত্রই উন্মুখ। কোনো বিশেষ ধর্মীয় নীতির আলোকে নয়, স্রেফ সাধারণ ভালো-মন্দের মিশ্রণে জীবনকে নৈতিকতা-নিরপেক্ষ দর্শনের আলোকে উপভোগ করার কথাই বলা হয় এই দুই চরিত্রের মাধ্যমে।
দেহ ও আত্মার চিরন্তন বিবাদ ঘুচিয়ে, আলো ও অন্ধকারের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘটিয়ে, বিপরীতধর্মী শক্তিগুলোকে একের জন্য অন্যকে অপরিহার্য করে তোলে, ইতি ও নাতির সমান গুরুত্ব নিশ্চিত করে, ‘আছে ও নাই’-কে সমান মর্যাদায় ধারণ করে এক উচ্চতর মানসিক অবস্থানে বাস করাই এই দর্শনের প্রতিপাদ্য। কেবল কাজানজাকিস কিংবা তার সৃষ্ট প্রধান দুই চরিত্রেরই নয়, বিশ্বের আরও বহু মুনি-ঋষি, শিল্পী-সাহিত্যিকেরও বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি এই দর্শন।
আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথও একইভাবে ক্ষয়কে, নেতিকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। কন্যা মাধুরিলতার মৃত্যুর পর লেখা একটি কবিতায় মৃত্যুকে গ্রহণ করে ‘আছে-নাই’-এর সমুদ্রে নিজেকে যেভাবে মেলাতে চেয়েছেন সেটাই সনাতন মুনি-ঋষি, সাধক আর মরমিয়া দার্শনিকদের মূল কথা। জোরবা, অডিসিয়াসও একই দর্শনে বিশ্বাসী; কিন্তু শিল্পকর্মে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন, গতিপ্রকৃতি, যাত্রাপথের নানা বাঁক ও চড়াই-উতরাইয়ে দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যও নেহায়েত কম নয়।
কাজানজাকিস মনে করেন না এই বিপরীত যুগলের দ্বন্দ্বের কারও নিরঙ্কুশ জয় হয়। বাস্তবে সেটা অবশ্য সম্ভবও নয়, তবে শক্তিমত্তায় তারতম্য তো হতেই পারে। নেতির প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যদি ইতি কোণঠাসা হয়ে পড়ে তো শুরু হয় মাৎস্যন্যায়। আর যদি হ্যাঁ হয় বিত্তবান, তখন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আসে মধুমাস। অবশ্য কাজানজাকিস আরও উদারচেতা হয়ে এই দুই বিপরীত শক্তিকে শত্রু কিংবা দ্বান্দ্বিক হিসেবে দেখেন না, দেখেন পরস্পরের পরিপূরক এবং সহযোদ্ধা হিসেবে।
তার আত্মজীবনী ‘রিপোর্ট টু গ্রেকো’তে কাজানজাকিস আথস পাহাড়ের আশ্রমের একজন পাদ্রির প্রথম ‘অবৈধ’ যৌন অভিজ্ঞতার কাহিনি বলেছেন। পাদ্রি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলছেন, ‘আমার তখন মনে হচ্ছিল যেন ঘরে স্বয়ং ঈশ্বর এসেছেন এবং এসে আনত হয়েছেন আমার বালিশে-এমন যেন হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যাবে।’ কোনো প্রার্থনা নয়, উপবাস নয়, এক নারীই যেন খ্রিষ্টকে নিয়ে এসেছিল তার ঘরে।
এভাবে সে অবাক হয়ে ভাবে-তাহলে কি পাপের পথেও ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়? তাহলে পাপ-পুণ্যের দুটো পথ কি সমান্তরালভাবে ঈশ্বরের দিকে, চিরায়তের দিকে প্রসারিত? তাহলে কি পাপাচারও ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত? এইসব প্রশ্ন করতে গেলেও যে গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সাহসের প্রয়োজন তা সম্ভবত চিন্তাচেতনার উচ্চমার্গে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।
জোরবার জীবন দর্শন কাজানজাকিস প্রধানত বস্তুজগতের নানা উপসর্গ সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ করেন। বিশ্ব তার কাছে সরল, আদিম ও চিরকালের কুমারী। সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়, নক্ষত্রপুঞ্জের চলাচল, ঝড়-বৃষ্টি, সমুদ্র, পাহাড়-এরা সবাই তার কাছে নব নব বিস্ময়ের ধন। সবকিছুকে সে শিশুর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে-এমন যেন প্রকৃতির এইসব উপসর্গ সে প্রথম দেখছে।
এভাবে বিশ্বকে শিশুর মতো হেসে স্পর্শ করা বা অবলোকন করাও এক ধরনের প্রার্থনা, বলতে কি শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ‘ওহ,’ ‘আহ’ বলতে পারা অর্থাৎ তাকে বিস্ময়ে উপভোগ করার চেয়ে ভালো প্রার্থনা আর নেই।
জোরবা যে কেবল নিসর্গেরই বোদ্ধা প্রেমিক তা নয়। মানুষের, বিশেষ করে নারী জাতির প্রতি তার সহমর্মিতাবোধ তাকে এক উন্নত মাপের পৌরুষে দীপ্যমান করে তোলে। মেয়েদের সম্পর্কে নানা ঠাট্টা-মশকরা ও হালকা মন্তব্য করলেও আসলে তাদের প্রতি তার গভীর প্রেম আর সহানুভূতিই প্রকাশ পায়। মাদাম অরতেনসের সঙ্গে তার বিয়ে, বিশেষ করে এই ষাটোর্ধ্ব ফরাসি নারীর প্রতি তার যে অঙ্গীকার তা তার মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুপরবর্তী নানা কার্যকলাপে প্রকাশ পায়।
জোরবার দর্শন দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে স্থূলভাবে প্রকাশ পেলেও মানুষের যোগ্যতার বিভিন্ন পর্যায় বুঝতে সে কিন্তু একজন চিন্তাশীল মানুষের মতোই বিবেচনাবোধের পরিচয় দেয়। সে জানে তিন রকমের মানুষ আছে যারা দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে তিন রকমের যোগ্যতার পরিচয় দেয়। একদল খাবারকে স্রেফ দেহের তেল-চর্বি আর জৈব সার উৎপাদনে ব্যবহার করে।
দ্বিতীয় শ্রেণির লোকে খাদ্যকে রূপ দেয় কাজে-কর্তব্যে, আমোদ-ফুর্তিতে। এরাই গড়পড়তা মানুষ। কিন্তু আরও কেউ কেউ আছে যারা দৈনন্দিন আহার্যকে রূপান্তর করে আত্মায়, ঈশ্বরে। এভাবে নানা ধরনের কথাবার্তায়, জোরবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত হলেও হাতে-কলমে শিক্ষা থেকে যে অভিজ্ঞান অর্জন করে এবং নিসর্গের ও দৈনন্দিন রহস্যের মাঝখানে বাস করে তা জীবনের অংশ হিসেবে যাপন করে, তা সুশীল সমাজের বহু শিক্ষিত মানুষেরও নাগালের বাইরে।
কাজানজাকিস তার আত্মজীবনী ‘রিপোর্ট টু গ্রেকো’য় তিন ধরনের মানুষের তিন রকমের প্রার্থনার কথা বলেছেন। এরা মনে করে তারা ঈশ্বরের হাতে ধরা তীর-ধনুক এবং সেভাবে তারা আর্জি জানায়। প্রথমজন বলে: আমি তোমার হাতে ধরা ধনুকের ছিলা; আমায় টানো ঈশ্বর, নইলে যে পচে গেলাম। দ্বিতীয়জনের প্রার্থনা: আমায় বেশি জোরে টেনো না প্রভু, ছিঁড়ে ছুটে যাব; আর তৃতীয়জন বেপরোয়া।
সে বলে, আরও জোরে টানো প্রভু, যদি ছিঁড়ি তো ছিঁড়ব, কে পরোয়া করে? যেমন জোরবা, তেমনি অডিসিয়াস-দুজনেই এই তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত মানুষ। দুজনই জীবনকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় ভোগ করে একেবার ছিবড়ে করে রাখতে চায় যেন মৃত্যু যখন জিভ চটকাতে চটকাতে আসবে তখন যেন সে এসে পায় কেবল একরাশ হাড়গোড়। এ ধরনের জীবনমুখী দর্শন কাজানজাকিসের নায়কদের করে তুলেছে প্রাণবন্ত, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের মরবিড, ফ্যাকাসে নায়কদের পাশে এদের অবস্থান খুবই উজ্জ্বল ও জীবন্ত।
জোরবা ও অডিসিয়াস বিশ্বসাহিত্যের এই দুই চরিত্রের মৃত্যুদৃশ্যের স্থান-কাল বিভিন্ন মাত্রায়, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে হলেও তাদের অপরিহার্য গুণ বহুলাংশে একই। জোরবা মৃত্যুর আগে বালিশ-চাদর ছুড়ে ফেলে; স্ত্রী, পড়শিদের ঠেলে সরিয়ে মৃত্যুশয্যা থেকে লাফিয়ে নেমে, জানালার শার্সিতে হাতের নখ চেপে বসিয়ে দূরের পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে হাসে, কখনো ঘোড়ার মতো হ্রেষা ধ্বনি ছাড়ে। এভাবে মৃত্যু এসে পায় তাকে।
অন্যদিকে অডিসিয়াস মরণ বরণ করে যখন তার দেহ ক্রমে বাষ্পের আকার ধারণ করে, তার বরফের জাহাজ দক্ষিণ গোলার্ধের সাগরে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যায়, তার মাংস গলে, চোখের দৃষ্টি জমাট বাঁধে এবং হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকি যায় থেমে। মুক্তির পবিত্র চূড়ায় লাফিয়ে উঠে বায়বীয় ডানা ঝাপটিয়ে স্বয়ং মুক্তির খাঁচা থেকেই সে উড়াল দেয়।
চারপাশে সবকিছু ভঙ্গুর কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এরই মধ্যে শোনা যায় তামস জলরাশির ওপর ভেসে থাকা এক সাহসী নির্দেশ: এগিয়ে চলো বন্ধুগণ, পাল তুলে এগিয়ে চলো, হও আগুয়ান; স্বচ্ছ হাওয়ায় লাগে মৃত্যুর শুভ পরশন। এভাবে কাজানজাকিসের দুই প্রধান চরিত্র জোরবা আর অডিসিয়াস বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে ওঠে।
লেখক: শিক্ষাবিদ ও অনুবাদক
সাম্প্রতিক দেশকাল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন
© 2024 Shampratik Deshkal All Rights Reserved. Design & Developed By Root Soft Bangladesh