মুখোমুখি সৈয়দ আবুল মকসুদ
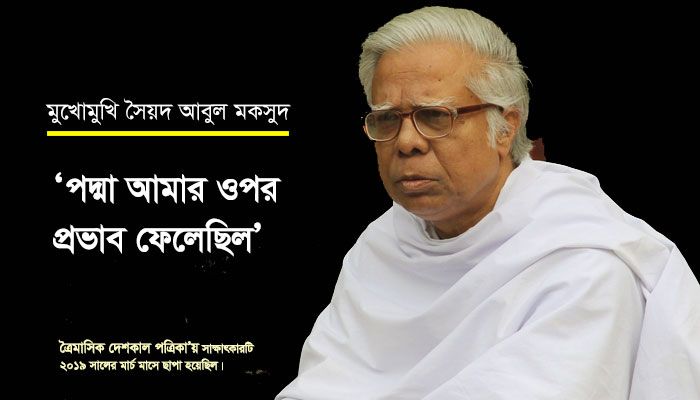
আনোয়ার পারভেজ হালিম
প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ০৭:৫২ পিএম
আপডেট: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ০৭:৫৭ পিএম
প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ০৭:৫২ পিএম
আনোয়ার পারভেজ হালিম
আপডেট: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ০৭:৫৭ পিএম
লেখক, গবেষক, সাংবাদিক ও কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি না ফেরার দেশে চলে গেলেন। উত্তাল রাজনীতির সংস্পর্শে কেটেছে তাঁর কৈশোর আর যৌবন। দেখেছেন ব্রিটিশদের বিদায়, পাকিস্তানের জন্ম ও দুঃশাসন, অতপর একাত্তর এবং বাংলাদেশ। তাঁর দেখা সেই সময়কার সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তিনি। ত্রৈমাসিক দেশকাল পত্রিকা’য় সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিল ২০১৯ সালের মার্চ মাসে। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আনোয়ার পারভেজ হালিম ।
আপনার মা-বাবা, ভাই-বোনসহ পরিবারের কথা বলুন।
আমার জন্ম ১৯৪৬ সালের ২৩ অক্টোবর। সেই সময় উপমহাদেশে হিন্দু- মুসলিম দাঙ্গা চলছিল। আমার জন্ম হওয়ার কথা ছিল কলকাতায়। আমার মা ছিলেন ভারতের উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী। তারাও ১৯২৫ সালে এই দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচার জন্য ফয়েজাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। আমার নানা কলকাতাতেই সেটেল হয়েছিলেন। ছেচল্লিশের দাঙ্গার কারণে মা আর কলকাতায় যেতে পারেননি। যে কারণে আমার জন্মও ওখানে না হয়ে এদেশে হয়েছে। আমার বাবা এখানেই থাকতেন। তিনি মাঝে মাঝে কলকাতা যেতেন।
আমি ছিলাম মায়ের প্রথম সন্তান। এরপর আমার একটি বোনের জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা যান। যে কারণে মা উর্দুভাষী হলেও আমি কিন্তু উর্দু জানি না। আমার মা-ও বাংলা বলতে পারতেন না। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তবে চাচাতো ভাই-বোন ছিল আটজন। তারা সবাই ছিল আমার বড়। আমরা সবাই এক পরিবারেই ছিলাম। আমাদের বাড়ি মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার এলাচিপুরে। এ গ্রামটা আরিচাঘাটের কাছেই।
এলাচিপুরে তো সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নানার বাড়ি...
হ্যাঁ, তার নানার বাড়িও ছিল এই গ্রামে। আমার দাদার দিক থেকে উনারা আমাদের আত্মীয় হন। যা বলছিলাম, এলাচিপুরের সেই বাড়িটা কিন্তু নেই। ভাঙনের কারণে নদীতে চলে গেছে। আমার শৈশবে যে পদ্মা দেখেছি, সেটা ছিল সমুদ্রের মতো বিশাল এক উত্তাল নদী। ভাঙতে ভাঙতে নদীটা একেবারে আমাদের বাড়ির খুব কাছে চলে এসেছিল। ৫/৬ বছর এভাবে ছিল। তারপর বাড়িটা নদীর গর্ভে চলে যায়।
আমার শৈশব খুবই একাকিত্বে কেটেছে। একে তো মা ছিল না- তার উপর ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তারপরই হলো দেশব্যাপী বন্যা। বাড়ির সামনে বিশাল পদ্মা নদী- এখন মনে হয়, এসব কিছু আমার উপর প্রভাব ফেলেছিল।
পঞ্চাশ সালের বন্যাটা ছিল ভয়াবহ। এই বন্যার মধ্যেই আসামে হয়েছিল ভূমিকম্প। ফলে আসাম থেকে প্রচুর কাঠ ভেসে ভেসে পদ্মায় এসেছিল। শুধু কাঠই নয় এর সঙ্গে গরু, ভেড়া, মহিষ, হাতি এমনকি মানুষের লাশ ভেসে যেতে দেখেছি। মানুষের জীবন সম্পর্কে আমার উপলব্ধি, ফিলোসফি অব লাইফ- সেটা ওই সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বন্যা, দারিদ্র্য এসব থেকে এসেছে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে দেশে বন্যা হয়েছে। বন্যায় মানুষের ভয়াবহ দুর্ভোগ দেখেছি, যা আমার জীবনে প্রভাব ফেলেছে। এখনো বন্যা ও নদী ভাঙন দেখলে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বলতে পারেন পঞ্চাশের দশকেই তৈরি হয়েছে।
আপনার শৈশবের কথা আরও জানতে চাই।
আমার বাবা তখন ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ডসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি সারাদিন বাইরে থাকতেন। সে সময় শিবালয়ে অনেক বড় লঞ্চঘাট ছিল। সেখানে বড় বড় স্টিমার ভিড়তো। গোয়ালন্দ থেকে শিবালয়, সেখান থেকে মুন্সীগঞ্জ হয়ে নারায়ণগঞ্জে স্টিমার যেত। দু’টো স্টিমারের নাম মনে আছে- একটা ছিল অস্ট্রিচ এবং আরেকটা ছিল কিউই। অনেক বড় স্টিমার এক একটায় এক হাজার লোক ধরতো।
আমার বাবা যেহেতু একজন স্থানীয় নেতা ছিলেন, আর ওই পথে যেসব নেতা যাতায়াত করতেন- ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, এমনকি ভারতের তখনকার বড় বড় নেতারাও- তারা শিবালয় ঘাটে নামতেন। আব্বা তাদেরকে ডাব-টাব খাওয়াতেন। আমিও আব্বার সাথে ঘাটে যেতাম। ওই বয়সেই আমি বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের দেখেছি।
তখনকার দিনে গ্রামে রোজকার পত্রিকা রোজ পাওয়া যেত না। ফলে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি, ভাষা অন্দোলনের খবর ২/১দিন পর আমরা জানতে পারি। বাবাকে দেখলাম ভীষণ গম্ভীর হয়ে আছেন। তিনি ‘হাইলি শক্ড’ ছিলেন। শহীদ রফিক ছিলেন মানিকগঞ্জেরই ছেলে। বাবা রফিককে নিয়ে ১৬ পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকা ছেপেছিলেন। কবিতার পুস্তিকা ছিল সেটা। আর আমরা না বুঝেই স্লোগান দিতাম- ‘নূরুল আমিনের মুণ্ডু চাই, কল্লা চাই’, ‘নূরুল-নাজিম ভাই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই’। আসল ব্যাপারটা কী, তা কিন্তু বুঝতাম না। মজার ব্যাপার, ওই পুস্তিকা ছাপার কাজে আমি প্রথম ঢাকায় আসি। এই প্রথম স্টিমারে চড়ে আমার ঢাকায় আসা। এটা বায়ান্নর মার্চ মাসের শেষ দিকের কথা। ঢাকার বাংলাবাজার থেকে বইটা ছাপা হয়েছিল।
ঢাকা দেখার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, কী কী দেখলেন?
তখনকার ঢাকা এখন কল্পনাও করা যাবে না। লালবাগে আমাদের বাসা ছিল। সেখানে আমার কাজিনরা থাকতেন। সদরঘাট থেকে রিকশায় লালবাগে গিয়েছিলাম। আমার কাছে সেটা ছিল এক মহাএলাহি কাণ্ড। আমার মনে হয়েছিল- কী এক আধুনিক বাহনে উঠেছি! তখন বাস চলতো, সেটাকে বলা হতো টাউন সার্ভিস। সেই বাস সদরঘাট থেকে চকবাজার-লালবাগ হয়ে এখনকার ইডেন কলেজের কোনা দিয়ে এসএম হল-মেডিক্যাল কলেজ-কার্জন হলের সামনে দিয়ে ঘুরে গুলিস্তান হয়ে আবার নবাববাড়ি যেত। এই বাসকে আমার মনে হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক বাস। এটা ছিল বায়ান্ন সালের অভিজ্ঞতা।
আপনার স্কুলজীবন কেমন ছিল?
এরমধ্যে আমি কিন্তু কোনো স্কুলে ভর্তি হইনি। যদিও স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন আমার বাবা। কিন্তু তিনি আমাকে স্কুলে যেতে দেননি। একদিন স্কুলে গিয়েছিলাম। তখনকার স্যাররা বেত দিয়ে পেটাতেন। ওই বেত দেখে স্কুলে যাওয়ার আর আাগ্রহ হয়নি। বাড়িতে ২/৩ জন শিক্ষক ছিল তাদের কাছেই পড়তাম।
এর মধ্যে চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন এসে গেল। আমার বাবা ফজলুল হক সাহেবের কৃষক-প্রজা পার্টি করতেন। বাবা মওলানা ভাসানীর ভক্ত হলেও যে কারণেই হোক সমর্থক ছিলেন ফজলুল হকের। আমাদের আসনে সেবার যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন আব্দুল লতিফ বিশ্বাস। উনি ছিলেন এখনকার বিএনপি নেতা এমকে আনোয়ারের শ্বশুর। আমরা তাকে চাচা ডাকতাম। তখন নির্বাচনী প্রচারণায় ওদিকে গেলে স্থানীয় নেতাদেরকে শিবালয়ে যেতে হতো। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হককে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম। এ সময় শেখ সাহেবকেও প্রথম দেখি। তখনও উনি বড় নেতা হয়ে ওঠেননি। সে সময় তিনি রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। শেখ সাহেব নদীর ওই পারের মানুষ হওয়ায় আমরা তাকে কাছের মানুষ মনে করতাম। যদিও তার তুলনায় ইউসুফ আলী চৌধুরীর (মোহন মিয়া) সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। এভাবে ছোটবেলা থেকেই আমি রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছি।
শিবালয়ের তেওতায় মানিকগঞ্জ জেলার প্রথম হাইস্কুল, যা তেওতা হাইস্কুল- আমার দাদা ছিলেন সেই স্কুলের অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টার। তাঁর সূত্রে আমাদের বাড়িতে প্রচুর বই ছিল। নাইনটিনথ সেঞ্চুরির সব পত্র-পত্রিকা আমাদের বাড়িতে আসতো। কমপ্লিট ওয়ার্কস অব বঙ্কিম চন্দ্র, কমপ্লিট ওয়ার্কস অব রমেশ চন্দ্র দত্ত, তারপর গিরিশ চন্দ্রসহ সবার বই ছিল। যেহেতু আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ শিশু- রাতের বেলা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আব্বা আমাকে বই পড়ে শোনাতেন।
আপনাদের ওই এলাকায় একসময় হিন্দু জমিদারি ছিল, জমিদাররা কি তখনও ছিল, নাকি ওপারে চলে গিয়েছিল?
আমাদের এলাকার জমিদার ছিলেন তেওতার কিরণ শঙ্কর রায়। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের নেতা। আটচল্লিশে তিনি ভারতের মন্ত্রী হয়েছিলেন। মন্ত্রী হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য তিনি মারা যান। তাঁর সঙ্গে আমার বাবার ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাবা মাঝে মাঝে ৫০/৬০টা পাঙ্গাশ-ইলিশ মাছ নিয়ে কলকাতায় কিরণ শঙ্করের বাড়িতে যেতেন।
সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হলে, জমিদাররা এ দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়। তখন দখলদারিত্বের কোনো ব্যাপার ছিল না। দুই দেশের মধ্যে যার যার সম্পত্তি এক্সচেঞ্জ হতো। শান্তিপূর্ণ বিনিময় হতো। পঞ্চাশের দাঙ্গার পর হিন্দুরা সব হিড় হিড় করে চলে গেল। কেন যাচ্ছে তখন আমি ভালো করে বুঝতাম না।
সেই তেওতার জমিদারবাড়িতে একটা বিরাট লাইব্রেরি ছিল। শেষবার পঞ্চাশের দাঙ্গার পর জমিদারের পরিবার যখন চলে যায়, তখন দুই/তিন আলমারি বই আমার বাবাকে দিয়ে যান। এর মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের ক্ল্যাসিক বই ছিল। ল’এর বই বেশি ছিল। আমার মনে আছে, জমিদার বাবাকে বলেছিলেন, ‘তোমার ছেলেকে আইন পড়িও, বইগুলো রেখে গেলাম, কাজে লাগবে।’
আমার বাবাও ছিলেন বইয়ের পোকা। কাজিনরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তারাও বই পড়তেন। এখান থেকে আমার বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আবারও বলছি- নিজের বিষণ্ণতা, উত্তাল নদী, বন্যা, তারপর দুর্ভিক্ষ, দরিদ্র- মানুষের যে করুণ আহাজারি দেখেছি, সেসব আমার ওপর ভীষণ ছাপ ফেলেছে। এখনও নদীভাঙা মানুষ, কিংবা রিলিফ নিতে আসা মানুষের দৃশ্য আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়।
এলাচিপুরে আপনাদের বাড়িঘর কি এখনও আছে?
আমাদের বাড়িঘর তখনই নদীভাঙনে চলে যায়। এরপর বাবা মানিকগঞ্জের ঝিটকায় গিয়ে বাড়ি করেন। আমি সেখানকার আনন্দমোহন হাইস্কুলে প্রথম ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার কাজিনরাও সেখানে ভর্তি হয়েছিলেন।
স্কুলের পড়াশোনা কেমন ছিল?
স্কুলটা খুব ভালো ছিল। পড়াশোনার মানও ভালো ছিল। কিন্তু আমি নিজে ছাত্র হিসেবে খুব খারাপ ছিলাম। আমাদের স্কুলের তখনকার হেডমাস্টার ছিলেন কালী প্রসাদ ভৌমিক। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও ব্যক্তিত্বের কাছে বাংলাদেশের এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো ভাইস চ্যান্সেলরই যোগ্য নন। ওই স্কুলের পাঠাগারটিও ছিল খুব সমৃদ্ধ।
আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি, কবিতা-টবিতা লিখি, ছাপাও হয়েছে কিছু। তখন স্কুলের পাঠাগারের জন্য একজন সহকারী দরকার ছিল। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার বললেন, ‘আলমারির চাবিটা তোর কাছে থাক।’ ৭/৮টা আলমারিতে ইংরেজি সাহিত্যের বইসহ সব ধরনের বই ছিল। এটা আমার জীবনের ভিত্তি তৈরিতে সাহায্য করেছে। মানুষের জীবনের ভিত্তিটা কিন্তু শৈশবেই তৈরি হয়ে থাকে। আমাদের স্কুলের শিক্ষকরা ছিলেন ভীষণ রকম আদর্শবাদী। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রায় সবাই গরিব ছিলেন। শীতকাল ছাড়া প্রায় সবাই খালি পায়ে স্কুলে যেতাম। আমাদের পারিবারিক অবস্থাও তখন ভালো ছিল না। তখন পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো বাহাদুরি ছিল না। কিন্তু বই পড়ার প্রতি আকর্ষণ ছিল। আমার জন্মের পর থেকে দেখেছি, মা যতদিন বেঁচে ছিলেন কলকাতা থেকে বাড়িতে স্টেটসম্যান পত্রিকা এবং উর্দু পত্রিকা আসতো।
রাজনীতির সংস্পর্শে আসলেন কি স্কুলে থাকতে?
স্কুল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শেষ দিকে সম্ভবত ১৯৬১ সালের কথা। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন বড় নেতা ছিলেন খোকা রায়, অনিল মুখার্জী ও জ্ঞান গুহরা। আমাদের এলাকার এক হিন্দু বাড়িতে রাতের বেলা যতদূর মনে পড়ে- অনিল মুখার্জী কয়েকজন নেতা-কর্মীসহ এসেছিলেন। আমরাও কয়েকজন সেখানে ছিলাম। মূলত আমাদের সবক দেয়ার জন্য তারা সেখানে এসেছিলেন। রাশিয়ার বিপ্লব এবং বিপ্লব পরবর্তী সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে উনি আলোচনা করেন। কমিউনিজম, মার্ক্সিজম সম্পর্কে খুব সহজ কথা বললেন। তার কাছে জানলাম রাশিয়ায় নাকি কোনো গরিব নেই, সব পাল্টে গেছে। আরও জানলাম, চীনে নাকি সব মানুষ খেতে পাচ্ছে। কেউ না খেয়ে থাকে না। আমার কাছে তার কথাগুলো ভালো লাগলো।
এরমধ্যে চৌ এন লাই ঢাকায় এসেছিলেন। বাবা বললেন- চলো, ঢাকায় গিয়ে চৌ এন লাইকে দেখে আসি। সত্যি সত্যি বাবার সঙ্গে ঢাকায় এলাম। এখনকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চৌ এন লাইকে দেখলাম। এভাবে বাবার সঙ্গে আমি ইংল্যান্ডের রাণীকে দেখতেও ঢাকায় এসেছিলাম। যা বলছিলাম, অনিল মুখার্জীর কাছে রাশিয়া আর চীনের গল্প শুনে আমি কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। ভাবলাম- খারাপ তো নয়, এদের সঙ্গে থাকতে হবে। এনিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। তখনও আমি মার্ক্সবাদের বই-টই পড়িনি। আমার আরও ভালো লেগেছে, যারা কমিউনিজমের কথা বলতো, তারা একেবারে সাধারণ মানুষ। ভালো একটা জামাও পরে না। সারা বছর প্রায় ৬০ ভাগ লোক খালি গায়ে থাকে।
এরমধ্যে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন শুরু হলো। আমরা রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রণো এসব নেতাকে অনুসরণ করতাম। আমাদের বাসা ছিল লালবাগে। এর ঠিক উল্টোদিকে ছিল মেনন ভাইয়ের স্ত্রী বিউটি আপাদের বাসা। তখনো তাদের বিয়ে হয়নি। বিউটি আপার বাবা কেরামত আলী সাহেব ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। এই কেরামত আলী, আমার কাজিনরা এবং আমি মিলে তখন লালবাগে একটা লাইব্রেরি করেছিলাম। নাম ছিল গ্রন্থ বিতান- লালবাগ শাহী মসজিদের কাছেই, এখনও সেটা আছে। বেশ সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। সেই সময় বিউটি আপার দু’জন মামা এসেছিলেন খুলনা থেকে। ওনারা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির লোক। ওনারা খুলনা থেকে আসলেই রাতের বেলা বাসায় বসে আমাদের সঙ্গে কমিউনিজম নিয়ে আলোচনা করতেন এবং বুঝাতেন।
ঢাকায় এসে কলেজে ভর্তি হলেন?
হ্যাঁ, ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান আমাদের শিক্ষক ছিলেন। আমার তখন একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল- ছুটির দিনে বড় বড় মানুষদের দেখার জন্য তাদের বাড়িতে ছুটে যেতাম। কবি জসীমউদ্দীন, কুদরত-ই-খুদা, মনসুরউদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, অর্থাৎ ওই সময়ে যারা বিখ্যাত, যাদের বয়স ষাটের ওপরে, এ ধরনের মানুষদের সঙ্গে দেখা করতাম। এভাবে কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয়।
আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। টাঙ্গাইলের ব্যারিস্টার শওকত আলী খানসহ কয়েকজন মিলে গঠন করলেন পাকিস্তান সোশ্যালিস্ট পার্টি। শওকত আলী ছিলেন দলের সভাপতি। নতুন দলটির অফিস ছিল শেখ সাহেব বাজারে। এ দলের ছাত্র সংগঠনের নাম দিলেন ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট ফোরাম। আমাকে করা হলো এ ফোরামের কনভেনর। আমাদের ধারণা ছিল- ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের বাইরে গিয়ে কিছু একটা করবো। কিছুদিন চেষ্টাও করলাম। শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো না। দু’বছরের মাথায় ১৯৬৪ সালের দিকে শওকত আলীর পার্টি বিলীন হয়ে গেল।
এসবের পাশাপাশি আমি পত্রিকায় কাজ করতাম। মওলানা ভাসানীর পত্রিকা। অর্থ যোগাতেন ব্যারিস্টার শওকত আলী। সম্পাদক ছিলেন আনোয়ার জাহিদ। পত্রিকাটির নাম ছিল সম্ভবত ‘নতুন দিন’, ঠিক মনে পড়ছে না- ‘নতুন কথা’ও হতে পারে।
ওই সময় একটা দাঙ্গা হয়েছিল...
১৯৬৪ সালে শুরু হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আমরা তখন ভলান্টিয়ারের কাজ করেছি। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, মহল্লার হিন্দু বাড়ির আশেপাশে আমরা পাহারা দিয়েছি। এর মধ্যে আব্দুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহাসহ আরও বড় বড় ১৫/১৬ জন নেতা চীনপন্থী কমিউনিজমকে সামনে নিয়ে এলেন। বলা হলো- সোভিয়েতের কমিউনিজম দিয়ে বিপ্লব হবে না।
ভিক্টোরিয়া পার্কের দক্ষিণ পাশে ব্যারিস্টার শওকত আলীর বাড়িতে একদিন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি ইতিমধ্যে চীন থেকে দুইবার ঘুরে এসেছেন। তিনি মাও সে-তুঙ-এর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। এটা আমাদের জন্য ছিল থ্রিল! মওলানাকে মাও সে-তুঙ পিকআপ করেছেন। মাও সে-তুঙ বুঝেছিলেন যে, ভাসানী যেহেতু কৃষকদের সঙ্গে ৬০ বছর ধরে আছেন, সুতরাং ‘হি ইজ দ্য রাইট পারসন’। বিপ্লব হবে কৃষকদের মাধ্যমে।
ভাসানী আমাদের জানান, মাও সে-তুঙ তাকে বলেছেন যে, ‘মওলানা, আপনি তো কৃষকদের নেতা। আপনাদের শ্রমিক নেই- কৃষক আছে। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের জন্য এখনও আপনারা প্রস্তুত নন। এজন্য আপনাদের আরও সময় লাগবে।’
ভাসানীর ভাষ্য মতে, আইয়ুব খান মাও সে তুঙকে বলেছেন, তিনি ইস্ট পাকিস্তানে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন। ইস্ট পাকিস্তানের জন্য অর্থ বরাদ্দও বাড়াবেন। রাস্তাঘাট বানাবেন। কলকারখানাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবেন। কারণ, ইস্ট পাকিস্তানে ভূমিহীন কৃষক বেশি। তাদের কর্মসংস্থান করতে হলে ডেভেলপমেন্ট দরকার।
ভাসানী আমাদের জানান, মাও সে তুঙ তাকে বলেছেন- ‘মওলানা, আপনারা আইয়ুবকে বাধা দেবেন না। বাধা দিলে আপনাদের উন্নয়ন হবে না। কৃষকের উন্নতি হবে না। বরং রাস্তাঘাট হলে কৃষিজাত পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরবরাহে সুবিধা হবে। কলকারখানা হলে ভূমিহীন কৃষকেরা শ্রমিকের চাকরি পাবে এবং এক সময় তারাই আন্দোলনে শক্তি যোগাবে। তাছাড়া, ইস্ট পাকিস্তানে চীনের মতো জনসংখ্যা যেহেতু বেশি, সুতরাং এখানে বিপ্লব হবেই। সে জন্য সবার আগে আপনাদের দরকার উন্নয়ন।’
এরপর ভাসানী আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘রাশিয়ার পক্ষে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়। আর তোমরা আইয়ুবকে গালাগাল না করে কৃষকদের নিয়ে সংগঠিত করো।’ ভাসানীর সেদিনকার কথাগুলো আমার ভালো লেগেছিল।
এরমধ্যে ছাত্র ইউনিয়নেও ভাঙন ধরে। মেনন ও রণো ভাইরা মস্কোপন্থা থেকে সরে আসে। আব্দুল হক, তোয়াহা, আলাউদ্দীন, আব্দুল মতিনরাও ভাসানীর মতামতকে গুরুত্ব দেন। রুশ কমিউনিজমের প্রতি তাদের মোহ কমেছে। মওলানা ভাসানী বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করে বেড়াচ্ছেন। ১৯৬৮ সালের দিকে খুব অল্পদিনের মধ্যে চীনপন্থী বিপ্লবীরা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এদিকে বোঝা যাচ্ছিল যে, আইয়ুব খান চিরস্থায়ী ক্ষমতায় থাকার পাঁয়তারা করছে।
এ সময় আব্দুল মতিনদের গ্রুপের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এরা ছিল আরও বেশি বিপ্লবী। চারু মজুমদারের লাইনে এরা দ্রুত বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্ন দেখে। এদের একটা গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি গঠন করে। তখনকার ছাত্রনেতারা ছিল খুবই ডেডিকেটেড এবং স্কলার, এখনকার ছাত্র নেতাদের মতো নয়। আমিও এই কৃষক সমিতির সঙ্গে কাজ করতে লাগলাম। কিন্তু ১৯৬৮ সালে এসে মতিন ও আলাউদ্দীনরা হত্যার রাজনীতি বেছে নেয়। চারু মজুমদারের লাইন মানে নকশাল। আমিও তাদের সঙ্গে ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ এলাকায় কয়েক মাস কাজ করেছি। আমি তখন কৃষি বিভাগে তথ্য কর্মকর্তার সরকারি চাকরি নিই এবং আব্দুল হক ও তোয়াহার পরামর্শে ওই এলাকায় থাকি। চাকরিটা মুখ্য ছিল না, এর আড়ালে রাজনীতি করাই ছিল উদ্দেশ্য। বছরখানেক পর ওই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।
আমার বাসায় তখন এই বিপ্লবীরা এসে থাকতো। জোতদার খতমের নামে তারা অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলো হত্যাকা- ঘটায়। কর্মীরা প্রায়ই এসে খুনখারাবির গল্প করতো। বিষয়টা আমার কাছে একেবারে ভালো লাগেনি। কারণ, আমি মূলত সাহিত্যের লোক। রেডিওতে অনুষ্ঠান করছি। লেখালেখি করছি। রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান- আমরা সবাই তখন সমাজ পরিবর্তনের জন্য লেখালেখি করছি। এরমধ্যে খুনখারাবির কথা শুনে আমার ভীষণ খারাপ লাগতো। আসলে বলতে চাচ্ছি, চারু মজুমদারের লাইন আমার একেবারেই পছন্দ ছিল না।
কিছুদিন পর ১৯৭০ সালে এই নকশালপন্থীরাও ভাগ হয়ে যায়। একদিকে হক-তোয়াহা, আরেকদিকে মতিন-আলাউদ্দীনরা। বাঙালি যে কত অপরিণামদর্শী, সেটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারলাম। বাস্তবতার সঙ্গে কোনো মিল নেই- তারা এমন সব হটকারি সিদ্ধান্ত নিতো। তাদের এই বিভক্তি আমার পছন্দ হয়নি। ভাসানীও বললেন যে, ‘ওরা ভুল করলো। ওরা আমাকে আরও কছুদিন ব্যবহার করতে পারতো।’ যেহেতু, এ দেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, তাই মওলানা ভাসানী ইসলামিক সোস্যালিস্ট মুভমেন্ট করতে চেয়েছিলেন। মাও সে তুঙ তাকে বাধা না দিয়ে বলেছিলেন, ‘ঠিক আছে আপনার বিশ্বাসে আমি বাধা দেবো না। কিন্তু আপনি কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন।’ হক-মতিনরা যখন বেরিয়ে যান, তখন তারা ভাসানীর সমালোচনা করেছিলেন। এটাও ছিল তাদের চরম হটকারী কাজ।
ওই সময়ে তো পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনও তুঙ্গে ওঠে...
এরমধ্যে শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা দিয়ে ফেলেন। তার পার্টি কখনোই আমরা করতাম না। কিন্তু ছয় দফা ঘোষণার পর মুজিবের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মে। আমার মনে হলো, ছয় দফা খারাপ তো না, আমাদের তো স্বায়ত্তশাসনও দরকার। অর্থাৎ আমি মনে করলাম, দুই ধারার আন্দোলনই চলতে পারে। একটা হলো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অটোনমি মুভমেন্ট, আরেকটা হলো মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সোস্যালিস্ট মুভমেন্ট। আওয়ামী লীগের নীতি-নৈতিকতা যা-ই থাক না কেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর শেখ মুজিবের প্রতি আমার অন্যরকম উপলব্ধি জন্মালো।
১৯৭০ সালের নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসতে থাকলো, জনগণ বুঝতে পারলো যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতবে এবং ক্ষমতায় যাবে। নির্বাচন নিয়েও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। এ সময় ভাসানীর সঙ্গে শেখ সাহেবের একটা বোঝাপড়া হয়। মওলানা ভাসানী চেয়েছিলেন, শেখ মুজিব অন্তত একবার কেন্দ্রের ক্ষমতায় যাক। বেশিদিন হয়তো থাকতে পারবেন না। ছয় দফা হয়তো বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কিছু তো আদায় করতে পারবেন। এ কারণেই ভাসানী মুজিবকে সমর্থন দিয়েছিলেন।
আরেকটি বিষয় বলে রাখি, স্বাধীনতার কথা কিন্তু মুজিব প্রথমে বলেননি। মওলানাই প্রথম স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। তিনি দক্ষিণবঙ্গ সফর শেষে ঢাকায় ফিরে ঘোষণা দিলেন, ‘ইন্ডিপেনডেন্ট ইস্ট পাকিস্তান জিন্দাবাদ’, ‘ভোটের বাক্সে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো’। মুজিবও এ ব্যাপারে ভেতরে ভেতরে মওলানাকে সমর্থন করতেন। মওলানার লক্ষ্য ছিলÑ স্বাধীনতার প্রশ্ন তুললে পশ্চিম পাকিস্তানিরা দ্রুত মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।
আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জেতার পর বাম দলগুলো ভিন্ন পন্থা নিলো। তারা আওয়ামী লীগের ছয়দফার চেয়েও আরেক ধাপ এগিয়ে জোর গলায় স্বাধীনতার কথা বলতে লাগলো। আমরা যারা প্রগতিশীল লেখক ছিলাম, যেমন- আহমদ শরীফ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, ফরহাদ মজহার, হুমায়ুন কবির, আরও অনেকে মিলে আমরা বিভিন্ন লেখালেখি, সভা-সেমিনারে স্বাধীনতার প্রসঙ্গটিকে সামনে নিয়ে এলাম।
তারপরও তো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো...
ইয়াহিয়া যখন ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা করলো, তখন পূর্ব পাকিস্তানে দল-মত নির্বিশেষে দ্রুত একটা ঐক্য গড়ে ওঠে। আমার এখনও মনে আছে- শেখ মুজিব ছিলেন পূর্বাণী হোটেলে। আমি তখন বদরউদ্দীন উমরের ‘গণশক্তি’ পত্রিকায় কাজ করি। আমার অফিস ছিল দৈনিক বাংলার মোড়ে। ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর মুজিব রাস্তায় নেমে এলেন। দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ স্রোতের মতো রাস্তায় নেমে এসেছে। সবার একটাই দাবি স্বাধীনতা চাই। আমার এক আত্মীয় চাকরি করতেন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে। তিনি একটা কাগজে হাতে লিখলেন- ‘বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স’ এবং সেটা পিআইএ’র অফিসে লাগিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ডেকে এ বিষয়ে একটা প্রেস রিলিজ তৈরির জন্য বললেন। ২৫ মার্চ পর্যন্ত এভাবে মিছিল-মিটিং চলতে থাকলো। তারপর তো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।
সাংবাদিকতা পেশায় এলেন কীভাবে?
আমার বাবা চাকরি-বাকরি পছন্দ করতেন না। বাবার এই বৈশিষ্ট্য আমার ভেতরেও ছিল। ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুন মেনে চলা আমার পছন্দ ছিল না। কৃষি বিভাগের চাকরিটা কয়েক মাস করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সে সময় আহমেদ রফিক ‘নাগরিক’ নামে একটা প্রগতিশীল পত্রিকা বের করতেন। আমিও ওই পত্রিকার সঙ্গে ছিলাম। তারপর ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে আমি একটা টেডেল মেশিন কিনে ছাপাখানা দিলাম। নাম দিলাম আদর্শলিপি। ওটা ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের পেছনে, কমলাপুরে। চারজন কর্মচারী ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল- একটা সাহিত্য পত্রিকা বের করবো।
একদিন দৈনিক পূর্ব পাকিস্তানের আহমেদ হুমায়ুন বললেন, ‘ছাপাখানা দিয়েছেন, আপনার তো কাজ দরকার। আমার কিছু পত্রিকা বাঁধাই করে দেন।’ উনার সারাজীবনের সংগ্রহে থাকা দেশ পত্রিকা আমাকে বাঁধাইয়ের জন্য দিলেন। আমি বললাম, হুমায়ুন ভাই আপনার পত্রিকা বাঁধাই করে দেবো, তবে একটু সময় লাগবে। আমি ওগুলো পড়ার পর বাঁধাই করবো। আমি সেই দেশপত্রিকা প্রেসে বসে পড়তাম। এরপর তো ২৫ মার্চ যুদ্ধ লেগে গেল। সারারাত প্রেসেই কাটালাম। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ২৬ মার্চ আকাশ বাণীর দুইটার সংবাদ শুনি। কিন্তু খবরে কিছুই বললো না। আমার মনে আছে- ঘোষক ছিলেন অনিল চট্টোপাধ্যয়। খবর শেষ হওয়ার পর তিনি হঠাৎ বললেন, ‘বিশেষ ঘোষণা। পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে।’
প্রেসের কাছেই ছিল কবি জসীমউদ্দীনের বাড়ি। দৌড়ে গেলাম তাঁর বাড়িতে। উনি বললেন, ঢাকায় থাকা ঠিক হবে না। বাড়ি চলে যাও। তারপর আত্মীয়-স্বজন মিলে না খেয়ে নবাবগঞ্জ হয়ে হাঁটতে হাঁটতে মানিকগঞ্জে গ্রামের বাড়ি গেলাম। জুন মাসে খবর পেলাম প্রেস লুট হয়ে গেছে।
যুদ্ধ চলাকালে দেশেই ছিলেন?
৩০ মার্চে আমরা ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরীর বাড়িতে গেলাম। উনি আমার বয়সী সব তরুণ-যুবকেদের নিয়ে বসলেন। উনি আমাদের যদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন। এসময় ২/৩ দিন ধরে রেডিও-তে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা বার বার হচ্ছিল। ২৭ তারিখ তো স্পষ্ট তাঁর ঘোষণা শুনেছি। উনি ঘোষণায় বলেছিলেন- ‘শেখ মুজিব আমাদের সঙ্গে আছেন।’
আমরা মানিকগঞ্জেই ছিলাম। নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আমার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে আগস্ট মাসের দিকে তাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আসি। জীবিকার জন্য একসময় আমি ইস্ট পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের যে জার্নাল বের হতো, সেটায় কাজ করতাম। এজন্য বড় বড় ডাক্তারদের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। বাবাকে মেডিক্যালে ভর্তি করে একদিন ডা. আহমেদ রফিকের বাসায় যাই। সেখানে এক যুবকের দেখা পেলাম। তাকে আগে চিনতাম না। জানলাম তাঁর নাম ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তিনি এবং ডা. মবিন পড়াশোনা ক্ষান্ত দিয়ে লন্ডন থেকে এসে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। তারা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি হাসপাতাল করেছেন। ঢাকায় এসেছেন ওষুধ নিতে। জানতে পারলাম আহমেদ রফিক, ডা. ফজলে রাব্বি, ডা. আলীম আরও কয়েকজন চিকিৎসক মিলে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ওষুধ সংগ্রহ করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠান। সম্ভবত এই বিষয়টা গোয়েন্দারা জেনে গিয়েছিল। কারণ, ডা. ফজলে রাব্বি এবং ডা. আলীমকে পরবর্তীতে আলবদরা ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল।
স্বাধীনতার পর কাজ শুরু করলেন কোথায়?
দেশ তো স্বাধীন হলো। ঢাকা তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে। এদিকে প্রশাসন গোছানোর জন্য ভারতীয় আমলারাও এসেছে। তারা পূর্বাণী হোটেলে উঠেছিল। একজন ভারতীয় কর্নেল আমাকে বললেন, ‘পূর্বাণীতে আসো। ওখানে আমরা একটা প্রেস সেল করবো।’ আমি ওই সেলে কিছুদিন কাজ করেছি। ওটা ছিল টেম্পোরারি। ফয়েজ আহমেদ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার দায়িত্ব নিয়েছেন। গেলাম সেখানে। উনি বললেন, ‘তুমি পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনালে (পিপিআই) যোগ দাও। পিপিআই ছিল সরকারি বার্তা সংস্থা। সালমান রহমানরা ওটার শেয়ার ছিল। স্বাধীনতার পর পিপিআই হলো বিপিআই। আমি এবং বেবি ইসলাম মিলে বিপিআই’তে কাজ শুরু করলাম। সরকারই বেতন দিত। কিছুদিন পর তথ্য মন্ত্রণালয় বিপিআই বন্ধ করে দিয়ে স্টাফদের বাসসে চাকরি দেয়। সেই থেকে বাসসে চাকরি করেছি।
বাসস ছাড়লেন কেন?
২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি বইমেলায় সন্ত্রাসীরা লেখক হুমায়ুন আজাদকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। এ নিয়ে আমি প্রথম আলোতে লিখি। তখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন তরিকুল ইসলাম। তিনি এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী বিষয়টি ভালোভাবে নেননি। ওনারা ফোন করেন বাসসের প্রধান সম্পাদক গাজীউল হাসান খানকে। গাজীউল হাসান লন্ডন থেকে এসে সবে বাসসে যোগ দিয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ‘মকসুদ ভাই, আপনার লেখা আমি পড়ি। ভালো লেখেন। কিন্তু কলাম লেখা বন্ধ করলে হয় না?’
আমি বললাম, একঘণ্টা পর জানাচ্ছি। এ সময় টাইপিস্টকে দিয়ে পদত্যাগপত্র টাইপ করালাম। তারপর সেটা দিয়ে চলে এলাম। এরপর আর বাসসে যাইনি। এরপর থেকে পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখছি। মাঝে মাঝে টেলিভিশনে টক শো’তে অংশগ্রহণ করি।
আপনি এই যে সাদা চাদর ও সাদা লুঙ্গি পরেন এর কারণটা কী?
ইরাকে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে পশ্চিমাদের পোশাক ত্যাগ করে সাদা চাদর আর সাদা লুঙ্গি পরা শুরু করলাম।
সাম্প্রতিক দেশকাল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন
বিষয় : সৈয়দ আবুল মকসুদ
© 2024 Shampratik Deshkal All Rights Reserved. Design & Developed By Root Soft Bangladesh