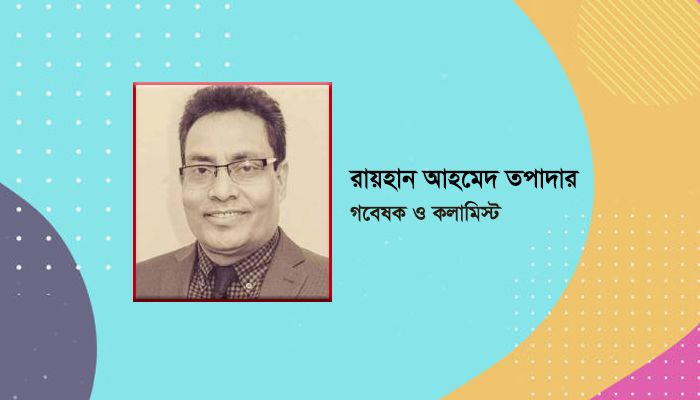
বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সমস্যা ও তার বিরূপ প্রভাব ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করায় সমগ্র মানবজাতি এখন শঙ্কিত। উন্নত বিশ্বে এসব সমস্যা উন্নয়নশীল দেশের সমস্যার তুলনায় ভিন্নতর এবং ভিন্নমাত্রার। সমস্যার এই ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের প্রতিই পরিবেশ সমস্যা হুমকি স্বরূপ। পাঁচ দশক আগে তোলা পরিবেশ বিজ্ঞানীদের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হচ্ছে। ৬০ দশকের শেষভাগে সুইডেনের স্টকহোমে আয়োজিত পরিবেশ বিজ্ঞানীদের প্রথম সম্মেলনে ওঠা উদ্বেগকে সত্যে পরিণত করতেই যেন উষ্ণায়নের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী বাড়ছে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উপকূলীয় নিম্নভূমি তলিয়ে যাচ্ছে সাগরে। আর এসবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো।
জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। আর এই ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো বরাবরই পরিবেশ দূষণের জন্য উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ অপরিকল্পিত কলকারখানার কথা বলে আসছে। তবে প্রশ্ন ওঠে, আসলেই কি উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী? উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতি এমনিতেই দীর্ঘদিনের উপনিবেশিক শাসনের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তাই উন্নত দেশগুলোকেই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে দায়িত্ব নিতে হবে। বাংলাদেশের মতো গরীব দেশের অর্থনীতি চাঙ্গাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। একইসঙ্গে জ্বালানি সক্ষমতা অর্জন, মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষা বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করতে হবে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, বাতাসে যদি এক শতাংশ ওজোন কমে যায় তাহলে, ২০৭৫ সালের আগে যারা জন্মাবে, তাদের ৩০ লাখ থেকে ১.৫ কোটি মানুষের চামড়ায় ক্যান্সার দেখা দেবে, ৫ লক্ষ থেকে ২৮ লক্ষ মানুষের নতুন করে চোখে ছানি পড়বে।
এমনকি এই ওজোন স্তর ঘটিত সমস্যা বর্তমানে বিজ্ঞানীদের ভরিয়ে তুলেছে। ১৯৩১ সালে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন আবিষ্কারের পর থেকে ব্যাপক ব্যবহার এবং আধুনিক ইলেকট্রনিক শিল্পে এর চাহিদা বেড়েছে। ১৯৮৬ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের উৎপাদন সমগ্র বিশ্বের উৎপাদনের ৭০ শতাংশ এবং ব্যবহারের ৫০ শতাংশ। এর ফলে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু প্রদেশের ওজোন স্তরে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। তবে আশার কথা ক্লোরোফ্লেুারো কার্বনের বিকল্প রাসায়নিকের উৎপাদন শুরু হয়েছে।সভ্যতার সবচেয়ে বড় সংকট হিসাবে দেখা দিয়েছে, শিল্পে ব্যবহৃত বর্জ্য পদার্থ। কোথায় ফেলা হবে এই বর্জ্য? যেখানেই ফেলা হোক না কেন, তার থেকে দূষণ ছড়াবেই। বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্য সৃষ্ট হয় জৈব রাসায়নিক শিল্পে। ১৯৩০ সালে যেখানে উৎপাদন ছিলো ১০ লাখ টন, ১৯৯০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫০ কোটি টন। এরপর প্রতিনিয়তই উৎপাদন বেড়ে চলেছে। এই সব বর্জ্য জমা হচ্ছে হ্রদে, পুকুরে, নদীতে, সাগরে। মানুষ এ যাবত ৭০ লাখ রাসায়নিক তৈরি করেছে। প্রতি বছর কয়েক হাজার নতুন রাসায়নিক আসছে। এদের মধ্যে ৮০০০ রাসায়নিক বিপজ্জনক। ১৯৯২ সালে ২৩০ কোটি গ্যালন শিল্পজাত বর্জ্যপদার্থ সাগরে ফেলা হয়। নিউইয়র্কের বর্জ্য ফেলার স্থান স্টটেন দ্বীপ, সেখানে প্রতিদিন ২২,০০০ টন বর্জ্য জমা হচ্ছে। আমেরিকার শিল্পজাত বর্জ্য প্রতি বছর ৫৬ কোটি টন মারাত্মক ক্ষতিকারক বর্জ্য সৃষ্টি করে। এই বর্জ্য পদার্থের মধ্যে অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক হল পারমাণবিক বর্জ্য। এ নিয়ে মানুষ কী করবে, জানেন না বিজ্ঞানীরা। পারমাণবিক চুল্লির জ্বালানি হল ইউরেনিয়াম। এই পদার্থটিকে যখন খনি থেকে তোলা হয় তখন রেডন নামে এক তেজস্ক্রিয় গ্যাস বিকিরণ করে যা শ্রমিকদের ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এবং ইউরেনিয়ামকে জ্বালানি দণ্ডের মাধ্যমে আণবিক চুল্লিতে প্রবেশ করানোর পর ভাঙন প্রক্রিয়ায় বিপুল তাপশক্তি ও অসংখ্য বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়।
এছাড়া বায়ু দূষণের পরিমাণের হিসাব নিকাশ করলে দেখা যায়, ব্রাজিলের রিও ডি শহরে জেনিরো ১৯৯২ সালে যে সম্মেলন হয়েছিল পরিবেশ নিয়ে তাতে আবহাওয়া নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সর্বশেষ জাপানের কিয়োটা শহরের সম্মেলনে চুক্তি হয়। চুক্তিতে ২০১২ সালের মধ্যে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে ফেলার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। এদিকে আমেরিকা ওই চুক্তিতে সই করেনি। বায়ু দূষণের জন্য বিজ্ঞানীরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতিকে দায়ী করেন। বিভিন্ন খনিজ জ্বালানি যেমন কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ালে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। হিসাব অনুযায়ী, বিগত একশ’ বছরে বাতাসে ২৫ শতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়েছে। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় প্রচুর সালফার-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশে। সালফার-ডাই-অক্সাইড বাতাসে থাকা অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এ দুই প্রকার অ্যাসিড বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস পায়, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পানির উৎসগুলো দূষিত হয়ে পড়ে। বায়ু দূষণের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, বায়ু দূষণের পরিমাণ না কমালে ২০৪০ সাল নাগাদ পৃথিবীর উষ্ণতা ৫০ সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাবে। তাতে মেরু অঞ্চলে বরফ গলবে, হিমবাহগুলো গলতে শুরু করবে, পানি স্তর ২-৩ ফুট বেড়ে যাবে। সমুদ্র উপকূলের শহরগুলো ডুবে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এমনকি আমেরিকার মায়ামি, ফ্লোরিডার মতো শহর ডুবে যাবে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার চেষ্টা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকের বা পরিবেশ সচেতন ব্যক্তিদের উদ্বিগ্ন হলে চলবে না। এ ব্যাপারে সবার সচেতন হতে হবে। বিশ্বের তাপমাত্রা কমানোর জন্য কত বিস্তর কথাবার্তা শোনা গেল, কত নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, কত প্রতিশ্রুতি।
কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। কোনো কোনো দেশে অকালে প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। কোথাও বন্যা-প্লাবন, কোথাও অনাবৃষ্টি। গত বছর বড় ধরনের দাবানলে দগ্ধ হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া। ক্যারিবিয়ান থেকে জাপান পর্যন্ত ভেসে গেছে বন্যায়। আর এর সবকিছুর জন্যই মূর্খের মতো আমরা এল নিনোকে দায়ী করছি। এল নিনোর ভূমিকা আছে বটে, তবে তা সামান্য। মূলত দায়ী গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাব। প্রহসন এই যে, গ্রিনহাউজ গ্যাস কমানোর ব্যাপারে আমাদের মতো গরিব দেশগুলোর ভূমিকা যৎসামান্য। গ্রিনহাউজ গ্যাসকে আদৌ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি-না আবার গেলেও কতখানি যাবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে কতিপয় ধনী দেশের ওপর। মজার ব্যাপার হলো, তারাই আবার তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি করার সময় ‘শ্রমের মানদণ্ড’ বা ‘পরিবেশ রক্ষা’র বিষয়টিকে শর্তযুক্ত করে দেন। দেখা গেছে, আফ্রিকার গরিব দেশগুলোতে পরিবেশ দূষণের মাত্রা খুবই কম অথচ মেক্সিকো বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সর্বোচ্চ পরিবেশ দূষণকারী রাষ্ট্র যখন তাদের সঙ্গে চুক্তি করে, তখন তারাই আবার ওই দেশগুলোকে পরিবেশ বহাল রাখার সবক দেয়। পরিবেশ দূষণের জন্য যারা সবচেয়ে বেশি দায়ী দেখা যাচ্ছে, পরিবেশের জন্য তাদেরই মায়াকান্না সবচেয়ে বেশি। এরই নাম পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা। যার লক্ষ্য, শুধু সারা দুনিয়ার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নয়, মুনাফাবাজ কোম্পানিগুলোকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেয়া, যাতে কেয়ামতের আগে পর্যন্ত তারা গরিব দেশগুলোকে শুষে খেতে পারে। আর রাজনৈতিকভাবে দুর্বল দেশ হলে তো কথাই নেই। জবরদস্তি খাটানো ছাড়াই তাদের যেকোনো মনোবাঞ্ছা পূরণে ব্যস্ত থাকে এই জাতীয় দেশগুলো। ধনীরা কতটা কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়বে, তার ওপর নির্ভর করছে আমাদের টাটকা বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার ক্ষমতা। দেখা যাচ্ছে, একক বিশ্ব ব্যবস্থাপনা বা মোড়লগিরির সুবাদে আমাদের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাপারটিও তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে।
আমাদের মনে রাখতে হবে, ভোরের টাটকা বাতাসে যতই জগিং করা হোক, সুস্থ পরিবেশে আমাদের বাঁচার অধিকার আছে কি-না তা নির্ভর করছে ধনীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। সে ক্ষেত্রে জগিং করেও লাভ হবে না, যদি আমরা বিশ্ব পরিবেশ ব্যবস্থা বদলানোর চেষ্টা না করি, ধনীদের বিশ্ব পরিবেশ বিধ্বংসী ব্যবস্থা বহাল রাখি এবং বিশ্ব পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের নামে তাদের রদ্দিমার্কা জিনিস বেচা-বিক্রি বন্ধে সরব না হই, প্রতিবাদ না করি। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ন্যূনতম সংস্কারের প্রশ্নকে আড়াল করে গরিব বিশ্বের জনগণের ওপর সব দায় চাপিয়ে তাপমাত্রা কমানো যাবে না। পরিবেশ দূষণ পৃথিবীর সব দেশেরই একটি অভিন্ন সমস্যা। দূষণ রোধে বিভিন্ন ধরনের সম্মেলন, সেমিনার, চুক্তি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বান্ধব বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলছেন। কিন্তু পরিবেশ দূষণের ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। এই অনিশ্চয়তার জন্য ধনী দেশগুলো বেশি দায়ী। তবে এই পরিবেশ দূষণের নেতিবাচক প্রভাব থেকে কোনো দেশেরই মুক্তি নেই। তাই পৃথিবীতে আমাদের টিকে থাকতে হলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাটা জরুরি। আর তা না পারলে পৃথিবী থেকে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়াটাও অসম্ভব কিছু নয়। আজকে যে বিশ্ব মানচিত্রের প্রত্যন্ত কোণ ঢাকায় ৩৮ ডিগ্রি তাপমাত্রায় আমরা নাগরিকরা হাঁসফাঁস করছি কিংবা সুদূর চুয়াডাঙ্গার যে অধিবাসী কোন পরিবেশ পাপ না করেও হিটস্ট্রোকে বেহাল দশার মধ্যে আছেন তার জন্য দায়ী সে নিজে নয়। গ্রিনহাউজ গ্যাসকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বের সঙ্গে প্রাণ ও পরিবেশ কম বিনষ্টকারী তৃতীয় বিশ্বের এখানেই প্রবল রকম একটি রাজনৈতিক বিরোধ রয়েছে। উন্নত দেশ বলে পরিচিত দেশগুলো কেবল বিষাক্ত গ্যাস ছড়ায় আর আমরা তা শুষে নিই।
আসলে প্রকৃতির অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্য তারাই বেশি দায়ী। আমরা শিকার মাত্র। গ্রিন হাউস উদ্গীরণের কারণে দুনিয়াব্যাপী জলবায়ুর যে নেতিবাচক পরিবর্তন তাতে তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশবাদীরা কি কোন ভূমিকা রাখতে পারছেন? বিশ্বব্যাপী পানি ও জ্বালানির ওপর দখল প্রতিষ্ঠার জন্য যে মরণপণ লড়াই চলছে সেই লড়াইয়ে বা তাদের প্রস্তুতি কী। ধনী দেশগুলোর বরাতে পরিবেশ বিষয়ে সবচেয়ে বড় ক্ষতির শিকার আমরা তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলো। অতএব বিশেষ ধরনের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও মুনাফাবাজ বিশ্ব ব্যবস্থার মূলে আঘাত না করলে পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রাণ রক্ষা সম্ভব নয়।
লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট
সাম্প্রতিক দেশকাল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন
বিষয় : বৈশ্বিক উষ্ণায়ন গ্রিনহাউজ গ্যাস
© 2024 Shampratik Deshkal All Rights Reserved. Design & Developed By Root Soft Bangladesh