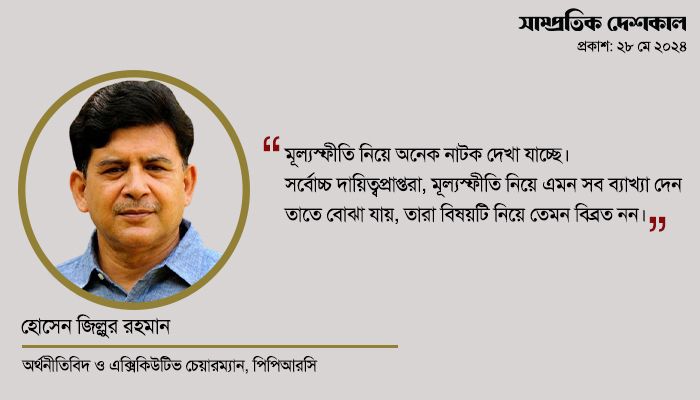
মূল্যস্ফীতি নিয়ে অনেক নাটক দেখা যাচ্ছে। সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্তরা, মূল্যস্ফীতি নিয়ে এমন সব ব্যাখ্যা দেন তাতে বোঝা যায়, তারা বিষয়টি নিয়ে তেমন বিব্রত নন। ২০২৩ সালে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা দেখলাম, দায়িত্বপ্রাপ্তরা এগুলোকে সমস্যা হিসেবেই দেখছেন না। লিপস্টিকের বিক্রি বেড়ে যাওয়া নিয়ে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সিদ্ধান্ত টেনে বলেছেন, মানুষের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের মতো অর্থনীতিবিদের আসলে বেকার হয়ে যাওয়াই ভালো। কারণ যারা অর্থনীতি চালাচ্ছেন, তাদের মাথায় যে সূচকগুলো কাজ করছে, সেগুলো অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত নয়।
বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বিব্রতকর বিষয় হলো, ক্ষমতায় যারা আছেন, তারা সার্বিকভাবে বিষয়টি যেভাবে মূল্যায়ন করছেন এবং সাধারণ মানুষ যেভাবে দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তারা কিন্তু ধরেই নিয়েছেন, এটা এভাবেই হবে এবং এটাই ঠিক। তারা অন্য কোনো বিবেচনা মাথায় নিচ্ছেন না।
দীর্ঘ মেয়াদে বাজার অস্থিতিশীল। মূল্যস্ফীতি কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করলেও তাতে কাজ হচ্ছে না। বলাবাহুল্য, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি নিয়েই বিতর্ক আছে। এটা স্পষ্ট, ব্যাংক খাতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এ আয়োজন। বেসরকারি একটি বড় ব্যাংকের তারল্য সংকট কাটাতে একই সঙ্গে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা ছাপিয়েছে। সরকারের প্রভাবশালীদের দখলে থাকা এই ব্যাংকসহ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংকট কাটাতে নানা ধরনের চেষ্টা অব্যাহত। কিন্তু অর্থনীতিকে বাঁচাতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন বিস্তর। কারণ অবশ্য স্পষ্ট, রাজনৈতিক বিবেচনায় অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ।
এর প্রভাব সর্বত্র বিরাজমান। মূল্যস্ফীতিও তার বাইরে নয়। মূল্যস্ফীতির অংশীজন কারা? স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ী। এর সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিও প্রভাবক ভূমিকা পালন করে। বাজার যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন অনেক সময় আমদানি করতে হয়। যেখানে ব্যবসায়ী ও সরকারের ভূমিকাই প্রধান। সরকার যখন আমদানির অনুমতি দেয়, সেখানে কেমন শুল্ক আরোপ করে, তাও দেখার বিষয়। ফলে মূল্যস্ফীতিতে তিনটি ফ্যাক্টর স্পষ্টতই কাজ করছে: সরকারের বাজার ব্যবস্থাপনা, মুদ্রানীতি এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের গতিশীলতা।
চলমান পরিস্থিতি যদিও নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তারপরও আমরা একে স্বাভাবিক হিসেবেই ধরে নিয়েছি বা ধরে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি খাদের কিনারেই দাঁড়িয়ে। গত বছর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন এবং চলতি বছর ডলারের সংকট আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, নীতিগতভাবে আমাদের সমস্যা কোথায়? সংকট দূর করার জন্য আমদানির ওপর বিধিনিষেধের মাধ্যমে রিজার্ভ ‘সুরক্ষা’র চেষ্টা করে সরকার। চলতি বছর রপ্তানির জন্য নগদ প্রণোদনা বন্ধ করার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ডলার ঘাটতির সম্পর্ক রয়েছে। যদিও এসবের মাধ্যমে অল্প কিছু উপকার হতে পারে। বাস্তবতা হলো, এ ধরনের পদক্ষেপে তাৎক্ষণিক কিছু উপকার হলেও দীর্ঘ মেয়াদে এগুলো নীতিগত দিক থেকে খুব একটা সুফল বয়ে আনবে না।
এ ধরনের নীতি শেষ পর্যন্ত হিতে বিপরীত হতে পারে। সাময়িক পতন ঠেকিয়ে রাখতে গিয়ে অনেক সময় অংশীজনের স্বার্থ উপেক্ষিত থাকে। যেমন এতে আমদানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে পারে। তাই তাৎক্ষণিক সংকট উত্তরণের চেয়ে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল জরুরি।
আরেকটা বিষয় খেয়াল করার মতো। ‘নির্বাচন’-পরবর্তী যেসব পদক্ষেপ আমরা দেখছি, অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে সেখানে প্রাথমিকভাবে স্বজনতোষী পুঁজিবাদ সুরক্ষারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্বজনতোষী, স্বার্থান্বেষী গ্রুপ, রাজনৈতিক সুবিধাবাদী-এরা সবাই প্রায় এক। তারা প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে সরকারের অনুকূলে অযাচিত সুবিধা পেয়ে থাকে কিংবা তাদের সুবিধার জন্যই সরকারি নীতি গ্রহণ করা হয়। এরা রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত এবং দেশকে প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। সর্বত্রই তাদের প্রভাব স্পষ্ট অর্থনৈতিক খাত, বিদ্যুৎ, পরিবহন, অবকাঠামো চুক্তি, এমনকি সামাজিক খাত ইত্যাদিতে। তাদের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা নিয়ম ভাঙতে কিংবা বানাতেও কুণ্ঠিত হন না। অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনার আগ পর্যন্ত মনে হচ্ছে, স্বজনতোষী নীতিই চলতে থাকবে।
বাজার ব্যবস্থাপনাও একই সূত্রে গাঁথা। বাজার সিন্ডিকেট বা ক্ষমতাপুষ্ট গোষ্ঠীগুলো খুবই শক্তিশালী, যারা বাজারে বা বাজার ব্যবস্থাপনায় অনৈতিক মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে বিরাজ করছে। আমাদের এ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার আশীর্বাদপুষ্ট অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলোকে লালন করা হচ্ছে। তারা এখনো আগের মতোই রয়েছে। এটা কিছু বেড়েছেও। তারপরও মূল্যস্ফীতির স্বার্থে কিছু কথা প্রয়োজন।
বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম তথা সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা জরুরি। সে জন্য সরবরাহ শৃঙ্খল তথা সাপ্লাই চেইনের মধ্যে গতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, শাক-সবজি, চাল, মাংস, ভোজ্যতেল এবং শিশুখাদ্যের মতো নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পণ্যে সরকারি কার্যকর নজরদারি জরুরি। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্বাধীন বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূল্যস্ফীতির মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা, সেই সঙ্গে সম্ভাব্য সমাধানের জন্য সুষ্ঠু তদন্ত প্রয়োজন। হয়তো তাত্ত্বিক অনেক আলোচনাই বাস্তবতার সঙ্গে মিলবে না। সে জন্য বাস্তবতার আলোকে পদক্ষেপ নেওয়া চাই।
সম্প্রতি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২৯ পণ্যের দাম বেঁধে দিলেও, বাজারে সে অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করেনি ব্যবসায়ীরা। মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, সবজির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিজেদের মতো বেঁধে দিলেই যে তা কার্যকর হয় না, এটাই তার প্রমাণ। সংস্থাটি নিয়মিত ঢাকা শহরের দৈনিক পণ্যমূল্যের একটি তালিকা পাঠিয়ে দেয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে। এর মধ্যেও বড় গলদ। প্রতিদিন দামের যে তালিকা দেওয়া হয়, সে দরের সঙ্গে বাজারে প্রকৃত দামের বিস্তর ফারাক। একই সঙ্গে বাজারে অভিযান বা মন্ত্রীদের পরিদর্শনের মতো তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের মাধ্যমেও টেকসই সমাধানের সম্ভাবনা ক্ষীণ। এর পরিবর্তে পণ্য অনুসারে বাজার ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এমন ব্যবস্থা নিলে রাতারাতি না হলেও এক মাসের মধ্যে সুফল পাওয়া যাবে।
মোটের ওপর অর্থনৈতিক গভীর সংকট কাটাতে নীতিগত দিকেই নজর দিতে হবে। আমাদের সমস্যা এক ধরনের, অথচ ভিন্ন নীতি গ্রহণ করার ফল খারাপ হবে। একদিকে সংকোচনমূলক ঘোষিত কাগুজে নীতি, অন্যদিকে এই নীতির বিরোধী সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হচ্ছে। এতে স্ববিরোধী প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও বাজার ব্যবস্থার কারণে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। এ জন্য মূল্যস্ফীতি নিয়ে সরকারের উচিত হবে আসছে বাজেটের আগেই একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা। এটা এখন সময়ের দাবি। তাহলে আমরা বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারব।
আর স্বজনতোষণ সুরক্ষা নীতি থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার আশীর্বাদপুষ্ট অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলোকে লালন করা হলে কিংবা বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা না নিলে এবং জবাবদিহি নিশ্চিত না করলে সেই তিমিরেই থাকতে হবে। তবে নীতিগত সমস্যা থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে সংকট উত্তরণে ম্যাক্রো, মেসো এবং মাইক্রো পর্যায়ে অর্থাৎ সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাধারণ মানুষের নিজেদের চেষ্টার অভাব নেই। কিন্তু ট্র্যাজেডি হলো, এই অদম্য প্রচেষ্টা ক্ষমতার অলিন্দে গিয়ে রাষ্ট্রীয় নীতির বলি হচ্ছে। এসব প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন করলে দেশ আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গতিশীল অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।
অতিসম্প্রতি বিবিএসের জরিপে পারিবারিক আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব বেরিয়েছে। সেখানকার একটি তথ্য আমার কাছে চমকপ্রদ মনে হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০২২ সালের হিসাবের মধ্যে একটা টেবিল ছিল আয়ের খাত। মজুরি এবং বেতনের ওই খাতটা শুধু দরিদ্ররা নয়, মধ্যবিত্তের জন্যও সমান। দেখা গেছে, ছয় বছরের মধ্যে এই খাতে আয় ১০ শতাংশ কমেছে। বিবিএসের এই জরিপে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ৫ শতাংশ ধনীর হাতেই ৩০ শতাংশ আয়। ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে ৪০ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ পরিবারের হাতে ৫৫ শতাংশ আয়। ৫ শতাংশ পরিবারের ৩০ শতাংশ আয়, আর নিচের ৫০ শতাংশ পরিবারের আয় ১৮ শতাংশ। তার মানে, আমরা প্রবৃদ্ধির যে কৌশলে এগোচ্ছি, সেটাও সাধারণ মানুষের জন্য ঝুঁকি। কারণ ওই কৌশলে কার্যকর কর্মসংস্থান ও ন্যায্য মজুরির বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। চা শ্রমিক বা গার্মেন্ট শ্রমিকদের কথা বলি, অন্যত্রও একই অবস্থা। তার মানে সরকারের প্রবৃদ্ধির কৌশল অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি থেকে বহু দূরে। এখানে কর্মসংস্থান এবং ন্যায্য মজুরিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। এই প্রবণতাও আমাদের এক ধরনের বোঝা। উৎপাদনশীল শ্রমিক হওয়ার শর্তগুলো অর্থাৎ শিক্ষা, আবাসন, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি যে কমানো দরকার, সেগুলো সরকারের অগ্রাধিকারে নেই।
হোসেন জিল্লুর রহমান
অর্থনীতিবিদ ও এক্সিকিউটিভ
চেয়ারম্যান, পিপিআরসি
সাম্প্রতিক দেশকাল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন
© 2024 Shampratik Deshkal All Rights Reserved. Design & Developed By Root Soft Bangladesh