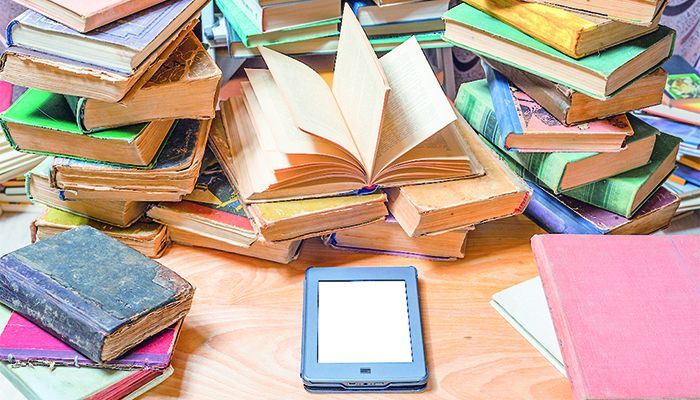
ই-বুক বনাম কাগজের বই। ছবি- সংগৃহীত
কাগজের বই, ই-বুক ও অডিওবুকের পাঠকরা ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের প্রিয় বই পড়তে প্রায় ১৭৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে। জার্মান সংবাদ মাধ্যম ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনে এমনটাই জানানো হয়েছে। প্রতিবছর প্রায় চার মিলিয়ন নতুন বই প্রকাশ হয়। যদিও সবগুলো বই পাঠকপ্রিয় হতে পারে না।
কিন্তু প্রশ্ন হলো এসব বই কি পরিবেশ ও জলবায়ুকে প্রভাবিত করছে? আর আমাদের কি বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য কাগজের বই থেকে ই-বুকে যাওয়া উচিত? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে দুই ধরনের বইয়ের সুবিধা ও অসুবিধা জানতে হবে। কারণ উভয় মাধ্যমের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে।
প্রায় ৬০০ বছর আগে জোহানেস গুটেনবার্গ জার্মানিতে ছাপাখানা আবিষ্কার করার পর থেকে বিশ্বব্যাপী বই প্রকাশনার পরিসর বেড়েছে। গুগলের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪৪০ থেকে ২০১০ সালে প্রেস আবিষ্কারের মধ্যে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন বই প্রকাশ হয়েছে। এসব বই মানবসভ্যতার জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কিন্তু সেই বইগুলোর প্রকাশ করতে অনেক গাছ লেগেছে।
প্রকাশনা জায়ান্ট পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউস ইউকে বছরে প্রায় ১৫ হাজার কাগজের বই প্রকাশ করে। তারা বলছে, এখন তারা টেকসই কাগজ ব্যবহার করছে। পেঙ্গুইনের সিনিয়র সাসটেইনেবিলিটি প্রোডাকশন ম্যানেজার কোর্টনি ওয়ার্ড-হান্টিং বলেছেন, তাদের বইয়ে ব্যবহৃত কাগজ শতভাগ ফরেস্ট স্টুয়ার্ডশিপ কাউন্সিল (এফএসসি) দ্বারা প্রত্যয়িত। তার দাবি, এই কাগজ টেকসই বা ‘পুনরুৎপাদনশীল’। অবশ্য বন সুরক্ষার বিষয়ে এফএসসি সমালোচিত হয়েছে। পরিবেশবাদী গ্রুপ গ্রিনপিসের মতো সংস্থা এফএসসির বিরুদ্ধে গ্রিনওয়াশিংয়ের অভিযোগ এনেছে।
কোর্টনি ওয়ার্ড-হান্টিং স্বীকার করেন, পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউসে জলবায়ু প্রভাবের ৭০ শতাংশের বেশি প্রিন্টার ও কাগজ মিল থেকে আসে। পেঙ্গুইনের গড় বই ৩৩০ গ্রামের মতো কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করে, যার মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস রয়েছে। এটি প্রায় এক কাপ কফির মতো।
এ ছাড়া পেপারব্যাক বইয়ের গড় জলবায়ু প্রভাব প্রায় তিনগুণ বা এক কিলোগ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতুল্য। এটি ১২২টি স্মার্ট ফোন চার্জ করা বা দুটি ক্যাফে ল্যাট তৈরির সমান।
যদিও কাগজ তৈরির উদ্ভাবন হার্ডকপি বইয়ের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়েছে, কিন্তু জলবায়ুর ওপর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ বই বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ সংস্থা ওয়ার্ডস রেটেড বলছে, প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ২ দশমিক ২ বিলিয়ন কাগজের বই বিক্রি হয়।
এমনকি যদি আমরা ধরে নিই যে, প্রতিটি বই শূন্য দশমিক ৩৩ কিলোগ্রাম সমতুল্য কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। তাহলে পরিমাণ দাঁড়াবে ৭ লাখ ২৬ হাজার টন কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা বছরে ১ লাখ ৪১ হাজার ২৬১টি বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহের সমান বা ১ লাখ ৬১ হাজার ৫০০ গাড়ি থেকে গ্যাস নির্গমনের সমান।
তবে হাজার হাজার বই সংরক্ষণ করতে পারে এমন একটি বৈদ্যুতিন পড়ার ডিভাইসের তাৎক্ষণিক পরিবেশগত সুবিধা হলো কোনো কাগজ ব্যবহার করতে হয় না।
ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই বইয়ের কাগজের জন্য বছরে ৩২ মিলিয়ন গাছ কাটা হয়। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির (আইইএ) তথ্য বলেছে, ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের প্রায় ছয় শতাংশ ছিল কাগজ প্রক্রিয়াকরণ।
এ ছাড়া ই-সংস্করণে নতুন বইয়ের জন্য পরিবহনের প্রয়োজন হয় না। কারণ ই-সংস্করণ যে কোনো সময় যে কোনো ডিভাইসে ডাউনলোড করা যায়।
বর্তমান ই-বুকের বাজারের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হলো অ্যামাজনের কিন্ডল। ওয়ার্ডস রেটেডের তথ্য বলছে, কিন্ডলের মাধ্যমে বছরে ৪৮৭ মিলিয়নেরও বেশি ই-বুক বিক্রি হয়। বহুজাতিক সংস্থা অ্যামাজন ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছে, প্রতি মাসে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫০ লাখ মানুষ এই ডিভাইস বা কিন্ডল অ্যাপের মাধ্যমে বই পড়েন।
বর্তমান প্রজন্মের কাছে ই-বুকের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বিশেষ করে জেন জেড পাঠকের কাছে। জার্মান ডেটা প্ল্যাটফর্ম স্ট্যাটিস্টা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ই-বুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১ দশমিক ১ বিলিয়নে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কিছু পাঠক কাগজ থেকে ডিজিটাল বইয়ের দিকে ঝুঁকছেন। তাতে কি পরিবেশ ও জলবায়ুর জন্য সুবিধা বাড়বে? এই প্রশ্নের উত্তর, না। কারণ ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর কিছু খারাপ দিক আছে। কারণ এই ডিভাইসগুলো তৈরিতে প্রচুর জ্বালানি ব্যয় করতে হয়। তা ছাড়া এগুলোর ব্যাটারিতে তামা, লিথিয়াম ও কোবাল্টের মতো ধাতু থাকতে পারে। যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আবার ডিভাইসগুলো প্লাস্টিকের তৈরি, যা মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উদ্ভূত। একই সঙ্গে এসব ডিভাইসের আলো পাঠকের চোখের জন্য ক্ষতিকর। তাই বলা যায় ই-বুকের ডিভাইস তৈরি যেমন জলবায়ুতে প্রভাব ফেলে, আবার এগুলো পাঠকের স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর।
