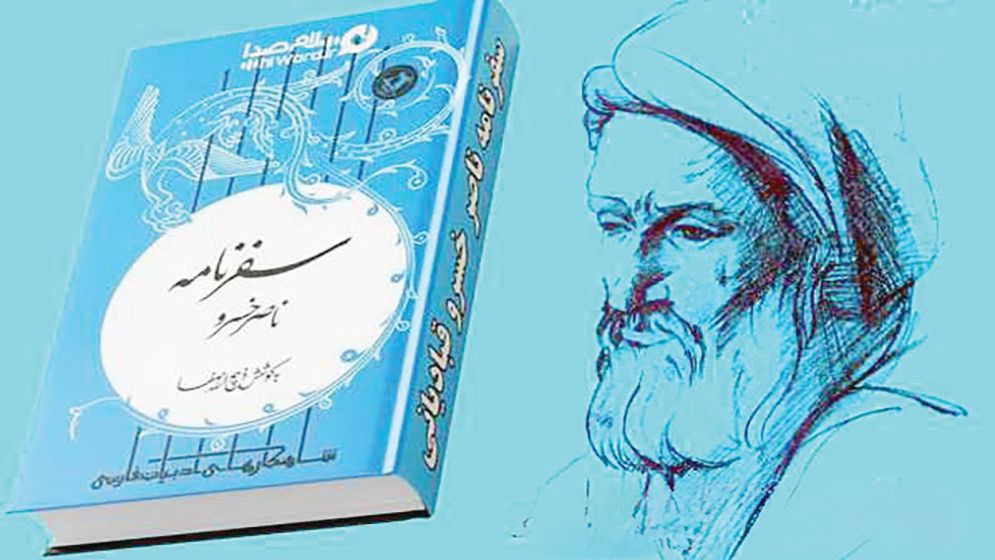
ফারসি সাহিত্য ভ্রমণ সাহিত্যে সমৃদ্ধ, যেখানে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য বা নগর-পরিদর্শনের বিবরণ নয়, বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবিধ ভূখণ্ডের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এ ধারার এক অনন্য ও স্থায়ী কীর্তি হলো ইরানের প্রখ্যাত কবি, গদ্যকার ও ভ্রামণিক নাসের খসরু কোবাদিয়ানির সফরনামা। এটি তার সাত বছরের দীর্ঘ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বয়ান। যেখানে তিনি সুন্দর সাহিত্যিক বুননে খোরাসান থেকে মিশর এবং আবার বলখে প্রত্যাবর্তনের কাহিনি তুলে ধরেছেন। সফরনামাটি পঞ্চম হিজরি শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক নিদর্শন।
নাসের খসরু শুধু একজন ভ্রামণিক নন; তিনি একজন কবি, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, কোরআনের ব্যাখ্যাকার ও ইসমাইলি মতবাদের প্রচারক ছিলেন। তার সফরনামা সমাজ ও ধর্মের প্রতি এক বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে, যা এ গ্রন্থটিকে ইতিহাস ও সাহিত্যের যুগল সম্পদে পরিণত করেছে। ৩৯৪ হিজরি তথা ১০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বলখ অঞ্চলের কোবাদিয়ান শহরে জন্মগ্রহণকারী নাসের খসরু পঞ্চম হিজরি শতকের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক। ভ্রমণের আগে তিনি সেলজুক আমলের এক প্রভাবশালী সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এবং রাজদরবারের অন্দরের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন। ৪০ বছর বয়সে এক গভীর আত্মিক জাগরণ তার মধ্যে ঘটে এবং সত্যের সন্ধানে তিনি ভ্রমণ শুরু করেন।
তিনি যে সফরনামা ছাড়াও কাব্যগ্রন্থ তথা দিওয়ান রচনা করেছিলেন, যা তাকে সমকালীন সাহিত্য জগতে সমধিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। সবিশেষ কাসিদা রচয়িতা হিসেবে তার প্রাতিস্বিকতাও ছিল। এ ছাড়া তিনি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গুশায়েশ ও রাহায়েশ তথা উন্মোচন ও মুক্তি নামক একটি সুখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পাশাপাশি রোশনায়ি নামে এবং সাদাত নামে দুটো মাসনভি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি গণিতের উচ্চমাপের একজন গবেষক ছিলেন। সে বিষয়ে তিনি গারায়েবুল হিসাব ও আজায়েবুল হিসাব নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর কবিতায় এবং সফরনামার ভূমিকায় পাওয়া যায় যে, এক স্বপ্নই তাকে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ৪৩৭ হিজরিতে যাত্রা শুরু করে ৪৪৪ হিজরিতে তা সমাপ্ত করেন।
নাসের খসরু নগর, বাজার, স্থাপত্য, রাস্তা, মানুষের জীবন, ধর্ম, আচার-আচরণ, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে নিখুঁত পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য তার এ সফরনামায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিবরণ পঞ্চম হিজরির সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে অমূল্য তথ্য প্রদান করে। তিনি যে শহরগুলো বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে : নিশাপুর, মারভ, নেসা, হেরাত, বসরা, বাগদাদ, মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম, দামেস্ক, কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া।
এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে এমন একসময়, যখন বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত ও মিশরের ফাতেমীয় খিলাফতের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের দুর্বলতা ও বিভিন্ন শহরের নৈতিক ও জ্ঞানগত অবক্ষয়ও সমালোচনাভাবে তুলে ধরেছেন। এই রচনা প্রথাগত ইতিহাসবিদদের মতো সরকারি আনুগত্যে লেখা হয়নি; বরং একজন স্বাধীন চিন্তাবিদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ফসল। এতে জনগণের জীবন ও সময়ের মনস্তত্ত্বও প্রতিফলিত হয়, যা একে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।
নাসের খসরুর সফরনামা উৎকৃষ্ট ও পরিশীলিত গদ্যের নিদর্শন। সে সময়ে অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আরবি শব্দে পরিপূর্ণ হলেও তিনি পরিশীলিত ফারসি গদ্য ব্যবহার করেছেন। ফলে গ্রন্থটি শুধু ইতিহাস নয়, সাহিত্যিক সৌন্দর্যেরও দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি প্রথম পুরুষে (আমি) বর্ণনা দিয়েছেন, যা পাঠকের মনে ঘনিষ্ঠতার আবহ তৈরি করে। স্থান ও মানুষ সম্পর্কে তার সংবেদনশীল ও সজীব বিবরণ এই রচনাকে শিল্পসাহিত্যে উন্নীত করেছে। এই ভ্রমণ কথা শুধুই ভূগোল বা ইতিহাস নয়; এর গভীরে রয়েছে দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা। এই গ্রন্থটি একটি রোজনামা বা ধারাবাহিক ভ্রমণ-বিবরণ। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ স্থান ও তারিখসহ উপস্থাপন করেন। এতে পাঠক ভ্রমণ পথ ও তার চিন্তার বিবর্তন অনুসরণ করতে পারেন। এই গ্রন্থ ফারসিতে রচিত অন্যতম প্রথম ও প্রভাবশালী ভ্রমণসাহিত্য। এটি ইবনে বতুতা, শারদেন, হাজি সিয়্যাহদের মতো পরবর্তী ভ্রমণকারীদের রচনার পথ প্রস্তুত করে।
নাসের খসরু তার সাহিত্যিক ক্ষমতার সঙ্গে ধর্ম, দর্শন ও সমাজবাস্তবতা একত্র করেছেন। এই বহুমাত্রিকতা তাকে এক আন্তবিষয়ক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। তার রচনাটি আজও ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও দর্শন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত। এটি মধ্যযুগীয় ইরান ও ইসলামী সভ্যতা জানার অন্যতম ভিত্তিকর্ম। নাসের খসরুর সফরনামা শুধু একটি ভ্রমণ কথা নয়; এটি এক বহুমাত্রিক রচনা যা সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও ভূগোল-সব ক্ষেত্রেই অসামান্য গুরুত্ববহ। এ রচনাটি পঞ্চম হিজরির ইরান ও ইসলামী দুনিয়া জানার এক অনন্য দর্পণ, একই সঙ্গে এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা ব্যক্তি, অভিজ্ঞতা ও বৃহৎ মানবচিন্তার একটি অভাবনীয় সংমিশ্রণ। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও এর সত্যান্বেষণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও উচ্চশ্রেণির ভাষাশৈলী নতুন প্রজন্মের কাছেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও প্রেরণাদায়ক।
