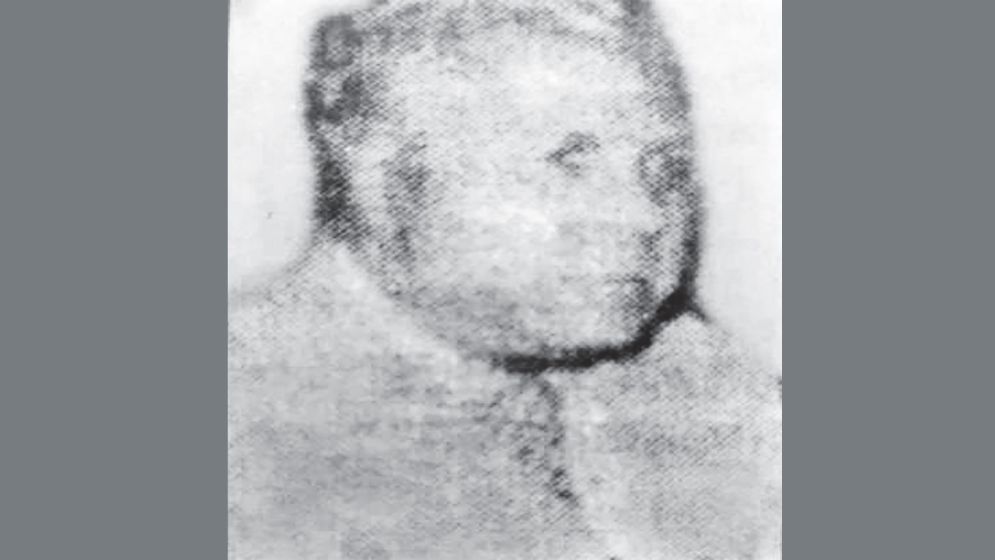
খন্দকার আবদুল হামিদ
১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যাত্রা শুরু করেন। এর আগে ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল তিনি তার শাসনকে বেসামরিক করার উদ্দেশে ১৯ দফা কর্মসূচি চালু করেন। জিয়ার রহমানের আগে ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ শব্দটি এখানে ছিল সুদূর পরাহত। তিনিই এটি চালু করে জনগণের ভেতরে চেতনার এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। আজকে যা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ বিষয়টি যার মাথায় প্রথম এসেছিল তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক। ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমানের উপস্থিতিতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বিষয়ে একটি সেমিনারে খন্দকার আবদুল হামিদ বলেন, বাঙালি জাতীয়তা বললে মাল্টি-স্টেট ন্যাশনালিজমের কথা এসে পড়ে। কারণ বাংলাদেশের বাইরেও কয়েক কোটি বাঙালি আছেন। আমরা কি সেসব বাঙালিকে বাংলাদেশের জাতির শামিল করতে পারি? জটিল আন্ত রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে ঝুঁকি না নিয়ে (প্যানবেঙ্গলিজম বা সুপ্রা-ন্যাশনালিজমের) কথা আমরা কি ভাবতে পারি? পারি না। আর তাই আমাদের জাতীয়তাকে ‘বাঙালি জাতীয়তা’ বলে অভিহিত করতে পারি না। করলে টেকনিক্যালি ভুল হবে, পলিটিক্যালি তা বিপজ্জনক হতে পারে।
মূলত খন্দকার আবদুল হামিদ বিশ্বের বাঙালিদের কথা মাথায় রেখেই তিনি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ভাবনাটির কথা চিন্তা করেছিলেন। জিয়াউর রহমান খন্দকার আবদুল হামিদের এই তত্ত্বটি গ্রহণ করেন। এই তত্ত্বটিকে অবলম্বন করে তার ১৯ দফা প্রণয়ন করেছিলেন। সাংবাদিক খন্দকার আবদুল হামিদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এতটাই প্রখর ছিল যে জিয়াউর রহমান তাকে শুধু গুরুত্বই দেননি। মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগও দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ‘আমার পিতা খন্দকার আবদুল হামিদ’ লেখায় তার মেয়ে লতিফা চৌধুরী স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন “মন্ত্রী হলেও আমার বাবাকে দেখেছি এক বিষণ্ন, চিন্তাযুক্ত নিরানন্দ মানুষ হয়ে এক অজানা মনঃকষ্টে ভুগতে। মিন্টো রোডের সরকারি বাসার জানালার পর্দা লাগানোর জন্য সরকারি লোক এলে তিনি তাদের বলেছিলেন, ‘কী আর হবে এত খরচা করে, ক’দিনের জন্য নতুন পর্দা টাঙানোর! এখন এসব থাক।’
তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর মিলিত জোট যুক্তফ্রন্টের সময়। তার রাজনীতি ছিল শুধুই দেশের মানুষের জন্য। শেরপুর একটি হিন্দুপ্রধান এলাকা হলেও সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান ছিল না তখন। হিন্দুপ্রধান এলাকায় তিনি সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী হয়েছেন প্রতিবারই। প্রথমবার মন্ত্রী হয়ে তিনি মাত্র এক বছর মন্ত্রিত্ব করেই ইস্তফা দিয়েছিলেন নিজের ইচ্ছায়। শুনেছিলাম রাষ্ট্রপতি জিয়াও নাকি অবাক হয়েছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি তাকে জানিয়েছেন, এই চাকরি করা তার স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি রাষ্ট্রপতিকে আরো বলেছিলেন, ‘আপনাকে আমি সত্য ও সঠিক পরামর্শ দিতে পারছি না, কারণ এখন আমি লালফিতায় বন্দি। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি দেশ এবং মানুষের জন্য আমাকে আবার সাংবাদিকতায় ফিরে যেতে হবে।’ বাসায় ফিরে আমাদের বলেছিলেন, ‘আজ আমি একটু শান্তিতে ঘুমাব।’ মাত্র এক মাস অসুস্থ থেকে আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেননি। ১৯৮৩ সালের ২২ অক্টোবর তার জীবনাবসান হয়।
উল্লেখ্য, সাংবাদিক ও রাজনীতিক খন্দকার আবদুল হামিদের জন্ম ১৯১৮ সালের ১ মার্চ শেরপুরে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক এবং ১৯৫৩-১৯৫৬ সালে দৈনিক মিল্লাত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সিনিয়র ‘লিডার রাইটার’ পদে যোগ দেন। এ পত্রিকায় তিনি ‘স্পষ্টভাষী’ ছদ্মনামে মঞ্চে নেপথ্যের কলাম এবং একই সময় ‘মর্দে মুমীন’ নামে উপসম্পাদকীয় কলাম লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮২ সালে দৈনিক দেশ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি নিযুক্ত হন।
সাংবাদিকতার পাশাপাশি খন্দকার আবদুল হামিদ রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী হিসেবে তিনি শেরপুর থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় যুব উন্নয়ন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮১ সালে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পরে ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের মন্ত্রিসভায় তিনি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রম, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। খন্দকার আবদুল হামিদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সাংবাদিকতায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালে তাকে ‘একুশে পদক’ প্রদান করে।
