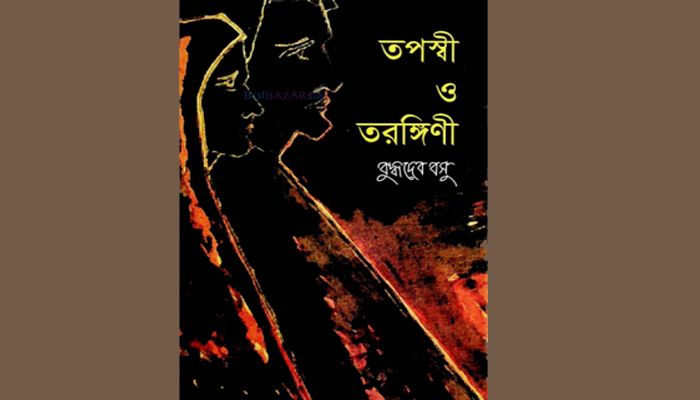
বুদ্ধদেব বসু বাংলা ভাষাসাহিত্যের আধুনিক কালের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক জন। যিনি তার প্রায় প্রতিটি লেখায় দিতে চেয়েছেন প্রাচীন ও নতুনের মিশ্রণে নতুনতর কিছু এবং বোধের উত্তরণে চিরকালীন। তেমনি এক রচনা ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’, প্রথম নাটক- যা কবিতায় বা কথা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির একটি। পূর্ণাঙ্গ অভিনয়যোগ্য ও শিল্পমূল্যে উজ্জ্বল এই নাটকের পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীর মাঝে তিনি সঞ্চার করেছেন আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব, প্রেম, বেদনা ও রোমান্টিক আবেগ, যা সাধারণ মানুষেরা ‘কাম’ নাম দিয়ে অপলাপ করে থাকে, তারই পথ ধরে দু’জন মানুষের পূর্ণের পথে উত্তরণের অসাধারণ প্রকাশনা। নারী ও পুরুষের আপন সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বকীয়তার মূল্য ও একে অপরের পরিপূরকতার বিশিষ্ট কার্যকারণ।
এই নাটকের দুই উল্লেখযোগ্য চরিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী ছাড়াও রয়েছে লোলাপাঙ্গী, চন্দ্রকেতু, বিভাজক, রাজমন্ত্রী, অংশুমান ও রাজকুমারী শান্তা যারা প্রত্যেকেই তাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পাপ-পূণ্য, লাভ- লোকসানের হিসাবে ষোলআনা পাকা; ঠিক তাদের উল্টো চরিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী, যারা আপন সত্তার উদ্বোধনের সাধনায় আপনাকে জানতে ও খুঁজতে ব্যাকুল। বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির ঊর্ধ্বে কেবল মানবিক দিকের প্রকাশ, স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও সত্তা হিসেবে মানবমূল্য খোঁজা ও বোঝার চেষ্টায় যারা রত।
‘তরঙ্গিনী’ অসাধারণ সুন্দরী এক বারবণিতা যে তার পেশাগত দক্ষতা, ছল-কলায় শীর্ষে। যার অঙ্গুলী হেলনে যে কোনো পুরুষোত্তমের হৃদয় হেলতে সময় নেয় না অনুক্ষণের; কিন্তু তার এই গর্ব, এই ক্ষমতা মুহূর্তেই লীন হয়ে যায় ঋষ্যশৃঙ্গের উচ্চারিত প্রশ্নের মাধ্যমে- ‘আপনি কি কোন পথভ্রষ্ট দেবতা? না কি আমারই কোনো অচেতন সুকৃতির ফলে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন? ... আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধর বিশ্বকরণার বিকীরণ!’ প্রথমে এই প্রশ্নে তরঙ্গিণী কৌতুক বোধ করেন কিন্তু সময়ের স্রোতে এই প্রশ্নই তরঙ্গিণীর আপন সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য খোঁজার প্রধান সহায়ক হয়ে দেখা দেয়।
তখন সে জানতে চায়, বুঝতে চায়- সে আসলে কে? কী তার জীবনের উদ্দেশ্য? পুরুষ মাত্রই কী রূপের স্তুতিকারী? না পুরুষ মানে নারীর পরিপূর্ণতার সহায়? তরঙ্গিনীকে পুরুষবধের সব কলা শেখানো হয়েছে; কিন্তু দেওয়া হয়নি পুরুষ সম্পর্কে কোনো ধারণা, যে পুরুষ কেবলই নিরপেক্ষ ভালোবাসার বাহন। পুরুষ মানেই যে কেবল সম্পদ আহরণের মাত্রা নয়, পুরুষ যে নারীর আলাদা এক চরিত্র তা প্রকাশের সহায়ক, তরঙ্গিণী কেবল ঋষ্যশৃঙ্গের কথার মাধ্যমেই বুঝতে পেরেছে।
নারী স্বতন্ত্র, নারী এক আলাদা সত্তা- যেখানে বহিরাবরণের সঙ্গে তার অন্তঃআবরণের সংযোগ কেবল নির্লোভ একান্ত চাওয়ায়, যা বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়ায় ভাস্বর নয়, যেখানে নারীর বাহ্যিক রূপ প্রধান। ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীকে তার অন্তঃআবরণের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করান যেখানে তরঙ্গিণী কেবলই একান্ত নারী, ভোগের উপাচার নয়।
এই আবিষ্কারটুকুই তরঙ্গিণীকে তার আপন সত্তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে যে- ইন্দ্রিয় সুখের সঙ্গে অর্থের কোনো যোগসূত্র নেই, যা সে এতদিন জেনে এসেছে বরং তা কেবল ইন্দ্রিয়সুখের প্রাপ্তিতে, সেখানে নেই আর কোন চাওয়া কিংবা পাওয়া, যেখানে একজন মানবীর উপস্থিতি কেবল একজন মানবী হিসাবে, ভালোবাসার পাত্রী হিসাবে, যা তরঙ্গিনীর চিন্তার সাগরে কখনো আঘাত হানেনি। তাইতো মুহূর্তে জেগে উঠে তরঙ্গিণীর হৃদয় আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অতিভূত করল ‘রোমান্টিক প্রেম’- যার অর্থ হলো কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব, অবিচল, অবস্থানির্বিশেষ এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তি- যার প্রতীক রাধা।
অপরদিকে ঋষ্যশৃঙ্গও জানত না পুরুষ মানে কী? পুরুষের জীবনে নারীর প্রয়োজনীয়তা, উপস্থিতির কার্যকারণ। তার পিতা বিভা-ক একান্তভাবে চেয়েছেন ছেলে তপস্বী হোক, এতে তাঁর পিতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় সিদ্ধিই সম্ভব; কিন্তু তরঙ্গিণীর উপস্থিতি, তার সমস্ত বোধি সত্তাকে করে তোলে নির্বোধ। প্রশ্নবাণে মুখরিত হয় আপন সত্তা। নিজেকে নতুন রূপে, নতুন সত্তায় আবিষ্কার করে ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত তপস্বী হয়ে ওঠেন আরক্ত, নারীকে কাছে পাবার চরম লালসা তাকে অকস্মাৎ ভূ-পতিত করে এবং নতুন এই বোধের সিদ্ধি লাভের লিপ্সা তাকে করে তোলে ব্যাকুল।
তথাপিও হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তি তাকে করে তোলে বিষণ্ণ, অন্ধকারেও তাই খুঁজে ফেরে স্বার্থবিহীন সে নারী সুখ ও দেহকে যে কেবলই তার পুরুষসত্তাকে জাগ্রত ও অতিক্রম করতে সফল ও সক্ষম। বৈষয়িক লাভ- লোকসানের হিসাবে যে ভালোবাসা নয়, কেবল নারী-পুরুষের একান্ত ভালোবাসাই যেখানে উপজীব্য ও কাম্য। তাইতো দ্বিতীয়বার তরঙ্গিণীর উপস্থিতি তাকে আবার তাঁর সেই সত্তা সম্পর্কে করে তোলে সচেতন, সে পুনরায় ফিরে যায় তাঁর মৌলিক ঋজুতা ও নির্মলতায়, তার মধ্যে দেখা দিল এমন এক স্বপ্রকাশ, যা সহজে অন্যের ভক্তির আনুকূল্য। তাই তরঙ্গিণীকে ছেড়ে চলে গেলেও সে হতাশ না হয়ে চরম ভালোবাসার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না।
কেননা তরঙ্গিণীর ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি জন্মেছে আপত্তিপূর্ণ ভালোবাসা, যা কেবল দিতে ইচ্ছুক, নিতে ইচ্ছুক নয়; কিন্তু মানব-মানবীর ভালোবাসার একান্ত কাম্য আসক্তিহীনতা- যা নিতে ও দিতে জানে কোন লাভ- ক্ষতির হিসাব ছাড়া; কিন্তু আসক্তিপূর্ণ ভালোবাসায় একের দ্বারা অন্যের ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ। কেননা সে আসক্ত তাকে দিয়ে যে কোন কাজ ভালোবাসার দাবিতে করিয়ে নেওয়া সম্ভব কিন্তু আসক্তিহীনতায় নয়।
তাইতো তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গ পুনরায় পথে নামে সেই ভালোবাসার খোঁজে, যেখানে ভালোবাসা কেবলই ভালোবাসার জন্য, কোনো পক্ষের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও এককসত্তার দাবিকে অবদমন করা নয়। হতে পারে তা মানুষের সঙ্গে, হতে পারে তা ঈশ্বরের সঙ্গে। সেই প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কেবলই খুঁজে যেতে হবে- নির্লোভ, ক্ষমতাহীন ক্ষমতার স্বার্থে- যে ক্ষমতা কেবল ভালোবাসার, যে ক্ষমতা আদি, পূর্ণ ও নিরপেক্ষতার মূর্তিতে উজ্জ্বল ও ভাস্বর।
