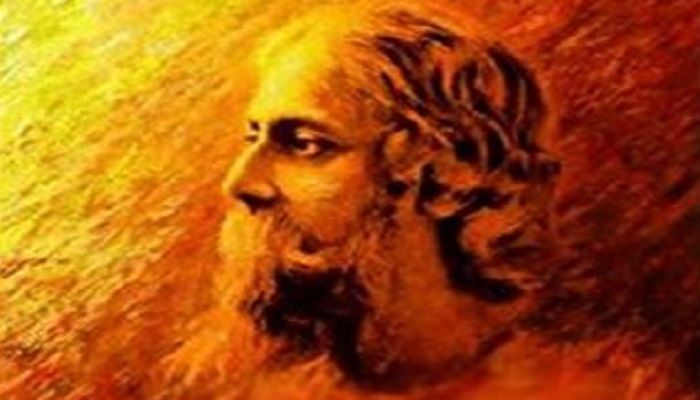
১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ‘গোরা’ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময় এক আইরিশ যুদ্ধে মারা যান, এ সময়ে তার আসন্ন প্রসবা স্ত্রী আশ্রয় নেন ব্রাহ্মণ কৃষন্দ দয়ালের বাড়িতে। সেই বাড়িতে সন্তান প্রসবের পরে মৃত আইরিশের স্ত্রীও মারা যান। যে সন্তান জন্ম নেয় তখন এই আইরিশের সে হলো- গোরা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘গোরা’ একটি চমৎকার উপন্যাস, যেখানে লেখক মানবিকতা বোধের সুন্দর উপস্থাপন করেছেন ধর্মের হাত ধরে। প্রথমে পাঠে মনে হয় লেখক যেন ধর্মেরই জয়গান গাইছেন; কিন্তু তাই কী? আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও আসলে এ হলো মানবতাবাদের সুন্দর পদ্যময় উপস্থাপন, ধর্ম তার অনুষঙ্গ মাত্র।
উপন্যাসের নায়ক গোরা, যাকে চরম ধার্মিক করে দেখানো হয়েছে; কিন্তু সে জানে না যে ধর্ম তার শক্তি, তার আশ্রয়স্থল সে ধর্মে তার কোনো অধিকারই নেই। সে আইরিশ। জন্মসূত্র ছাড়া মুসলমান হওয়া যায়; কিন্তু হিন্দু হওয়া যায় না। তথাপিও গোরার এই ধর্মবোধ আসলে মানবিক বোধের অন্যপ্রকাশ। গোরা তখন যে সমাজ ব্যবস্থায় ছিল তাতে মানুষকে জাগানো খুব কঠিন ছিল মানবিক বোধ দ্বারা। তাই তৎকালীন ইংরেজ শাসনামলে গোরা ধর্মকে বেছে নেয় তার আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে, কেননা এই ধর্মের ব্যাপারে সকল মানুষই সব সময়ই দুর্বল। ধর্মবোধের কারণে যদি তারা মানবিক হয়ে ওঠে সেটাই ছিল গোরার মূল লক্ষ্য, ধর্মপ্রচার বা প্রসার নয়। তাইতো প্রায়শ্চিত্ত করার আগেও গোরার মনে সন্দেহ উঁকি দেয় যে, কেন সে প্রায়শ্চিত্ত করবে? করলেও তা কি ঠিক হবে?
এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আরেকটি শক্তিশালী চরিত্র লালিতা। যে বিনয়ের জন্য তার সমস্ত ত্যাগ করে তার সংসার করতে চলে আসে সমাজের প্রবল বাধা সত্ত্বেও। স্থির বক্তব্য প্রকাশে যার মধ্যে নেই কোনো শঙ্কা, নেই কোনো ভয়।
এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই অসাধারণ জীবন্ত। যে যার মতো যেভাবে প্রকাশ করেছে তাদের নিজস্ব ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথ সে প্রকাশভঙ্গি প্রকাশে দেখিয়েছেন অসাধারণ চমৎকারিত্ব যেন সত্যিই তারা আমাদের সামনে জীবন্ত। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আনন্দময়ী, পরেশবাবু হয়তো অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সাহস দেখাননি; কিন্তু ভালোর সমর্থন করতে পিছপা হননি। তাই তাদের মহিমানিত্ব করেছে বহুলাংশে; কিন্তু বিনয়কে মনে হয়েছে একতাল কাদা! যখন যেভাবে যে তাকে সেই আদল দিতে চেয়েছে সে সেই আদলই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছে কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই, যা কোনো চরিত্রেরই কাম্য নয়।
চমৎকার একটি উপন্যাস এই গোরা। যেখানে লেখক মানবতার জয় ঘোষণা করছেন আনন্দময়ীর দ্বারা, গোরার দ্বারা যা লেখক চেয়েছেন সর্বান্তকরণে তথাপিও উপসংহারে গোরার অভিব্যক্তি, যা তাঁর জন্মে, তাঁর ধর্মের অনুকূলে ছিল না তাতে একটু অনাদরের ছাপ পরিলক্ষিত।
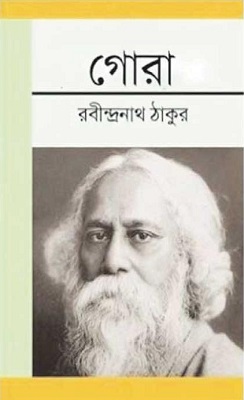
কেননা কেউ যদি বহু বছর পর জানতে পারে যে- সে যে বাড়ির সদস্য, যে ধর্মের অনুসারী তা কোনো কিছুই তার নয়, তখন স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ করাটাও অস্বাভাবিক। কেননা এগুলো মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; কিন্তু লেখক যদি এই অস্বাভাবিক আচরণকে মানব ধর্মের জয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান- তবে ঠিক আছে; কিন্তু স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। যেমনটা সপ্তপদীর রিন। ব্রাউনের অভিব্যক্তিতে ছিল নিজেকে হারানোর চরম উপলব্ধি। সহজ, সাধারণ প্রকাশ, গোরা ঠিক তার উল্টো কারণ- সে মানব ধর্মের মূর্তি, মানবিকতার প্রতীক। গোরার চরিত্র সে জন্য নমস্য। তবে আরও ভালো হয়ে উঠতো যদি লেখক আরেকটু সময় নিয়ে, আরেকটু সুচারুভাবে সমাপ্তিটা টানতেন! সেক্ষেত্রে মানবিকতার সব দিকগুলোয় পরিস্ফুটিত হতো চমৎকারভাবে।
পরিশেষে এ কথা বলা যায়- সমাজের সুন্দরের চর্চা ও মানবিকতার পাঠ নেওয়ার ক্ষেত্রে এ উপন্যাস অবশ্য পাঠ্য এবং অপরিহার্য একটি আখ্যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে একটি শিক্ষা নেওয়ার নতুন দিক দেখিয়েছেন, তা কারও এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়- কেননা সমাজ সংসারে শেষাবধি টিকে থাকে মানবিকতা।
