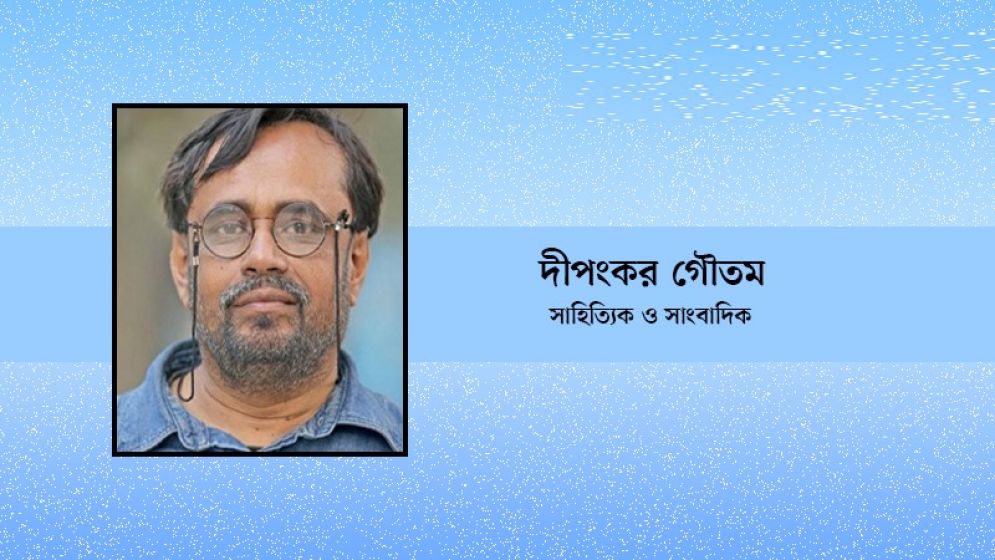
বিচারগান লোকসংগীতের একটি অনন্য ধারা। এই গানে দুটি পক্ষ থাকে, দুই পক্ষের দুজন দলপ্রধান বা পদকর্তা থাকেন। তাদের সঙ্গে থাকে দোহার বাদকরা। তবে লোকসংগীতে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো সহযোগী শিল্পী বা দোহার, যারা একই সঙ্গে যন্ত্রীও। সারা দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যা নামলেই শুরু হয় বাড়ির উঠোন বা স্কুল-কলেজের মাঠে সামিয়ানা টানিয়ে হ্যাজাকের আলোয় শুরু হয় এই গান। এখন বেশির ভাগ এলাকায় বিদ্যুতের আলো পৌঁছে যাওয়ায় হ্যাজাক লাইট আর চোখে পড়ে না। কথা ও সুর সহযোগে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিচার গান পরিবেশন করা হয়।
বিচার গান মূলত আধ্যাত্মবাদী সাধন-ভজনের একটি পালাগান। অনেকটা কবি গানের মতোই। ভারতীয় গবেষকদের অনেকেই বলেছেন, কবিগান ও তরজা গান থেকে বিচারগানের উৎপত্তি। কিন্তু এর পক্ষে কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। তবে বিচারগানে কবিগানের আঙ্গিক আছে সত্য, কারণ লোকসংগীত ও লোকনাটকের বিভিন্ন উপাচারের সঙ্গে মিল আছে। ‘বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংগ্রহমালা : বিচারগানে’ বলা হয়েছে, গৌড়ীয় কীর্তনের আঙ্গিকের সঙ্গে বাউল গানের যোগ ঘটিয়ে বিচারগানের প্রবর্তন। তবে এ কথা ঠিক যে একসময় এ গান বাউলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাউলদের মধ্যে সাধন-ভজন সংক্রান্ত মৌলিক কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে গানের মাধ্যমে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা হতো।
 বিচারগানের আসরের একটি দৃশ্য।
বিচারগানের আসরের একটি দৃশ্য।
কালক্রমে এ ধারার বিস্তার ঘটে এবং কাহিনির বিবর্তন ঘটে ও বাউল মতাদর্শের বাইরের লোকও এ গানের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিচার গানের আসর সাজানো হয় গোল আকৃতিতে, খোলা জায়গায় সামিয়ানা টানিয়ে-দুজন গানের দলের প্রধান মুখোমুখি হয়ে বসতেন, সাধারণত দর্শক-শ্রোতাদের মাঝখানে। দুজন গায়ক বা সরকারের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা হয়। প্রথমে বিষয় নির্বাচন করে পরে দুজন বয়াতির একজন পক্ষে এবং অন্যজন বিপক্ষে থেকে নিজ নিজ যুক্তিসহ গানের কথায় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বিচারগানের বিষয় প্রধানত-শরিয়ত, মারফত, নবীতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব, যৌবনতত্ত্ব প্রভৃতি। এ ছাড়া নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য প্রভৃতি বিষয় নিয়েও এ গানের প্রতিযোগিতা হয়।
বিচারগান দীর্ঘ সময় ধরে পরিবেশিত হয়। গান পরিবেশনকালে মূল গায়েন দাঁড়িয়ে গান করেন এবং দোহাররা তার সঙ্গে ধুয়া ধরে। সাধারণত এসব গানের দর্শকের বেশির ভাগই শ্রমজীবী মানুষ। স্রষ্টার বন্দনা দিয়ে শুরু হয় গান-বেজে ওঠে দেশীয় খোল-করতাল, দোতারা, খঞ্জনি-বেহালা, জুড়ি, বাঁশি ও হারমোনিয়াম। যন্ত্র ও সুরের সহযোগে যে আবহ তৈরি হয় তার মধ্যে অচিরেই হারিয়ে যায় দর্শক-শ্রোতা।
আমাদের দেশের মফস্বল অঞ্চলের সংস্কৃতিচর্চার একটি নিজস্ব দিক রয়েছে । সেটা হোক জারি-সারি, বৈঠকী গান বা পুঁথিপাঠ, সবকিছুর সঙ্গে ফসল তোলার যেমন একটা দিক আছে, আছে একসঙ্গে উৎসব উদযাপনের একটা বর্ণিল সরলতা। মানুষে-মানুষে যে আত্মার বন্ধন তার সবটাই মানুষের পারস্পরিক বন্ধনকে ঘিরে। অলস পলির মায়ায় বিধৌত এ অঞ্চলের লৌকিক ধর্মীয় উপাচার সবচেয়ে বেশি। মানুষ পরিশ্রম শেষে স্রষ্টাকে ডাকে, গানের মধ্যে প্রতিভাত হয় সেসব গাঁথা। মানুষ গানের ভেতরে খোঁজে তার আরাধ্য নিরঞ্জনকে। গানের আসরে গায়ক-শ্রোতা সবার যে কাতর আকুতি তা এক হয়ে যায়। গানের আসরে সবাই কান্না করে, কতটা সারল্য নিয়ে একজন আরেকজনকে ধরে কাঁদে তা না দেখলে বোঝা যাবে না।
সারা বাংলার মফস্বলের মানুষের এসব সংগীত যেন আত্মার খোরাক বা বেঁচে থাকার উপজীব্য। এখানের মানুষ জোছনার আলোয় বিশাল আকাশের নিচে বসে যে সুর তোলে তার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মবোধ ও মানবপ্রেমকে অন্তরে ধারণ করে। এ রকম অজস্র লোকাচারের মতো লোকসংগীতের ধারা-উপধারার সৃষ্টি হয়েছে। বিকশিত হয়েছে লোকসংগীতের অজস্র শাখাÑতারই একটি ধারা বিচারগান। যুগের পর যুগ বিচারগানের আসর সলতে জ্বলা প্রদীপের মতো টিকে আছে গ্রামে-গঞ্জে।
বিচারগান শুনলেই আদালতের একটি বিষয় মাথায় আসে। যেখানে একজন বিচারক থাকে আর থাকে অনেক উকিল, সেরেস্তাদার আরো কত কি! কিন্তু বিচারগানের আসরে যেসব বিষয় নিয়ে গানের সুরে পদকর্তারা আলোচনা করেন। তা জীবনের অন্তর্গত গুঢ়তত্ত্ব। আমাদের স্বশিক্ষিত গায়েনরা লোক নাটকের ঢঙে উপস্থাপন করে সৃষ্টিতত্ত্বসহ বিভিন্ন বিষয়। তার সঙ্গে তাল মেলায় দর্শক। তারাই বিচারক। প্রতিযোগিতামূলক এ গান গ্রামীণ মানুষের প্রাণ। জীবনের মানসিক এবং আত্মিক দিকের, যা বস্তুগত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বাইরে অবস্থিত তার চর্চা হয় এখানে। আবেগে আহ্লাদে এখানে গীত হয়-‘সপ্ততালা আসমান জমিন/এই মানুষের মধ্যে ঘেরা/চৌদ্দ ভুবন জোড়া মানুষ/চৌদ্দ ভুবন জোড়া।’ ব্যাপক বিতর্কের মধ্য দিয়ে এ গান রূপ পায় সমন্বয়ের। রাত বাড়তে থাকে। তাদের সুরের জাদুতে মানুষ বিমোহিত হতে হতে একসময় দুজন দলপ্রধান বিতর্কের অবসান করে। গান শেষ হয়, প্রতিযোগিতামূলক তর্ক-বিতর্ক একটি স্বতন্ত্র রূপ পায়। তখনো দর্শক যেন গানের শিল্পীদের সুরের সঙ্গে নিজেদেরও একাকার করে দিয়ে গাইতে থাকে। বিভিন্ন বয়সী মানুষের এ সম্মিলন আনন্দ স্নানের মতো। এখান থেকে মানুষ নিতে পারে সহনশীলতার দীক্ষা। কারণ বিচারগানে দুজন গায়েন বা সরকার একটি বিষয় নিয়ে কবি লড়াইয়ের মতোই গানের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করেন না। এভাবেই কথায়, সুরে বিচারগান ও বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতি ধারণ করেছে মানবধর্ম ও অসাম্প্রদায়িকতার নির্যাস।
এখানের স্বশিক্ষিত শিল্পীরা গায়-‘মনো রে, আগে ছাড় জাতিবিদ্যা/ঘৃণা লজ্জা হিংসা নিন্দা/এসব থাকলে সাধন হবে না।’ এই অসাম্প্রদায়িকতা, বিদ্বেষহীনতার শিক্ষা বিচারগান থেকে নেওয়া যায়। তার পরও যে সত্য তাহলো বিচারগান এখন প্রায় বন্ধের পথে। এখন গান করতে, গানের জমায়েত করতে অনুমতি লাগে। সব সময় অনুমতি মেলে না। আবার সাধারণ মানুষ অনুমতি দেওয়া লোকটির কাছে পৌঁছতে পারে না। এমন অজস্র কারণে আটকে আছে লোকসংস্কৃতির অনন্য শাখা ‘বিচারগান’। নদী- খাল-বিলের মতো এসব অনুষঙ্গ হারিয়ে গেলে হারিয়ে যাবে শিকড় সংস্কৃতি। যেটা কোনো মতেই কল্যাণকর নয়।
