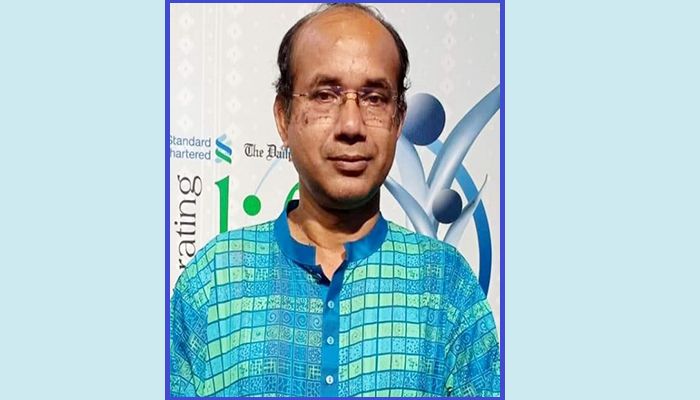
গণমাধ্যমে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ নিয়ে কমবেশি লেখালেখি হলেও আমরা একটি আদর্শ অবস্থান বেছে নিতে পারিনি। এ আমাদের জাতীয় দৈন্য। এক সময় ‘দৈনিক সংবাদ’-এ যশোর থেকে প্রবোধচন্দ্র সাহা এবং নাটোর থেকে এম এ সামাদ নামে দুই স্কুলশিক্ষক চিঠিপত্র লিখে বানান ভুল ও ভাষার অপপ্রয়োগ নির্দেশ করতেন।
পরে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রণজিৎ বিশ্বাস ‘ব্যবহারিক বাংলায় ভ্রমকণ্টক’ নামে কলাম নিবন্ধে ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার একক আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। কবি-সাংবাদিক অরুণাভ সরকার সংবাদপত্রে ভাষার অপপ্রয়োগ নিয়ে বেশ কিছু নিবন্ধ রচনা করেছেন। তার লেখা একটি গ্রন্থ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
তর্কাতীত না হলেও তার বক্তব্য বাংলা ভাষা ব্যবহারে সুচেতনা সৃষ্টির সহায়ক বলে আমার ধারণা। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ‘সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা’ নামের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। এ ছাড়া ড. হায়াৎ মামুদ, ড. মাহবুবুল হক ও দিলীপ দেবনাথ রচিত ভাষা ও বানান বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য খুবই দরকারি।
অক্টোবরের ১ তারিখ যখন এই নিবন্ধ রচনার জন্য কম্পিউটার খুলে বসি, তখন আমার হাতের কাছে ছিল ‘আমাদের সময়’ পত্রিকা।
এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করার কৃতিত্ব দাবি করলেও এর ভাষার শুদ্ধতা নিয়ে সংশয় কাটাতে পারিনি। আমি তাই ‘আমাদের সময়’-এ প্রকাশিত কোনো নিবন্ধ বা প্রতিবেদনকে নমুনা হিসেবে নিতে চাইনি। পত্রিকাটি এ দিন প্রকাশ করে ‘চ্যানেল আই’-এর একাদশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র। ওই ক্রোড়পত্রের মূল রচনাটিকে আমি নমুনা হিসেবে গ্রহণ করি মূলত তিনটি কারণে-
১. নিবন্ধের লেখক বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা সম্পাদক ও প্রকাশক
২. নিবন্ধের বিষয় বাংলাদেশের গণমাধ্যম
৩. নিবন্ধটি বিশেষ উপলক্ষে ক্রোড়পত্র আকারে সযত্নে প্রকাশিত
‘চ্যানেল আই আমাদেরকে আশান্বিত করে’ শিরোনামে আপাত দৃষ্টিতে ভুল দেখা না গেলেও এটি যে ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, তা-ও জানা থাকা দরকার। ‘ইত’ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ বসে কর্মবাচ্যে। তাই আশান্বিত (আশা+অন্বয়+ইত) করে হতে পারে না, হতে পারে ‘আশান্বিত হই’। তাই শিরোনামটি হতে পারত, ‘চ্যানেল আই আমাদের আশা জাগায়’ অথবা ‘চ্যানেল আই দেখে আমরা আশান্বিত হই’।
প্রথম বাক্যে লেখা হয়েছে, ‘চ্যানেল আই’র ১১ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে..’। হতে পারত একাদশ বর্ষে বা বছরে। ১১টি বছরে একসঙ্গে পা দিতে পারে না, দিতে পারে ১টি বছরে। সেই ১টি বছর হলো ১০ বছর পরের বছর অর্থাৎ একাদশ বছর। দ্বিতীয় বাক্যে লেখা হয়েছে, ‘... সৃজনশীল টিভি চ্যানেল দেখার সৌভাগ্যবান দর্শক’। একই বাক্যে ‘দেখার’ আর ‘দর্শক’ শব্দের প্রয়োগ শ্রুতিকটু। হতে পারত ‘...সৃজনশীল টিভি চ্যানেলের সৌভাগ্যবান দর্শক’। লেখা হয়েছে, ‘... টিভি নিউজ সাংবাদিকতার আরেকটি নতুন দিক।’ সাংবাদিকতা শব্দের মধ্যেই তো ‘নিউজ’ বা ‘সংবাদ’ শব্দটি রয়েছে। তাই হতে পারত ‘... টিভি সাংবাদিকতার আরেকটি নতুন দিক’। লেখা হয়েছে, ‘...একদিকে রাজনীতিক অঙ্গনে যেমন জবাবদিহির চর্চা শুরু হয়েছে...’। ‘রাজনীতিক’ বলতে ‘রাজনীতিবিদ’ অর্থাৎ ব্যক্তি বোঝায়। আর ‘জবাবদিহি’ নামের কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় নেই। তাই বাক্যটি হতে পারত, ‘...একদিকে রাজনৈতিক (বা রাজনীতির) অঙ্গনে যেমন জবাবদিহির চর্চা শুরু হয়েছে...’।
লেখা হয়েছে, ‘...আর এর পেছনে অবশ্যই চ্যানেল আই-এর সব সাংবাদিক, শিল্পী, কর্মকুশলীসহ সকল স্টাফদের অপরিসীম পরিশ্রম ও নিষ্ঠা রয়েছে’। একই বাক্যে ‘সব’ ও ‘সকল’ ব্যবহারের উপযোগিতা আমাদের বোধগম্য নয়। তাছাড়া ‘সব’, ‘সাথে’ প্রভৃতি শব্দ কবিতা ও গানে বেশি মানায়। এগুলো ভাষাবিদের কাছে ‘ব্যাড প্রোজ’ বা মন্দ গদ্য হিসেবে চিহ্নিত। এর পরিবর্তে ‘সকল’ কিংবা ‘সঙ্গ’ ব্যবহার করাই শ্রেয়। তারপরেও কথা থেকে যায়। বাংলা ভাষায় বহুবচনের দ্বিত্ব হয় না। তাই ‘সকল স্টাফদের’ চলে না। হতে পারত ‘সকল স্টাফের’।
লেখা হয়েছে, ‘টেলিভিশনকে কাজে লাগিয়ে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে যে বিপুল অবদান রাখা যায় তার প্রমাণ শাইখ সিরাজ’। লেখকের বক্তব্য এখানে অস্পষ্ট। শাইখ সিরাজ-ই কি তার প্রমাণ? নাকি প্রমাণ তার কর্মকা- বা অনুষ্ঠান? নাকি শাইখ সিরাজ তা প্রমাণ করেছেন? ‘টেলিভিশনকে কাজে লাগিয়ে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে যে বিপুল অবদান রাখা যায়, শাইখ সিরাজ তা প্রমাণ করেছেন’- এরকম বলা হলে কিছুটা হয়তো স্পষ্ট হত।
লেখা হয়েছে, ‘...যার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীব্যাপী দেশের গানবাজনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।’ এখানে ‘পৃথিবীব্যাপী দেশের গানবাজনা’ শুনলে কি আরাম লাগে? দেশের গানবাজনা
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দেওয়ার কথা হয়তো লেখক বলতে চেয়েছেন। তাই শব্দের স্থান বদল করে লেখা যেত, ‘... যার মধ্য দিয়ে দেশের গানবাজনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীব্যাপী মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।’ যথাস্থানে যথাশব্দের প্রয়োগ না হওয়ায় অর্থবিপত্তি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।
লেখা হয়েছে, ‘...এবং সংবাদে আরো উন্নততর প্রয়াস গ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে টেলিভিশনের অবদানের এক নতুন দৃষ্টান্ত গড়ে তুলবে’। ‘আরো উন্নততর প্রয়াস’ হতে পারে না। হতে পারে ‘উন্নত প্রয়াস’ অথবা ‘উন্নততর প্রয়াস’। আরও উন্নত মানেই তো উন্নততর। বাংলা ভাষাকে আপন করে না নিতে পারলে, এ ধরনের অপপ্রয়োগ ঘটতেই থাকবে বলে আমার আশঙ্কা।
এই নিবন্ধে আরও কিছু ভুল রয়েছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথে আমরা আর এগোচ্ছি না। আবার বিশ্লেষণের জন্য কেবল একটি নিবন্ধও যথেষ্ট নয়। গোটা পত্রিকাকে নমুনা ধরলে, এ ধরনের ভুলের তালিকা আরও বাড়ানো যায়। দেশের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিকের ছোট্ট একটি নিবন্ধে যদি এই ধরনের ভুলের সমাহার থাকে, তাহলে অন্য লেখকদের রচনায় কেমন ভুল থাকতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।
গণমাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ দূর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এবং বাংলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠান পদক্ষেপ নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগও এই বিষয়ে পাঠদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারে। আমরা জানি, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান সম্প্রতি উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলা ব্যাকরণ রচনার। একটি সমন্বিত ব্যাকরণ প্রণীত হলে, ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের সীমারেখা নির্ধারণ করা যাবে। কিন্তু তা মান্য করার দায়িত্ব নিতে হবে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদেরই। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি।
কৃষি প্রতিবেদনের ভাষা
প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে উন্নয়ন প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে কৃষি একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কিন্তু কৃষি বিষয়টি এত জটিল ও প্রযুক্তিগত যে, এর ভেতরের বিষয় না জানা থাকলে প্রতিবেদন রচনা সম্ভবপর নয়। কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন রচনার কাঠামো কিংবা প্রকরণে আপাত কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও তথ্য-উৎস, তাৎক্ষণিকতা, ভাষা প্রয়োগ, প্রযুক্তিজ্ঞানের কারণে তা অন্য উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। কৃষি প্রতিবেদন রচনার জন্য ধান, পাট, গম, ইক্ষু, চা, মৎস্য, ফল, পশুসম্পদ, সেচ, বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হয়।
আমাদের অর্থনীতিতে এক বিশেষ জায়গাজুড়ে রয়েছে
কৃষি। এখানে কৃষি বলতে শস্য, ফল, পশু ও মৎস্য সম্পদকেও বোঝায়। জিডিপিতে এই কৃষির অবদান ২১.৯১ শতাংশ। এর মধ্যে কৃষিশস্যের অবদান অর্ধেকেরও বেশি (১২.১০ শতাংশ)। এর মধ্যে আবার ধানশস্যের অবদান সর্বাধিক (১০ শতাংশ) এবং সামগ্রিক বিচারে পুরো ফসলের ৮৩ শতাংশ। দেশের আবাদি জমির ৭৬ শতাংশ জমিতে ধানের আবাদ করা হয়। সামগ্রিক শ্রমশক্তির বিচারে কৃষি শ্রমশক্তির পরিমাণ ৫১.৬৯ শতাংশ। এই শ্রমশক্তির ৫৫ শতাংশজুড়ে ধান। অর্থাৎ আমাদের কৃষি একান্তভাবেই ধানভিত্তিক কৃষি। আমরা কৃষি সাংবাদিকতা তথা কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার জন্য ধানশস্যকে বেছে নিতে চাই।
কৃষিতথ্য বিশেষত ধানবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য ধানের ক্ষেতই হতে পারে প্রধান তথ্য-উৎস। অর্থাৎ ক্ষেতের দিকে তাকিয়েই সাংবাদিকের বুঝে নিতে হয়- এবারে ধানের ফলন কি লক্ষ্যমাত্রা পেরোবে নাকি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে অর্থাৎ ফলন বেশি হলে এটি সংবাদ হিসেবে গণ্য হতে হবে। আবার ফলন কম হলেও তা নিয়ে সংবাদ তৈরি হতে পারে। কিন্তু প্রতিবেদকের জানা দরকার, কতটুকু জমিতে কতটুকু ফলন হয়। তার ব্যত্যয় ঘটলেই সংবাদের উপকরণ হতে পারে। এই উপকরণকে সংবাদ হিসেবে তৈরি করতে তখন আনুষঙ্গিক তথ্য জোগাড় করতে হয়। তার জন্য সাংবাদিকের কাছের উৎস হতে পারেন আশপাশের
কৃষক। স্থানীয় ব্লক সুপারভাইজার, কৃষি অফিস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের শাখা, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিকটতম শাখা, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন কিংবা সার ও বীজের ডিলারদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাদের কাছে তথ্য আছে, কিন্তু কী তথ্য দরকার হবে, তা নির্ধারণ করা না গেলে একটি ভালো রিপোর্টও ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে আমাদের সামগ্রিক কৃষিতে।
উদাহরণ হিসেবে দৈনিক ‘প্রথম আলো’র একটি সংবাদেও নমুনা বিশ্লেষণ করা যাক। ‘রাজশাহীতে এবার পারিজা ধানের ব্যাপক ফলন’ শিরোনামের এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, ‘রাজশাহী অঞ্চলে ...হাইব্রিড, উচ্চফলনশীল (উফশী) ও স্থানীয় জাতের মধ্যে পারিজা ধানের চাষাবাদই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বেশি ফলন পাওয়া যায় বলে কৃষকরা দিনদিন এই ধানের আবাদে ঝুঁকে পড়ছেন।’
এই রিপোর্ট লিখতে গেলে হাইব্রিড, উচ্চফলনশীল (উফশী) এবং পারিজা ধান সম্পর্কে সামান্য হলেও জানতে হবে। পারিজা ধান ‘হাইব্রিড’ নয়, বাংলাদেশের উফশীও নয়। এটি ভারতের ইনব্রিড জাতের একটি ধান, যা বাংলাদেশ সরকারের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির অনুমোদন লাভ করেনি। এটি চোরাপথে বাংলাদেশে এসেছে। তা যে পথেই আসুক, এটি আমাদের দেশিয় জাত নয়, হাইব্রিডও নয়। তাই রিপোর্টের তথ্য ঠিক নয়। প্রযুক্তিগত ধারণার অভাবে অনেক ভালো তথ্যও খারাপ রিপোর্টে পরিণত হতে পারে, এই প্রতিবেদন থেকে তা বোঝা যায়। ‘পারিজা’ যে ভারতীয় জাত, তা কিন্তু রিপোর্টার জানেন, ‘রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গতবার রাজশাহী অঞ্চলে যেখানে এক লাখ ৭১ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়েছিল, সেখানে এবার হয়েছে দুই লাখ ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে।
এর মধ্যে ৭৭ হাজার হেক্টর জমিতেই আবাদ হয়েছে পারিজা ধানের। কৃষকরাই প্রতিবেশী ভারতে উদ্ভাবিত এই জাতের ধান সংগ্রহ করেন।’ তাহলে ‘প্রতিবেশী ভারতে উদ্ভাবিত’ জাতকে ‘স্থানীয় জাত’ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে যখন এই তথ্য জানা গেল, তখন প্রতিবেদক এবং বিভাগীয় সম্পাদক এখানে আরেকটু নজর দিতে পারতেন। একই প্রতিবেদনে আবার লেখা হয়েছে, ‘কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কম সেচে ও অল্প সময়ের মধ্যে বেশি ফলন হয় বলে কৃষকদের এবার পারিজাসহ আউশ ধানের চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এতে তারা ব্যাপকভাবে সাড়া দেন। বদৌলতে এবার রাজশাহীতে আউশ ধান চাষের পরিমাণ বেড়ে প্রায় দেড় গুণ বেশি হয়েছে।’ এখানে মারাত্মক একটি তথ্য রয়েছে। ‘পারিজা’ জাতটি ভারতীয় এবং তা কৃষকরা নিজের উদ্যোগে সংগ্রহ করেন। এর অনুমোদন নেই ‘বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি’র। তাহলে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই জাত চাষে উদ্বুদ্ধ করে কোন অধিকার ও আইনের বলে। এ ব্যাপারে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির অভিমত ছাড়া এই রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
ফসলের ক্ষেত ও কৃষক ছাড়া কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদনের জন্য যে সকল উৎস ব্যবহার করা যেতে পারে, তা হলো-
১. ব্লক সুপারভাইজার/ থানা কৃষি অফিস/কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তর
২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
৩. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)
৫. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
৬. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
৭. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)
৮. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)
৯. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)
১০. বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)
১১. বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)
১২. মৃত্তিকা-সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)
১৩. বাংলাদেশ বন গবেষণা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)
১৪. কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ডি)
১৫. বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি)
এ ছাড়া আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, যেমন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এবং আরও অনেকের কাছে পাওয়া যাবে খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক তথ্য।
কৃষি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ হলো পত্রিকার জন্য দায়িত্বশীল কাজ। এর জন্য দরকার দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা। কেবল প্রতিবেদন-কৌশল জানলেই চলবে না, তার সঙ্গে যুক্ত করতে হয় কৃষিপ্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান। প্রতিবেদকের পাশাপাশি বিভাগীয় সম্পাদককেও সজাগ থাকতে হয়। যথাপ্রযুক্ত শব্দ প্রয়োগ ছাড়া কৃষি প্রতিবেদনে যথাতথ্য প্রকাশ করা যায় না। আর একজন সাংবাদিককে জানতে হয়, সরকারের কৃষি অফিস কী কী কাজ করে।
সরকারের ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে সরকারি ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাদে অন্যান্য দিন কৃষিবিষয়ক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। কোনো কারণে সেখানে তথ্য না পেলে তা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। অভিযোগ পাওয়ার পর তিনি পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অন্যথায় উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবহিত করা যাবে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য পাওয়া যাবে।
প্রত্যেক উপজেলায় ও জেলা দপ্তরে মাটির নমুনা পরীক্ষার জন্য সয়েল মিনিল্যাব সরবরাহ করা আছে। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের সহায়তায় মাটির নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা দপ্তরে প্রেরণ করলে মাটি পরীক্ষা করে ফসলের সার সুপারিশমালা প্রদান করা হয়। সেখান থেকেও তথ্য পাওয়া যায়।
বন্যায়/অতিবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন প্রেরণ করার দায়িত্ব স্থানীয় অফিসের। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের তালিকা তারা প্রণয়ন করে। কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ (সার, বীজ/চারা) সংগ্রহ করা, তা ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষিদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও যাবতীয় কাজ তদারকি করা হয়। সেখান থেকে খবরের উপকরণ বের করা যায় সহজেই।
আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ‘দাউদকান্দিতে হস্তচালিত ধানকাটা যন্ত্র প্রদর্শন’ শিরোনামে সংবাদ পড়লে পাঠকের মনে প্রত্যাশা জাগবে, এই ধরনের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ধারণা জাগবে। কিন্তু রিপোর্টে তা নেই। ‘প্রথম আলো’র দাউদকান্দি প্রতিনিধির পাঠানো রিপোর্টে আছে, ‘দাউদকান্দি উপজেলার জয়বাংলা বাজার মাঠে সম্প্রতি হস্তচালিত ধানকাটা যন্ত্রের এক প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। ...এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিটেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক এ এইচ ইকবাল আহমেদ ও উপপরিচালক মো. হাসান, দাউদকান্দি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তপনরঞ্জন মজুমদার ও উপসহকারী কর্মকর্তা জাবিউল্লাহ এবং কৃষক নূরনবী, আমির হোসেন ও সরদার মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন।’ এটি হয়ে গেছে অনুষ্ঠানের সংবাদ। কিন্তু কৃষি যন্ত্রপাতির বিবরণ থাকলে একে
কৃষিবিষয়ক রিপোর্ট করে তোলা যেত।
কৃষি প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। বুঝতে হয়, ফসলের মৌসুম অর্থাৎ কোন ফসল কোন মৌসুমে হয়, সে সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রাখতে হয়। আবহাওয়া এবং জলবায়ুর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। ধরুন, খরায় একটি এলাকায় ফসল নষ্টের আশঙ্কা নিয়ে প্রতিবেদন রচনার কথা ভাবলেন একজন প্রতিবেদেক। এ ধরনের সংবাদ এমন নয় যে, এক্ষুণি প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু আবার এমন যদি হয় যে, তথ্য সংগ্রহ করতে করতে তিন-চার দিন লেগে গেল, এর মধ্যে বৃষ্টি এসে গেল। তাহলে ওই সংবাদ প্রকাশোপযোগিতা থাকে না। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সেচÑ এ ধরনের বিষয় নিয়ে সংবাদ রচনার সময় অযথা সময়ক্ষেপণ করার সুযোগ নেই। তাতে একটি চমৎকার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে নিমিষেই। এই ধরনের
প্রাকৃতিক সমস্যাভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকতার প্রতি জোর দিতে হয়। একটি মৌসুমে কখন বীজ বুনতে হয়, সেচ দিতে হয়, কখন কীটনাটক দিতে হয়, কখন সার দিতে হয়, কখন ফসল ঘরে তুলতে হয়Ñ তা বিশদ করে জানতে হয়। অর্থাৎ সময়জ্ঞানটা খুবই জরুরি।
কৃষি প্রতিবেদনে ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিক সচেতন থাকা দরকার। ভাষা কিংবা শব্দ প্রয়োগের একটু হেরফের হওয়ার কারণে একটি তথ্য ভুল অর্থ বয়ে আনতে পারে। ‘ডুমুরিয়ায় বাংলামতি ধান একরে হয়েছে ৭০ মণ’ শিরোনামের এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে-
খুলনা অঞ্চলে ডুমুরিয়া উপজেলার কার্তিকডাঙ্গা বিলে প্রথমবারের মতো চাষ হওয়া বাসমতি সদৃশ ‘বাংলামতি’ ধান আনুষ্ঠানিকভাবে কাটা হয়েছে। ১৯ এপ্রিল উপজেলা
কৃষি কর্মকর্তারা আংশিক কাটা ধানের গড় করে জানিয়েছেন, একরে ৭০ মণ ফলেছে।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক এস এম আতিয়ার রহমান কার্তিকডাঙ্গা বিলে তার চিংড়ি ঘেরে এক একর জমিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ব্রি-৫০ জাতের বাংলামতি ধান চাষ করেন। তিনি সুপার রাইস বাংলামতি ধান চাষ করে সফল হওয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের দাবি, তাদের উদ্ভাবিত এ ধানের নাম বাংলামতি হলেও এটা গুণে-মানে ও স্বাদে বাসমতিরই নামান্তর। ধানচাষি আতিয়ার রহমান বলেন, ‘বাংলামতি ধানের ফলন ব্রি-২৮ জাতের সমান হওয়ায়
কৃষক ও কৃষিবিদরা দারুণ উৎসাহিত হয়েছেন। আমি চাই আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ অঞ্চলের কৃষকরা মূল্যবান বাংলামতি ধান চাষে এগিয়ে আসুক।’ ওই ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শিখা রানী ম-ল জানান, কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে আতিয়ার রহমানের এক একর জমিতে ৭০ মণ বাংলামতি ধান হয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পঙ্কজ কান্তি মজুমদার বলেন, ‘বাংলামতি ধানের ফলন দেখে আমি অভিভূত। কারণ অন্য ধানের তুলনায় এ ধানের দাম অনেক গুণ বেশি। চাষিরা মূল্যবান এ ধান চাষ করলে অনেক লাভবান হবেন।’
এখানে আমাদের আপত্তি ‘সুপার রাইস’ শব্দটি নিয়ে। এটি একেবারেই টেকনিক্যাল শব্দ। ফলন বেশি হয়েছে বলেই ‘বাংলামতি’কে সুপাররাইস বলা যায় না। ফিলিপাইনে ‘সুপাররাইস’ জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। ‘সুপার হাইব্রিড রাইস’ নামেও একটি জাত আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো ‘সুপার রাইস’ নামের কোনো জাতের ধান নেই। তাই ওই প্রতিবেদনে এই শব্দটি যথাপ্রযুক্ত নয়। এমনকি বৈজ্ঞানিক সত্য নয় এমন একটি তথ্য এখানে প্রচার করা হয়েছে। এতো গেলো টেকনিক্যাল শব্দের কথা। এবার সাহিত্যেও শব্দের বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। ‘নতুন ধানে হবে রে নবান্ন’ নামের প্রতিবেদনে ‘প্রথম আলো’ লিখেছে-
‘নতুন ধানে হবে রে নবান্ন’-এ কথা মাথায় রেখেই বগুড়া জেলার বিভিন্ন এলাকার চাষিরা আগাম রোপণ করা বোরো ধান কাটা শুরু করেছেন। এই ধান হাটে উঠতে শুরু করেছে। গত বছরের তুলনায় দাম এবার ভালো পেয়ে চাষিরাও খুশি।’
আমাদের এবারের আপত্তি শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ নিয়ে। এটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা ‘শরৎ’-এর চরণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কবিতাটি এমন-
জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে-
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিকো তোমার-
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী, তোমার আহ্বান লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
(শরৎ)
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘নূতন ধান্যে হবে নবান্ন’, আর আমাদের প্রতিবেদক লিখেছেন, ‘নতুন ধানে হবে রে নবান্ন’। ‘নূতন’ হয়ে গেছে ‘নতুন’, ‘ধান্যে’ হয়ে গেছে ‘ধানে’, ‘হবে’ হয়ে গেছে ‘হবে রে’। একটি জননন্দিত কবিতার এরকম বিকৃতি কখনো কাম্য নয়।
প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে অনেক প্রতিবেদন পাঠকের কাছে যথাযথ অর্থ বহন করে না। ‘ফরিদপুরে খোলাবাজারে চালের দাম বেড়েছে’ নামের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে-
ফরিদপুরে মোটা, মাঝারি, সরু- সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে। গত পাঁচ দিনে প্রতি কেজিতে দাম বেড়েছে গড়ে দুই টাকা।
খুচরা বিক্রেতাদের অভিযোগ, মিলার ও পাইকারি বিক্রেতাদের কারসাজিতে দাম বেড়েছে। পক্ষান্তরে পাইকারি বিক্রেতারা বলছেন, কৃষক মিলে ধান সরবরাহ না করায় চালের দাম বেড়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে খোলাবাজারে অস্ট্রেলিয়ান ইরির চাল প্রতি কেজি ২৮ থেকে বেড়ে ৩১ টাকা, স্বর্ণা ২৯ দশমিক ৫০ থেকে ৩২ দশমিক ৫০, মিনিকেট ৩৭ দশমিক ৫০ থেকে ৩৯ দশমিক ৫০, কাজল লতা ৩৪ থেকে ৩৬, ইরি-২৮ নম্বর ৩২ থেকে ৩৪, ইরি-২৮ এক নম্বরটা ৩৩ থেকে ৩৫ ও ইরি-২৯ নম্বর ৩১ থেকে ৩৩ টাকা হয়েছে।
বিক্রেতারা বলেন, বাজারে চালের ক্রেতা কম, সরকার সুলভমূল্যে বিভিন্ন পর্যায়ে চাল বিক্রি করছে, তারপরও চালের এ মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে মিলার ও পাইকারি বিক্রেতাদের কারসাজিতে। সাধারণত, বছরের এই সময় কখনোই চালের দাম বাড়ে না। ...ফরিদপুরের একাধিক পাইকারি চাল বিক্রেতা চালের মূল্য বৃদ্ধির কথা স্বীকার করে জানান, বর্তমানে মিলগুলো ধান পাচ্ছে না।
এখন কথা হচ্ছে, ‘অস্ট্রেলিয়ান ইরি’ নামে কোনো চাল নেই। ইরি হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান। ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইরি) নামের প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান ফিলিপাইনে। ‘ফিলিপাইনি ইরি’ হলেও কিছু একটা অর্থ দাঁড়াত। ‘অস্ট্রেলিয়ান ইরি’ নামে কোনো ধান থাকা সম্ভবপর নয়। ইরি-২৮ কিংবা ইরি-২৯ নামেও কোনো ধান নেই। আরও সোজা করে বলা যায়, ‘ইরি’ নামে কোনো ধানই নেই বাংলাদেশে। বাংলাদেশে আছে ব্রি-ধান। তাই ব্রি-ধান-২৮, বা ব্রি-ধান-২৯ বলা যেত। এলাকার মানুষ যে নামেই ডাকুক, জাতীয় পত্রিকায় তা নিয়ে প্রতিবেদন রচনার সময়ে যথাযথ প্রতিশব্দ ও পরিভাষার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। ‘করতোয়ার চরে ধান, কৃষকের মনে আশা’ নামের আরেক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে-
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় করতোয়া নদীর বুকে জেগে ওঠা চর নতুন আশার সঞ্চার করেছে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর কৃষকদের মধ্যে। ধু ধু বালুর চরটিতে এবারই প্রথম চাষ হয়েছে ইরি-বোরো ধান। গত বর্ষায় বিরাট এই চরটিতে প্রচুর পলি পড়ে। এক ফুটের মতো পলির স্তরে পার্শ্ববর্তী সাতবাড়িয়া, চরসাতবাড়িয়া, ঘাটিনা, চরঘাটিনা, লক্ষ্মীপুর, বড়লক্ষ্মীপুর ও গুচ্ছগ্রামের কৃষকেরা ধান চাষ করছেন। চরজুড়ে এখন সোনালি ধানের শীষ বাতাসে দোল খাচ্ছে।
‘ইরি-বোরো ধান’ শব্দটিও ‘সোনার পাথরবাটি’র মতো। ‘ইরি’ একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নাম, আর ‘বোরো’ একটি মৌসুমের নাম। এরকম ভিন্নমুখী দুটি শব্দের সহযোগে গঠিত ‘ইরি-বোরো’ কোনো ধানের নাম হতে পারে না। প্রতিবেদক এখানে ‘উচ্চফলনশীল বোরো ধান’ বা ‘উফশী ধান’ বোঝাতে চেয়েছেন। প্রযুক্তিগত ধারণার অভাবে এ ধরনের প্রতিবেদন রচিত হয়। কিন্তু প্রতিবেদনের শুদ্ধতা রক্ষায় এই সকল প্রযুক্তিগত শব্দের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়।
একটি খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে একজন বা একদল মানুষ। কিন্তু একটি কৃষি সংবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে দেশের সকল মানুষ। কৃষিবিষয়ক একটি সংবাদ দেশের অবস্থারও বদল করতে পারে। একটা উদাহরণ দিই। উত্তরবঙ্গের মঙ্গা নিরসন করা হচ্ছে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ব্রি-ধান-৩৩ সরাসরি বপন করলে ১০৩ থেকে ১০৫ দিন এবং রোপণ করলে ১১৫ থেকে ১১৮ দিন সময় লাগে। আশ্বিন-কার্তিক মাসেই ধানের কাটা শেষ হয়ে যাবে।
আর এ সময়েই মঙ্গা হয়। এই বিষয়টি প্রায় এক যুগ আগেই সকলের নজরে আনার চেষ্টা করেছিলেন ধানবিজ্ঞানী ড. ফরহাদ জামিল। তখন সরকার যদি এটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব দিত, তাহলে অনেক আগেই মঙ্গার আপদ কেটে যেত। কিন্তু গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটি আমলে আনে এবং উত্তরবঙ্গেও মঙ্গ নিরসনে এই জাতের ধান চাষের ওপর গুরুত্ব দেয়। আমাদের সংবাদপত্রও পালন করে ইতিবাচক ভূমিকা। মানুষ সচেতন হয় এবং এই জাতের ধান চাষে উৎসাহী হয়। কৃষির তথ্যকে ভালোভাবে বুঝে এভাবে প্রকাশের মাধ্যমে সাংবাদিকরাও পারে দেশের কৃষির উন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখতে।
দৈনিক পত্রিকার ভাষা-পর্যালোচনা
এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দৈনিক প্রথম আলো তার জন্মলগ্ন থেকেই এ দেশের সবচেয়ে বেশি গ্রাহ্য পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কেবল পাঠকপ্রিয়তা নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও প্রথম আলোর ভূমিকা আজ অনেক ক্ষেত্রেই পথিকৃতের। পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা পত্রিকা হিসেবে প্রথম আলো তার পাঠক বাড়ানোর চিন্তা ও উদ্যোগের পাশাপাশি আরও কিছু দায়িত্ব পালন করতে চায়। প্রচারসংখ্যা ধরে রাখা কিংবা বৃদ্ধি করার চেষ্টা প্রতিটি পত্রিকাই নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকে।
যেহেতু এই পত্রিকা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেহেতু এর প্রতি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম আলো পাঠকের সেই মনোভাবের কথা জানে। আর জানে বলেই, প্রথম আলো সেই প্রত্যাশা পূরণে উদ্যোগী হয়।
বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার বয়স দীর্ঘ হলেও এখনো একটি সর্বমান্য ভাষারীতি তৈরি হয়নি। সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়তো সম্ভবপরও নয়। কিন্তু নিজ নিজ কাজের সুবিধার্থে প্রতিটি পত্রিকায় এক ধরনের ভাষারীতি গড়ে ওঠে। লিখিত কিংবা অলিখিত ভাষারীতি প্রায় সকল পত্রিকাই অনুসরণ করে। ২০০০ সালে একটি দৈনিকের সম্পাদনা-বিভাগে কাজ করার সূত্রে একটি ভাষারীতি প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।
কিন্তু সেটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি। প্রথম আলো-ই প্রথম তাদের নিজস্ব ভাষারীতিকে গ্রন্থরূপ দিয়ে সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। নিজেদের প্রয়োজনে রচিত কিংবা মুদ্রিত হলেও এটি এখন সাধারণ পাঠক কিংবা লেখকদেরও প্রয়োজন মেটায়। যেহেতু প্রথম আলো এখন অনেক কিছুর আদর্শ হয়ে উঠেছে, তাই এক দশকের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তারা নিজেদের বদলে নিয়ে ক্রমাগত শুদ্ধতার দিকে যাত্রা শুরু করেছে। এই যাত্রা কেবল ভাষারীতি নিয়ে নয়, এই যাত্রা সাংবাদিকতার রীতি ও আচরণবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
পাঠক এখন প্রথম আলোর ভাষারীতি অনুসরণ করতে চায়। সাংবাদিকতার নবীস কর্মী কিংবা শিক্ষার্থীরা এখন প্রথম আলোর রিপোর্টিংয়ের ধরন বুঝতে চায়। তারা সম্পাদনার রীতিনীতি বুঝতে চায়। এই ক্ষেত্রে প্রথম আলো হতে পারে অনেকের কাছেই আদর্শ পত্রিকা। সেই কারণে নিয়মিত আধেয় পর্যালোচনা করে প্রথম আলো কতটা রীতিচ্যুত হচ্ছে কিংবা কতটা নতুন দিকের নির্দেশনা দিচ্ছে, তা অনুধাবনের চেষ্টা করা যেতে পারে।
প্রায় পক্ষকালের পত্রিকার আধেয় দেখে কিছুটা ধারণা অর্জনের চেষ্টা করা যাক-
প্রসঙ্গ শিরোনাম
এই পত্রিকায় যে ঘাটতিগুলো দেখা যায়, তার বেশিরভাগই শিরোনাম রচনার ক্ষেত্রে। সংবাদ শিরোনামের লক্ষ্য হচ্ছেÑ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা, সংবাদকে একনজরে/একবাব্যে পাঠকের কাছে তুলে ধরা এবং ব্যস্ত পাঠককে সংবাদ সম্পর্কে দ্রুত তথ্য দেওয়া। সংবাদের মূল কথাটি উদ্ধার করে যথাসম্ভব কম শব্দে শিরোনাম তৈরি করা হয়। এটি এত দ্রুত সম্পন্ন করতে হয় যে, ভুল থেকে যাওয়ার আশঙ্কা এড়ানো যায় না। এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, প্রথম আলোর সংবাদ-শিরোনাম অপেক্ষাকৃত বেশি আকর্ষণীয় হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে মূল সংবাদ থেকে বা মূল তথ্য থেকে বিচ্যুতিও ধরা পড়ে। উদারণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে-
প্রসঙ্গ সূচনা
রিপোর্টার যখন সব তথ্য হাতে নিয়ে বসেন, তখন শুরুতেই তাকে লিখতে হয় সংবাদ সূচনা বা ইন্ট্রো। সূচনায় ষড় ‘ক’ ব্যবহারের কথা আমরা জানি। এই ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করলে অনেক সাংবাদিকই রুষ্ট হন। সংবাদিকতা যেহেতু একটি শিল্প, তাই সকল ব্যাকরণ তার না মানলেও চলে। কিন্তু কাজের সুবিধার্থেই ব্যাকরণ আমরা তৈরি করে নিই। একটি ভালো সূচনায় অতিসংক্ষেপে মোটামুটি ছয়টি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ঘটনার প্রয়োজনে তিন-চারটি মৌলিক তথ্য দিয়েও ভালো সূচনা রচনা করা যায়। প্রথম আলোর প্রবণতা ফিচারধর্মী রিপোর্ট প্রকাশ করা। তাই সব সময় মৌলিক ছয়টি জিজ্ঞাসার জবাব সূচনায় দেওয়ার সুযোগ থাকে না। এই ব্যস্ততার যুগে গোটা রিপোর্ট সবাইকে পড়ানো যাবে না। মানুষের ব্যস্ততা যত বাড়বে, সূচনা লেখার প্রতি আমাদের তত বেশি মনোযোগী হতে হবে। প্রথম আলোতে সূচনা লেখা, সম্পাদনা কিংবা পুনর্লিখনের প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কয়েকদিনের ‘সূচনা’ পর্যবেক্ষণ করলে অনুধাবন করা যাবে যে, অনেক ক্ষেত্রে আমরা মূল তথ্য জানাতে ব্যর্থ হচ্ছি। উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হতে পারে-
সরল সংবাদ বিবরণী
প্রথম আলোতে সরল সংবাদ বিবরণীর চেয়ে বেশি থাকে ফিচারধর্মী প্রতিবেদন। ফিচারধর্মী প্রতিবেদনে রিপোর্টারের স্বাধীনতা থাকে তথ্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে। কিন্তু সরল সংবাদ বিবরণীর ক্ষেত্রে কিছু রীতি মান্য করা দরকার। কোনটি সরল সংবাদ আর কোনটি মানবিক আবেদনধর্মী সংবাদ তা নির্ধারণ না করেই বিবরণ লেখার চেষ্টা করা হয়।
আমরা দেখতে পাই, এই পত্রিকায় ফিচারধর্মী বিবরণীর আধিক্য রয়েছে। এটি যদি নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা পুনর্বিবেচনার সুযোগ খোঁজা দরকার। নমুনা হিসেবে বলা যায়, গত বছর ২৭ জানুয়ারির প্রথম আলোতে ‘কলাম ১’ বাদ দিলে সংবাদ রয়েছে ১০টি। এর মধ্যে ‘সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাটে বার্ড ফ্লু, চার হাজার মুরগি মারা গেছে’ এবং ‘২৭তম বিসিএসে বাদপড়া আরও ৬৫২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ’- এক-কলামের মর্যাদা পাওয়া এই দুটি সংবাদ বাদে বাকি আটটি সংবাদই ফিচারধর্মী। এই অনুপাত কমিয়ে আনা যেতে পারে। আর যে দুটিকে সরল সংবাদ বিবরণী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছি, তা-ও পুরোপুরি সরল হয়ে ওঠেনি। নমুনা হিসেবে ‘সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাটে বার্ড ফ্লু, চার হাজার মুরগি মারা গেছে’ সংবাদটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।
প্রসঙ্গ ভাষাগত সম্পাদনা
দৈনিক পত্রিকায় সাদামাটা সংবাদ কিংবা সরল সংবাদ বিবরণীতে ভাষায় অলঙ্কার প্রয়োগের চেয়ে শুদ্ধতা রক্ষাই জরুরি কাজ। কঠিন শব্দের কিংবা রূপকের আশ্রয় গ্রহণের চেয়ে সহজ শব্দ, সরল বাক্যই সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। প্রথম আলো প্রবর্তিত ভাষারীতি শব্দের যথাপ্রয়োগ নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু ভাষার পদবিন্যাস কিংবা বিশেষণ প্রয়োগের দক্ষতা সংশ্লিষ্ট সম্পাদককেই অর্জন করতে হয়। প্রথম আলো এ ব্যাপারে সচেতন। তারপরও প্রতিদিনই কিছু কিছু ভাষাগত দুর্বলতা পাঠকের চোখে পড়ে। যেমন-
আরও কিছু পর্যবেক্ষণ
ক্রীড়ার সংবাদগুলোর বেশিরভাগই ভাষার কারুকাজ। রচনা হিসেবে এগুলো উৎকৃষ্ট। যারা ক্রীড়ামোদী, যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বা অন্য কোনো মাধ্যমে ফলাফল জেনে গেছেন তাদের বিশ্লেষণাত্মক এই রচনাগুলো খুবই উপাদেয়। কিন্তু যারা মূল খবরটুকু সরাসরি জানতে চায়, তাদের জন্য এটি সুখপ্রদ নয় বলেই আমার ধারণা।
স্বাস্থ্যকুশল পৃষ্ঠার রচনাগুলো টেকনিক্যাল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বেশ কিছু রচনাপাঠে আমার মনে হয়েছে- এর পাঠক বুঝি চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মী। সাধারণ পাঠকের উপযোগী লেখার সংখ্যা বাড়ানো দরকার।
ঢাকায় থাকি পৃষ্ঠার সম্পাদনার ক্ষেত্রে অমনোযোগের ছাপ রয়েছে। ২৪ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রায় প্রতিটি প্রতিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়-
কিছু সুপারিশ
১. সাদামাটা সংবাদের ক্ষেত্রে সূচনায় ষড় ‘ক’ ব্যবহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার।
২. সূচনার সঙ্গে শিরোনামের সঙ্গতি বিধান করা দরকার।
৩. বিবরণীর শেষের দিক থেকে তথ্য এনে শিরোনাম করার প্রয়োজন দেখা গেলে রিপোর্টটি পুনর্লিখন করালে ভালো হয়।
৪. কপি সম্পাদনার সময়ে বাড়ানো-কমানোর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু রিপোর্ট এমন যে, একটানে কেটে ফেলা যায় না। তেমন রিপোর্ট ছোট করতে হলে পুনর্লিখনের মাধ্যমে করালে মূল তথ্য রক্ষা পেতে পারে।
৫. পুনর্লিখনের জন্য সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের চেয়ে ভিন্ন লোককে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।
৬. একাধিক অঞ্চলের সমধর্মী সংবাদ এক শিরোনামে প্রকাশ করার প্রয়োজন হলে, কেবল ইন্ট্রো লিখে আর উপশিরোনামে সংবাদগুলো জুড়ে দিলে ভুল থাকার আশঙ্কা থাকে। এগুলো পুনর্লিখন করাতে হবে।
৭. প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় ফিচারধর্মী প্রতিবেদনের সংখ্যা কমানো যেতে পারে।
৮. প্রতিটি বিভাগ বা পৃষ্ঠাকেন্দ্রিক সাপ্তাহিক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।
৯. ভাষারীতি সবাইকে জানানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
১০. কর্মীদের পাঠস্পৃহা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
১১. নিয়মিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যেতে পারে।
১২. কর্মীদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে।
১৩. দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।
লেখক : উপ-পরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
