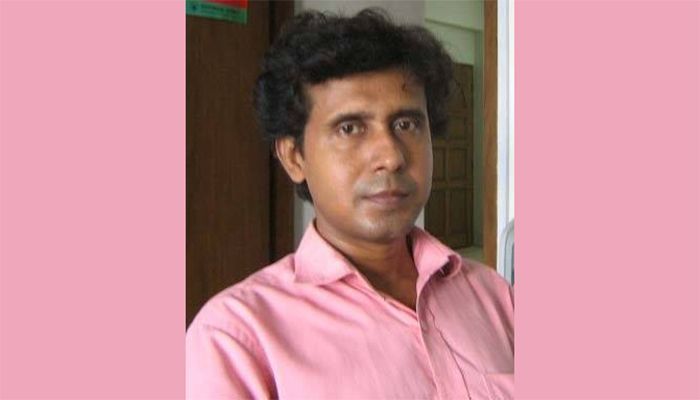
আলমগীর খান। ফাইল ছবি
পাঠ্যপুস্তক নিয়ে হৈচৈ বাংলাদেশে একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমাদের দেশে যে একটা জুতসই শিক্ষাব্যবস্থা চলমান দেশবাসীকে সেটা বোঝানোর জন্যই হয়তো আমাদের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কয় দিন পর পর দেশটাকে সরগরম রাখার একটা আয়োজন করেন।
এত দিন আমরা দেখেছি ১. ভুল তথ্য, বানান, বাক্য গঠন, ২. অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা, ৩. মুদ্রণ ত্রুটি, ৪. ছাপানোর নিম্নমান ইত্যাদি। এ বছর থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হলো লেখা চুরি, গুগল ট্রানস্লেটরের সাহায্যে বাঙালি ছেলেমেয়েকে উচিত শিক্ষা দেওয়া, বিজ্ঞানচর্চার নাম করে অদক্ষ উপস্থাপনা, দুর্বোধ্য আলোচনা ইত্যাদি।
এবার পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে দেশের মানুষ বলতে গেলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক পক্ষ উদ্বিগ্ন যে দেশে ছেলেমেয়েকে ধর্মবিমুখ করার চেষ্টা হচ্ছে। আরেক পক্ষ উদ্বিগ্ন, পাঠ্যপুস্তক ভুলে ভরা। কর্তৃপক্ষ ভুলভালের জন্য আংশিক দায় স্বীকার করেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদেরকে কোনোকালে খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ-কারণ লোম বাছতে কম্বল উজাড়!
বেশ কয়েক বছর ধরে বছরের প্রথম দিনই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। সারা বছর অজস্র খারাপ খবরের মাঝে এই একটি ভালো খবর দিয়ে বছর শুরু হয় বাংলাদেশে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাজটি ঠিকমতো হচ্ছে না। প্রথম দিকে বই উৎসবের কাজটি সরকার ভালোভাবে করলেও, দেখা যাচ্ছে এখন তা পারছে না।
অথচ একসময় এই বিরাট কাজটির দায়িত্ব সরকারের ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড’ একা কাঁধে তুলে নিত না।
মাধ্যমিকের বই ছাপানোর দায়িত্বটি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাসমূহ বহন করত, এখনো যেমন উচ্চ মাধ্যমিকের বই ছাপানো হয়। এনসিটিবি এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেও কাজটি আগের মতোই বেসরকারি প্রকাশনা ব্যবসায়ীরাই করেন। এনসিটিবি শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে। এতে ফল ভালো হয়েছে বলা যাচ্ছে না। অভিযোগ আছে, খারাপ সংস্থাগুলোকে ছাপানোর কাজ দেওয়ার, মুদ্রণের মান নিচে নেমে যাওয়ার ও নানারকম নয়ছয় করা নিয়ে।
প্রশ্ন হলো, প্রতিবছর সব বইই নতুন করে ছাপানো খুব কি জরুরি? একসময় স্কুলের ছেলেমেয়েরা দু-তিন বছর ধরে পুরনো বই ব্যবহার করত। বড় ভাইবোনের বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে পেত কিংবা কম দামে কারও কাছ থেকে কিনে নিত। যদি এই রেওয়াজ চালু থাকত তাহলে এখনকার চেয়ে হয়তো ১৫ থেকে ২০ কোটি বই কম ছাপলেও চলত। ৩৫ কোটি বই ছাপতে এখন প্রতিবছর সরকারের খরচ হয় প্রায় ১১০০ কোটি টাকা। পুরনো বই পুনরায় ব্যবহার করলে ছাপানোর এই খরচ হয়তো ৪ থেকে ৫শ কোটি টাকা কমে যেত। এই বিরাট অঙ্কের টাকা শিশুদের অপুষ্টি লাঘবে ব্যয় করা যেত। কিংবা প্রতিবছর সারা দেশের স্কুলগুলোয় চার/পাঁচশ কোটি টাকার নানারকম গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-বিজ্ঞানের বই কিনে দেওয়া যেত।
আবার প্রতিবছর ছেলেমেয়েদের হাতে সম্পূর্ণ নতুন বই তাদেরকে যে বার্তাটি দিচ্ছে তা একবার ভেবে দেখি। প্রতিবছর নতুন বই দেওয়ার ফলে এখন আর কোনো বই যতœ করে ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। বই পুরনো হলেও তার প্রতি ভালোবাসা থাকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।
এখন একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে পাঠ্যপুস্তকের বইয়ের মধ্যেই পৃথিবীর সব জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়ার। স্কুলকলেজ মূলত শিশুকিশোরদেরকে বইয়ের সমুদ্রে কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় তাই শেখায়। অতএব প্রতিবছর সবকিছু কয়েক পাতার পাঠ্যবইয়ের মাঝে ঠেসেঠুসে ঢুকানোর চেষ্টা না করলেই হয়। ছেলেমেয়েদের জ্ঞানতৃষ্ণাকে উসকে দেওয়া প্রয়োজন। স্কুলকলেজের ও পাড়ামহল্লার পাঠাগারে হাজার হাজার বই রাখুন, সেখানে তাদেরকে স্বাধীনভাবে পড়তে উৎসাহিত করুন।
আমরা এবারও লক্ষ করলে দেখব পাঠ্যবই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, নতুন তৈরি বইগুলো নিয়ে। প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির এসব বইয়ে শুরুতেই লেখা: ‘পরীক্ষামূলক সংস্করণ’। প্রশ্ন হচ্ছে, পরীক্ষামূলক সংস্করণ হুট করে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের হাতে তুলে দিতে হবে কেন? পরীক্ষামূলক ওষুধ তো হঠাৎ বাজারে ছাড়া হয় না, অল্প কিছু লোকের ওপর তাদের অনুমতি সাপেক্ষে প্রথমে পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা হয়। কেবল ইঁদুর ও গিনিপিগের ওপর পরীক্ষার ক্ষেত্রেই তাদের অনুমতি নিতে হয় না।
এই পরীক্ষামূলক সংস্করণসমূহ ২০২৩ সালে কি এনসিটিবির ওয়েবসাইটে রেখে সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণ করা যেত না? এই ব্যবস্থাটি শিক্ষা কর্তৃপক্ষের একটি গণতান্ত্রিক শক্তি ও পরমতের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করত। প্রাপ্ত মতামতসমূহ মুল্যায়নের পর চূড়ান্ত করে সেই বই পরের বছর শিক্ষার্থীদের হাতে দিলে ছিদ্রান্বেষীদের ও সরকার যাদেরকে গুজবরটনাকারী বলছে তাদের হাতে আক্রমণের কোনো অস্ত্রই থাকত না।
আমাদের দেশে হামেশা পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের বহর দেখে চোখে ভেসে ওঠে আমাদের আরেক কর্মযজ্ঞ-রাস্তা সংস্কার। একটি রাস্তা বানিয়ে কয়েক মাস যেতে না যেতেই আবার শুরু হয় খোঁড়াখুঁড়ি। কর্তৃপক্ষের লোকজন বলেন, আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলাতে পাঠ্যপুস্তক ঘন ঘন পরিবর্তন করতে হবে। কথা হচ্ছে, এই পরিবর্তনটা যেহেতু বিনে পয়সায় হয় না, তাদের কথায় কতটুকু আস্থা রাখা যায়?
সত্যি কি দুনিয়াটা মাসে মাসে পাল্টে যাচ্ছে? বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত¡সমূহ মাসে মাসে আবিষ্কার হয় না। মনে রাখা দরকার পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব শিক্ষককে সময় নিয়ে দক্ষ করে তুলতে হয়, শিক্ষার্থীর হাতে বই যাওয়ার আগেই। এ ক্ষেত্রে যে দায়সারা প্রশিক্ষণ হয় তা এতটা অপ্রতুল যে শিক্ষকগণই চোখে শর্ষে ফুল দেখতে থাকেন, শিক্ষার্থী দূরে থাকুক।
তাই বলে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এ বছর যারা যেভাবে যে যুক্তিতে যে দায়িত্বহীনতা ও অবহেলার সঙ্গে ও ন্যক্কারজনকভাবে এই পরিবর্তনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে ও জড়িত থেকে সামাজিকভাবে ও আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে তাদের কথায় ও যুক্তিতে ছিটেফোঁটাও সত্য নেই।
কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির সর্বাধিক বিতর্কিত দুটি বই প্রত্যাহার করেছে। মোট ৫৫ লাখ বই প্রত্যাহার করে নতুন করে ছাপতে সরকার গচ্চা দিচ্ছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। যে দেশে এখনো বহু ছেলেমেয়ে অভাবের কারণে বিদ্যালয়েই যেতে পারে না, সেই দেশে জনগণের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত এই টাকার শ্রাদ্ধ করার অধিকার কারও নেই।
আমরা দেখি পান থেকে চুন খসলেই হিরো আলমদেরকে পুলিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে পিঠ বাঁচাতে হয়, অথচ যারা পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এসব কাণ্ডকারখানা করেন তারা একজন প্রমিত বাংলায় দুঃখ প্রকাশ করলেই যেন সব সমাধান হয়ে যায়! প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের নামও জানা যায় না, তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরও সম্মানীর টাকাটা নিতে লজ্জাবোধ করেন না।
সম্পাদক
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি
