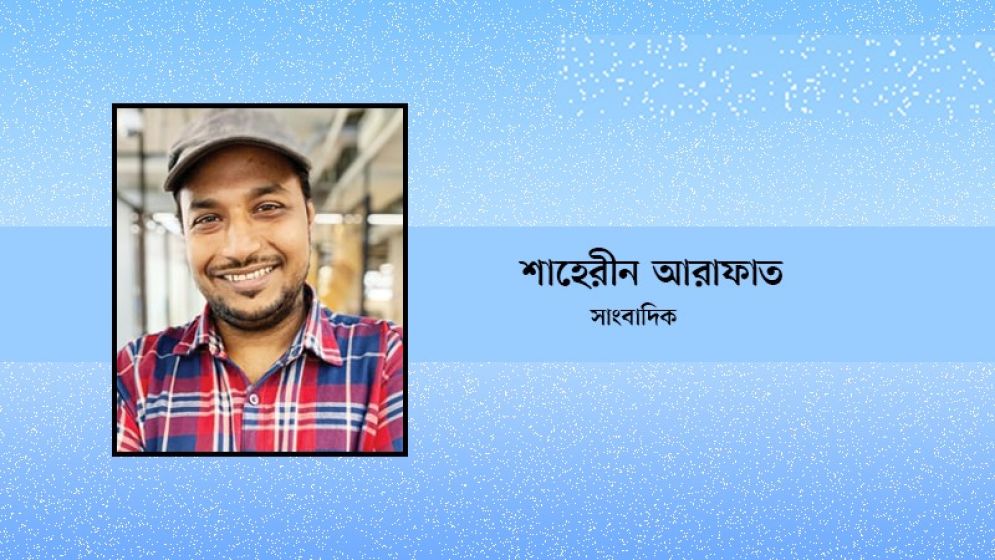
নেপালে বেকারত্ব, দুর্নীতি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় আঘাতের ক্ষোভ অবশেষে রাজপথে বিস্ফোরিত হয়েছে। ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি পদত্যাগ করেছেন। জ্বলেছে নেতাদের বাড়িঘর, সেনাবাহিনী উদ্ধার করেছে মন্ত্রীদের-এই দৃশ্য দক্ষিণ এশিয়ার নতুন এক রাজনৈতিক সংকটের প্রতিচ্ছবি। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক ছাত্রদের ওপর হওয়া দমন-পীড়নের নৈতিক দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেছিলেন। আরো কয়েকজন মন্ত্রী ও এমপি একই পথ বেছে নেন। রাজধানী কাঠমান্ডুসহ একাধিক শহরে সহিংসতা ছড়িয়েছে। বিক্ষোভকারীরা রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িঘর লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এই ক্ষোভ নেপালের গণতান্ত্রিক যাত্রার গভীর ফাটলগুলোকে স্পষ্ট করে তুলেছে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, এবার কোন পথে যাবে নেপাল!
দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একের পর এক গণ-অভ্যুত্থান দেখা গেছে। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার আরাগালয় (জনতার সংগ্রাম) আন্দোলন একজন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেয়। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান কয়েক দশকের ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান ঘটায়। পাকিস্তানে সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা এখনো চলছে। আর এবার গণযুদ্ধের দীর্ঘ সময় পর নেপাল আবারও অস্থিরতার পথে পা বাড়িয়েছে।
কাঠমান্ডুর রাস্তায় কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী শুধু টায়ার পোড়ানোর নয়; বরং সেই স্বপ্নগুলোরও, যেগুলো গণতন্ত্রের অভিপ্রায়ে জন্ম নিয়েছিল আর এখন ছাইয়ে পরিণত হচ্ছে। বারবার নেপাল দেখাচ্ছে, ক্ষমতা আর জনতার সম্পর্ক সংবিধান দিয়ে নয়; বরং রক্তপাত, অশ্রু আর ভাঙা কণ্ঠের মাপে নির্ধারিত হয়। তরাই থেকে পাহাড় পর্যন্ত-কোথাও পাথর ছোঁড়া হয়েছে, কোথাও গুলি, কোথাও আবার লাঠির আঘাত। এই বিক্ষোভ শুধু আজকের নয়; এটি সেই দীর্ঘ অসন্তোষের শৃঙ্খল, যা কখনো তরাই-মধেশ আন্দোলন, কখনো জাতিগত বৈষম্য আবার কখনো রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার রূপে সামনে এসেছে।
নেতৃত্বহীনতা এই ক্ষোভকে আরো গভীর করেছে। বিক্ষোভকারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ দাবি করেছে। এই আন্দোলন কেবল নীতির বিরোধিতা নয়; এটি যুবসমাজের সেই ন্যায়ের খোঁজের প্রতীক, যা বছরের পর বছর চাপা ছিল। কাঠমান্ডুর রাস্তায় ওঠা ধোঁয়া যেমন প্রতিরোধের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তেমনি পোশাকি গণতন্ত্রের ভেঙে পড়াও দৃশ্যমান করছে।
ক্ষোভের আগুন
৯ সেপ্টেম্বর পরিস্থিতি যখন চরমে পৌঁছে যায়, তখন প্রধানমন্ত্রী অলি পদত্যাগপত্র জমা দেন। তিনি লেখেন, ‘দেশে তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং সাংবিধানিক রাজনৈতিক সমাধান ও সমস্যা নিরসনের জন্য আমি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৭(১)(ধ) অনুযায়ী অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করছি।’ কিন্তু অলির পদত্যাগ আগুন নেভাতে পারেনি। কারফিউ ভেঙে বিক্ষোভকারীরা রাজধানীসহ অন্য শহরগুলোতে রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি ও দপ্তরে আগুন ধরিয়ে দেয়। অলির ভক্তপুরের ব্যক্তিগত বাসভবন পুড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাওডেলের বাড়িতে হামলা হয়। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক, নেপালি কংগ্রেস নেতা শেরবাহাদুর দেউবা এবং মাওবাদী পার্টির নেতা পুষ্পকমল দাহাল প্রচন্ডর বাড়িও হামলার শিকার হয়। এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী অর্জুন দেউবা রানার মালিকানাধীন একটি স্কুলও রক্ষা পায়নি।
পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয় যে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনীকে হেলিকপ্টারে করে মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করতে হয়েছে।
ঐতিহাসিক পটভূমি
নেপালের সাম্প্রতিক ইতিহাস সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ভরা-
১৯৯০ সালের গণ-আন্দোলন : রাজতন্ত্র দুর্বল হয় এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা ঘটে। তবে পরিবর্তন ছিল উপরিতলের, অভ্যন্তরীণ কোনো পরিবর্তন সেখানে হয়নি।
১৯৯৬-২০০৬ মাওবাদী বিদ্রোহ : এক দশকের গৃহযুদ্ধে প্রায় ১৭ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হন এবং বহু মানুষ নিখোঁজ হন। এটি রাজনৈতিক দৃশ্যপট পাল্টে দেয়।
২০০৬ সালের গণ-আন্দোলন : রাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর ঘটে নেপালের। তবু ক্ষমতা ও সমাজের দূরত্ব থেকে যায়।
২০১৫ সালের সংবিধান : প্রণয়ন করা হলেও মধেশি, থারু ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী এই সংবিধানকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দেয়। তাদের প্রতিবাদ পরিণত হয় ২০১৫-১৬ সালের নেপাল অবরোধে।
প্রতিটি বিদ্রোহই রাজতন্ত্র বা শাসক বদলেছে, কিন্তু জনগণের কাক্সিক্ষত ক্ষমতা তাদের হাতে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। এই ধারাবাহিক আন্দোলন ও বিদ্রোহ প্রমাণ করে, নেপালের রাষ্ট্রগঠন এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।
সাম্প্রতিক সহিংসতার সম্ভাব্য কারণ
নেপালের অস্থিরতা শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়; এটি সমাজ ও নাগরিক জীবনের গভীরে প্রভাব ফেলছে-
বারবার সরকার পরিবর্তন : গত ১৬ বছরে ১৩টি ভিন্ন সরকার ছিল ক্ষমতায়, যেগুলোর কোনোটি মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। অলি ও প্রচন্ডের ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি মানুষের আস্থা ভেঙে দিয়েছে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য বা অবকাঠামোতে কোনো কাজ হয়নি। এটাই যুবসমাজের ক্ষোভের মূল কারণ।
সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য : নেপালে বেকারত্বের হার ১৯.২ শতাংশ। সরকারি ও বেসরকারি খাতে সীমিত সুযোগ হতাশা বাড়িয়েছে। তার ওপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা মানুষের কণ্ঠরোধ করেছে, গুজব ছড়িয়েছে, ক্ষোভ আরো উসকে দিয়েছে।
অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা : রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিনিয়োগকারীর আস্থা ভেঙেছে, অর্থনীতি মন্থর হয়েছে। জাতিগত বৈষম্য, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও সামাজিক বৈষম্য নাগরিক জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করছে।
এসব কারণ মিলে সহিংসতার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। নেপালের এই অস্থিরতা কেবল দেশীয় নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় প্রভাব ফেলতে পারে।
রাস্তায় জনতা, দেওয়ালে দেওয়ালে ভাঙা প্রতিশ্রুতি
আজ নেপালের রাস্তায় যে ভিড় নেমেছে, তা সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, যা বারবার প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে-কখনো রাজতন্ত্র, কখনো গণতন্ত্র, কখনো প্রজাতন্ত্র ঘোষণার নামে। এই প্রতিবাদ এক প্রজন্মের হতাশা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। গত সপ্তাহে সরকার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইউটিউবসহ ২৬টি বড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করেছে। এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সরাসরি আঘাত হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীরা কাঠমান্ডুতে পার্লামেন্ট ভবন পর্যন্ত মিছিল করে; পুলিশ টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও লাঠিপেটা চালায়। এতে অন্তত ১৯ জন নিহত ও ১০০ জনের বেশি আহত হয়।
এই সহিংসতা আকস্মিক নয়; বরং পুরোনো ক্ষতগুলো নতুন করে ফেটে ওঠার মতো। মধেশি আন্দোলন, জাতিগত অসন্তোষ, দলগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গ-সব মিলেই আজ রাস্তায় প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশেষ করে তরাইয়ের জনকপুর, বিরগঞ্জ ও ধরন, সুদূর পশ্চিমে ধনগড়ি ও কাঠমান্ডু, পোখরা, ভরতপুর ও ভৈরহওয়ায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়সহ সরকারি দপ্তরে হামলা করে, টায়ার পোড়ায়।
ভারতের নীরবতা ও তার ছায়া
নেপাল-ভারতের সম্পর্ক শুধু কূটনীতির নয়, বরং ভূগোল, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বাঁধনে জড়ানো। খোলা সীমান্ত, লাখো নেপালি নাগরিকের উপস্থিতি, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-সব মিলিয়ে এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাই নেপালের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ভারতের নিরাপত্তার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল সীমিত। ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলন বা ২০০৬-এর রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে ভারত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, অনেক সময় প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতাও করেছিল। আজকের নীরবতা প্রমাণ করে, ভারত তার ঐতিহ্যগত ভূমিকা থেকে সরে গেছে।
নেপালে এখন ধারণা তৈরি হয়েছে যে ভারত শুধু কৌশলগত ও নিরাপত্তা স্বার্থেই সীমাবদ্ধ; যেখানে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে আগের চেয়ে অনেক সক্রিয়। অথচ প্রতিবেশীর দুঃখ-যন্ত্রণা বাতাসের মতো ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাই প্রশ্ন উঠছে-ভারত কি শুধু ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি প্রতিবেশীর রাজনীতিতে পদক্ষেপ নেবে? এমন পদক্ষেপ ভারতের জন্য হিতে বিপরীতও হতে পারে। শ্রীলঙ্কায় যেমনটা ঘটেছিল রাজীব গান্ধীর সময়কালে। তাই ভারত কৌশলগতভাবে প্রভাব রাখতে চাইবে।
গণতন্ত্রের পথ কতদূর
নেপালের অস্থিরতা কেবল তার ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। হিমালয়ের ঢাল থেকে ওঠা প্রতিটি ঢেউ ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রভাব ফেলে। যদি নেপালের সংকট আরো গভীর হয়, তবে চীনের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে, যা ভারতের জন্য দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।
দক্ষিণ এশিয়া আগেই অস্থিরতায় ভুগছে। পাকিস্তান রাজনৈতিক সংকট ও সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত, শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়াতে লড়ছে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের প্রশ্ন উঠছে। এর মধ্যে নেপালের অনিশ্চয়তা আঞ্চলিক ভারসাম্যকে আরো দুর্বল করবে। এটি স্পষ্ট করে যে, দক্ষিণ এশিয়ার শান্তির মানচিত্র ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। প্রতিটি দেশই নিজের সংকটে নিমগ্ন; কিন্তু প্রতিবেশীর বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেওয়া বা যৌথ সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।
সরকারি দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক সংকটের ফলে জনগণের মধ্যকার ক্ষোভই আন্দোলনকে শক্তি দিয়েছে। যেখানে শহুরে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। এর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারার সংশ্লেষ রয়েছে। এ বছরের শুরু থেকেই হিন্দু রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনর্বহালের আন্দোলন চলছিল। মধেশি অঞ্চলে ওই আন্দোলন গতি পায়। বর্তমান আন্দোলনে তাদেরও সোচ্চার অংশগ্রহণ ছিল। তবে তরুণদের এ আন্দোলনে রাজতন্ত্রপন্থিদের অবস্থান কতটা শক্তিশালী তা এখনো স্পষ্ট নয়।
নেপালের অবস্থা বাংলাদেশ থেকে অনেকটা ভিন্ন। সামাজিক বিভাজন অনেক বেশি। শহর আর প্রান্ত বা পাহাড়ি এলাকার মধ্যে শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক নয়; সাংস্কৃতিক ও চিন্তার পার্থক্যও অনেক প্রকট। দেশটির শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে বুর্জোয়া নাগরিক মানসিকতা আছে। বিপরীতে পাহাড়ি এলাকায় বৈষম্য অনেক বেশি; সেখানে এখনো মাওবাদীদের শক্ত সমর্থন টিকে আছে। ওই সব স্থানে রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন করা মোটেও সহজ হবে না। এক কথায়, নেপালের সমীকরণ সরল-সোজা নয়; বেশ জটিল। তবে এই সংকটের মূলে রয়েছে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে মাওবাদীদের ঐতিহাসিক ভুল। ২০০৬ সালে মাওবাদী আন্দোলন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও রাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে ভারতের মধ্যস্ততায় আত্মসমর্পণ করে এবং জাতিরাষ্ট্র গঠনের দিকে এগোয় নেপাল। আর এখানেই মূল সংকট নিহিত। এক কালের মাওবাদী বিপ্লবী পুষ্পকমল দাহাল প্রচন্ড, বাবুরাম ভট্টরাইদের আত্মসমর্পণে গণতন্ত্রের নামে পোশাকি নির্বাচনবাদী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। জনগণকে গাঠনিক ক্ষমতা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। জনগণের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়।
অতএব, নেপালের সংকট কেবল অলির পতন নয়, রাষ্ট্রগঠনের অসম্পূর্ণতার প্রকাশ। এবারও যদি সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে না ফেরে, তবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। আর যদি ফেরে, তবে হিমালয়ের এই দেশ দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন গণতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।
