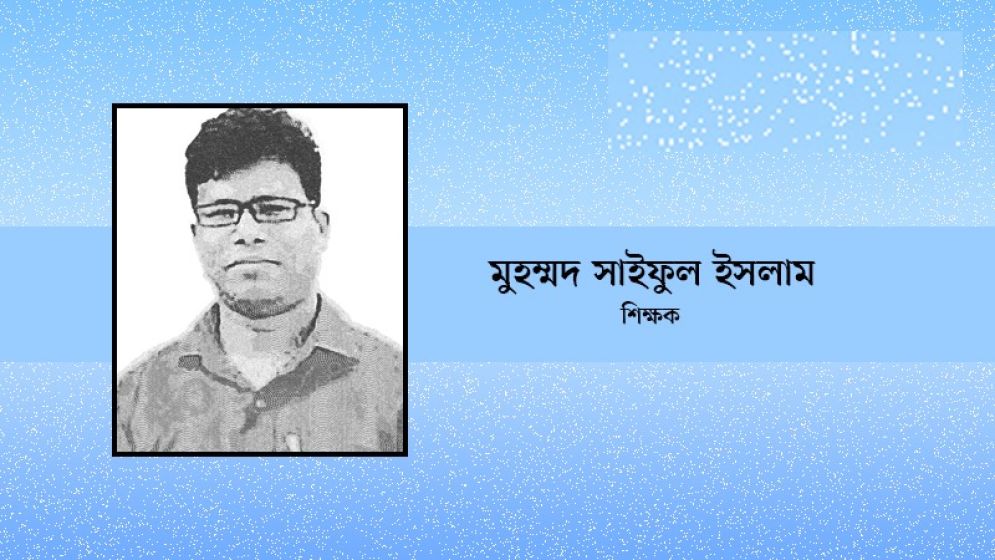
সময় ও বাস্তবতা বড় ভয়ংকর। হু হু করে আমাদের আয়ুর তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে, টেরও পাচ্ছি না। অথচ আমাদের মধ্যে থাকা সবচেয়ে মূল্যবান যে ‘জীবন’-বস্তুটা কী, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা আজ নেই বললেই চলে! কোনো একটা সত্য বা বস্তু সম্পর্কে জানতে পারলে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জন্মে। এই ভালোবাসা আমাদের কর্মে ও চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। জীবনের নাগাল এই পথে মেলে, আধুনিক মননের এই মহাশিক্ষা। কিন্তু কোনো সত্য কিংবা বস্তু সম্পর্কে আমাদের মনে যদি কোনো কৌতূহল ও আগ্রহ তৈরি না হয়, তবে তার সম্পর্কে আমাদের ভালোবাসা তৈরি হবে কী করে? কেন এই জিজ্ঞাসা মনে এলো, বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক, দু-চার বাক্যে।
প্রকৃতিগতভাবে, স্বাভাবিক নিয়মে আমরা প্রত্যেক মানুষ একটা আয়ুর শক্তি নিয়ে জন্ম নিই। পরে এই দুঃসহ ও নরকতুল্য পৃথিবীতে বিপুল কষ্টে, অশেষ দুঃখের ভেতর দিয়ে, বহু বেদনায় কিছু শিক্ষা অর্জন করি। অথচ এই অর্জিত শিক্ষার আসল অর্থটি বোঝা হয়ে ওঠে না কখনো! তার আগেই প্রত্যক্ষ পরিবেশের প্রভাবে নানা বিচিত্র সমস্যা ও সংকটে নিজেকে আমরা জড়িয়ে ফেলি। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝে নেওয়া ভালো কথাটা।
আজ আমাদের চারপাশে চলছে হিংসা ও ঘৃণা, ভয় ও বিভীষিকার তাণ্ডব! একে অপরের মধ্যে চলছে এমন মতপার্থক্য, যা পাশবিকতার স্তরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি সমাজ কখন নিচে নেমে যায়? যখন দেখা যায়, সেখানে পরস্পরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গালি উৎপন্ন হয়, সব স্তরে সে গালি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পণ্ডিত-মূর্খে ভেদ থাকে না। এই আবহের মধ্যে কেউ কি এই ‘জীবন’ নামের কোনো বস্তুর কথা কল্পনা করতে পারেন? পারে না যে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন! অথচ এর অভাব দেখা দিলে ব্যক্তি থেকে বিশ্বের ক্ষতি হয় অপূরণীয়! পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা হয়ে ওঠে সংকটে ভয়ানক!
দুই
এই যে ‘জীবন’-এর অর্থের কথা এমন সংকটের দিনে কেন তোলা হচ্ছে? কারণ এই মৌল সত্যের বাইরে মানবেতিহাস বলে কিছু নেই। ঠিক এই জন্য আমাদের এক প্রভাবশালী তীক্ষè বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক ১৪০ বছর আগে এ নিয়ে এক ভয়ংকর প্রশ্ন তুলেছিলেন! বলেছিলেন, ‘এ জীবন লইয়া কি করিব? কি করিতে হয়?’ এ জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার চেষ্টায় তিনি নিজের কথায় বলছেন, ‘সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছে, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশি-বিদেশি শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।’ এই ‘পরিশ্রম’ করে তিনি যা পেয়েছিলেন, তার ফলের কথায় তিনি যা বলেছেন, তা আমাদের আধুনিক মন গ্রহণ না করতে পারে, কিন্তু তিনি যে ‘জীবন’-এর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, তা এক কথায় অভাবিত!
অথচ ‘জীবন’ বস্তুটি বোঝার জন্যে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা ঠিক সেই বস্তুটি আমাদের চোখের আড়াল করে রেখেছে, অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। পরিবর্তে যে বস্তু আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, প্রবল করে তোলে আমাদের বাঁচবার বাসনার চেয়ে মৃত্যুর আকাক্সক্ষাকে, মধুলোভী মৌমাছির মতো আমরা সেদিকে পুরো শক্তি ব্যয় করছি! ওই যে আমরা শুনে নিলাম আমাদের দুর্দান্ত এক মহৎ প্রতিভার কাছে, যিনি বলছেন, প্রাণপাত পরিশ্রম করে সত্য নিরূপণ করতে হয় এবং যাতে দরকার হয় ‘অধ্যয়ন’-কথাটির অর্থ কী? চোখে আলোহীন মানুষের খুব বিরাট সংখ্যাও চক্ষুষ্মান ধূর্ত মানুষের স্বল্প সংখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না দীর্ঘকাল। পৃথিবীর সব দেশেই এই স্বল্প-সংখ্যা বিপুল সংখ্যার জনসাধারণের মৌল স্বার্থের বিরুদ্ধে ‘ন্যারেটিভ’ উপস্থাপন করে চলে! অথচ ‘জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা চোখে আলো দেয়।’ সে জন্যে মানুষের সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ‘সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশি-বিদেশি শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন’ করা দরকার নয় কেবল, জরুরি। জনসাধারণের এই যে বিরাট সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, তার পরম দুর্ভাগ্য যে, সভ্যতার বিপুল ঐশ্বর্য ও অমৃতময় ফল থেকেও সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কাজেই এই জনসাধারণকে যে বোঝায়, একমাত্র দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা তার লক্ষ্য; বাইরে সে কল্যাণকামী হলেও ভেতরে সে প্রবঞ্চক ও প্রতারক। কেন? উত্তর এরই মধ্যে দেওয়া হয়েছে। মানুষের চোখে দৃষ্টি নামের একটি মহাশক্তির দরজা খুলে যাক, এটা প্রবঞ্চক চায় না!
তিন
এই প্রতারণা আছে আমাদের তথাকথিত শিক্ষার মধ্যেও, অবশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, ‘আধুনিক শিক্ষা প্রণালির দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সবাইকে এক এক, কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব হইতে হইবে-সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভালো করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সব স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথচ যে সৌন্দর্য দত্তপ্রাণ, সর্ব সৌন্দর্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ, সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন।’
কেন এমনটা হয়, তার অন্য একটি গুরুতর কারণও আছে আমাদের শিক্ষার মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, শিক্ষকদের নির্দেশ : ‘মুখস্থ করো, মনে রাখো, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষè হইল, কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্তারূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলো বুড়ো খোকার মতো কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয় কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সব শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়-বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, তাহার পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।’
আমাদের স্বাধীনতার পরে, অর্ধশতাব্দী চলে গেলেও যে-জাতি শতকরা দুজন শিক্ষার্থীকেও বুদ্ধির ভাষা কী, যুক্তির ভাষা কেমন, চিন্তার ভাষা কী রূপ হয়, বিচার ও বিশ্লেষণের ভাষা বলতে কী বোঝায়, যুক্তি ও নৈতিকতার নিয়ম কেন মান্য হওয়া দরকার তা শেখাতে পারেনি। কাজেই এই জাতির ভেতর শত শত ভিন্ন গুণ থাকলেও তার প্রশস্ত বুদ্ধির কথা স্বীকার করা অসম্ভব।
কেন এই ‘ক্ষীণ দুর্বলতা’? আমরা সবাই জানি, পাঠ্যবই কেউ পড়ে না, মুখস্থ করে। সত্য যে, আমরা এ কথা সবাই জানি, মুখস্থবিদ্যার উদ্দেশ্য পরীক্ষার খাতায় উগলে দেওয়া, পাস করা যার লক্ষ্য। অতএব ছাত্রত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্যা মন থেকে মুছে যায়। যেমন-ভাঙা তেলের শিশি থেকে গড়িয়ে পড়া দু-একটা ফোঁটা তেল দিয়ে রান্নার কাজ সম্পন্ন করা যায় না, পরীক্ষার্থীর ওই মুখস্থ বিদ্যার তলায় পড়ে থাকা ‘ক-অক্ষর গো-মাংস’ দিয়ে তেমনি বিচারের ভাষা অর্জিত হয় না! যুক্তি ও নৈতিকতার নিয়ম বহু দূরস্ত! যে জ্ঞান স্বীকরণ কিংবা মনের ভালোবাসার সঙ্গে মিশে যায় না, তেমন জ্ঞান নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি গল্প বলেছেন। তার গল্পটি শুনে নেওয়ার দরকার আছে : একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাদু বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, ‘সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই, আঁটি খাইতে হয়।’ তার পর আঁব আসিল। সাহেব মালীর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন।
দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, ‘সাহেব, কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।’ সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষে ওল আসিল। সাহেব তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপূর্বক আধা কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মতো ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারীর ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার জায়গায় আঁটি, আঁটির জায়গায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র। এই ‘জীবন লইয়া কি করিব?’
চার
আমাদের বিখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ‘জীবন’ নিয়ে কী ভেবেছিলেন, এ প্রসঙ্গে খুব উল্লেখযোগ্য। তার ভাবনাটি তিনি কোনো লেখায় বলেছিলেন, তা নয়। কিন্তু তন্নিষ্ঠ জীবনের কথা বয়ে চলে লোকজ ধারার প্রবহমানতার ভেতর দিয়ে, অনেক সময় গল্পে রূপ নিয়ে। গল্পটি আমাদের শুনিয়েছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তার ‘নিষ্ফলা মাঠের কৃষক’ বইয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হওয়ার সুবাদে, তার স্মৃতিচারণায়।
‘জীবন’ কী-এ জিজ্ঞাসায় শহীদুল্লাহ বলেন, ‘আমরা যে প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা করে ঘুমাই, জীবনে এর মূল্য কী? তার মানে, প্রতিদিনের পুরো চব্বিশ ঘণ্টা থেকে চার ভাগের একভাগ সময় আমাদের জীবন থেকে চলে গেল। এর অর্থ এই যে, আমরা যদি গড়ে ষাট বছর বেঁচে থাকি, তবে আমরা বেঁচে থাকলাম আসলে চার ভাগের তিন ভাগ, অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ বছর। কর্ম ও চিন্তাহীনতায় অথবা অন্য স্বপ্ন বিলাসিতায় যদি দিনের আরো ছয় ঘণ্টা অপচয় হয়, তবে আমরা বেঁচে গেলাম মাত্র তিরিশ বছর। অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ও বিষোদ্গারে, অন্যের ওপর নিন্দা ও মিথ্যা প্রচারে যদি আরো ছয় ঘণ্টা ব্যয় করি, তবে আমরা বাঁচলাম মাত্র ১৫ বছর। পৃথিবীতে ষাট বছরের স্বাভাবিক শক্তির আয়ু পেয়ে এবং অর্জিত বিদ্যার আলো নিয়েও যে-আমি এভাবে জীবনের সত্য নিজের হাতে ধূলিস্মাৎ করলাম-ডক্টর শহীদুল্লাহ মনে করতেন, এটা এক ধরনের আত্মহত্যা! শিউরে ওঠার মতো জীবনের এই হিসাব! এ এক পরম দৃষ্টি! জীবন আসলে একটা গাণিতিক ব্যবস্থাপত্র। যেন গণিতের বাইরে জীবন নেই! কেন?
মৃত্যুটা জীবন নয়। আত্মকৃত কর্ম ও চিন্তাই জীবন, যেখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তা। এর শুরু ও শেষ কোথায়? বাল্য-কৈশোর কিংবা বার্ধক্যের কাছে কেউ কিছু দাবি করে না। ব্যক্তি নিজেও না। তার মানে, এই দুইয়ের মধ্যে জীবন খুঁজে নেয় তার আসল ঐশ্বর্য। এর দাবি সকলের কাছে। এখানেও গণিতের মতো সুনির্দিষ্ট সূত্রে ফলাফলের দিকে এগিয়ে নিতে হয় জীবনকে। বিচিত্রের মধ্য থেকে সত্তার আসল রূপ বেছে নিয়ে তার তাৎপর্য খুঁজে বের করবার সত্যের নামই জীবন। লেখাপড়া শিখে কেউ যদি এর মূল্য বোঝেন, তবে সে জীবনই সত্য ও যথার্থ। না বুঝলে আমরা কেবল মৃত্যুর জন্যে জন্ম নিই-এখানে জীবন নেই। আছে কেবল জন্ম আর মৃত্যু। এখানে অন্য জীবের সঙ্গে আমরা একই সমতলীয়, একই গোত্রভুক্ত। আসল জীবন থেকে হয়তো আমাদের এই শিক্ষাই পেয়ে থাকি, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা শহীদুল্লাহ এর দৃষ্টান্ত।
