বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি : রাজনৈতিক সম্পর্ক কিংবা টানাপোড়েন
কবীর আলমগীর
প্রকাশ: ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০৫
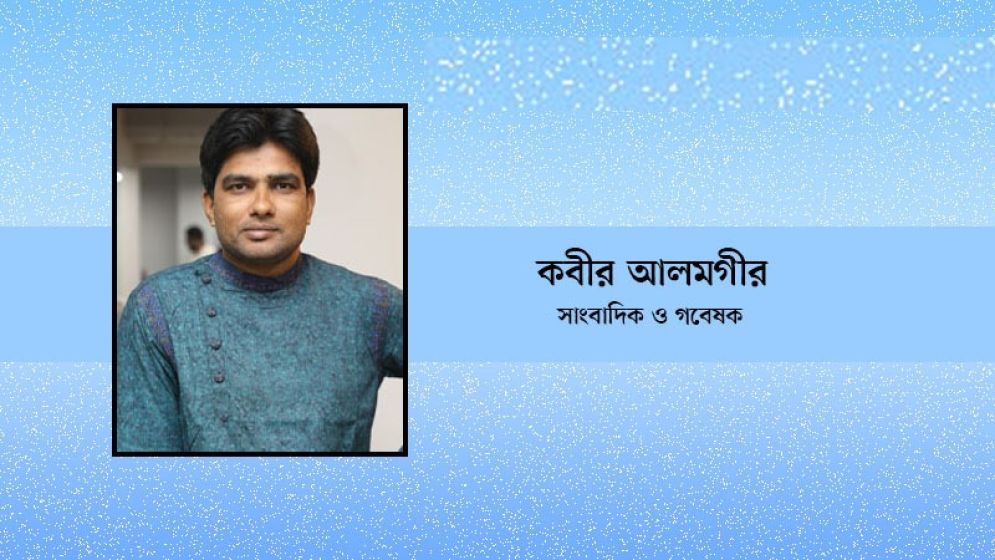
জুলাই সনদের বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, আগামী সংসদ নির্বাচন পুরোনো পদ্ধতিতে নাকি সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে হবে তা নিয়ে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপির রাজনৈতিক তর্ক ক্রমে জোরালো হচ্ছে। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই তিন দলের সম্পর্ক কিংবা টানাপোড়েন কতদূর গিয়ে দাঁড়াবে তা এক জটিল প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।
২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান শুধু একটি শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনই আনেনি, বরং দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জনগণের প্রত্যাশা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, আমাদের মূলধারার রাজনীতি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে গভীর আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। একটি সুস্থ, কার্যকর এবং জনমুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য কিছু মৌলিক নীতির ওপর গুরুত্বারোপ করা অপরিহার্য।
দেশের রাজনীতিতে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির মধ্যকার সম্পর্ক এক নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। তাদের মধ্যকার সম্পর্কের টানাপোড়েন বা গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ভবিষ্যৎ কৌশলগত দিকগুলো বিবেচনায় নেওয়া দরকার।
ঐতিহাসিকভাবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে একটি কৌশলগত জোটের সম্পর্ক ছিল, বিশেষত নব্বইয়ের দশকের পর থেকে। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় এই জোট ক্ষমতার অংশীদারির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। জামায়াতের যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এবং বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে বিএনপিকে প্রায়ই জামায়াতকে সঙ্গে রাখার বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রকাশ্যে বিএনপি জামায়াত থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলেও মাঠ পর্যায়ের আন্দোলনে বা বৃহত্তর সরকারবিরোধী কার্যক্রমে তাদের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া বা সমন্বয় দেখা গেছে। আর এনসিপির মতো নতুন দল রাজনৈতিক শক্তি অর্জন এবং নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে।
বিএনপি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল হিসেবে, স্বাভাবিকভাবেই এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব এবং সফলতার দাবি করে আসছে। অন্যদিকে জামায়াত-এনসিপি ও অন্যান্য দলগুলোও নিজের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে, যা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের চাপা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, যদি একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় বা একটি নতুন নির্বাচনের দিকে দেশ এগোয়, তখন ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং ভবিষ্যৎ জোট গঠনের সমীকরণ অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠবে। বিএনপি হয়তো জামায়াতকে সরাসরি জোটে অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করতে পারে, বিশেষত যদি দেশের ভেতর এবং আন্তর্জাতিক মহলে জামায়াতবিরোধী মনোভাব তীব্র থাকে। সে ক্ষেত্রে জামায়াত নিজস্ব শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করতে পারে। এনসিপিও মূল দলগুলোর সঙ্গে দরকষাকষি করতে চাইবে।
তৃতীয়ত, দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শিক এবং কৌশলগত ভিন্নতা নতুন করে সামনে আসতে পারে। যদিও বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে কিছু অভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্য আছে, তবুও তাদের মতাদর্শিক ভিত্তি সম্পূর্ণ এক নয়। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হলে জামায়াত তাদের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এজেন্ডাগুলো আরো জোরালোভাবে তুলে ধরতে পারে। এটি বিএনপির সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদী অংশের জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে। এনসিপির মতো দলগুলোও তাদের নিজস্ব দাবিদাওয়া বা এজেন্ডা নিয়ে আসবে, যা মূল দলগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের জটিলতাকে আরো বাড়াবে।
গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নতুন জোট বা মেরুকরণের সম্ভাবনা থাকে। যদি বিএনপি জামায়াতকে পাশে রাখতে না চায় বা রাখতে না পারে, তাহলে জামায়াত অন্যান্য সমমনা ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে একটি নতুন জোট গঠন করতে পারে, যা তাদের রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। একইভাবে এনসিপিও তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে এবং প্রভাব বিস্তারের জন্য অন্য কোনো বড় দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে পারে কিংবা ৩০০ আসনেই একক প্রার্থী দেওয়ার ঝুঁকি নেবে, যা হবে এনসিপির জন্য একটি টেস্ট কেস। বুলেট আর বারুদের সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ প্রজন্ম যে সাহস দেখিয়েছিল, আগামীর রাজনীতিতেও সেই সাহসের ধারাবাহিকতা তারা দেখাবে।
এখন প্রশ্ন হলো, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী বাস্তবতায় আমরা কেমন রাজনীতি চাই। বিগত বছরগুলোতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ এবং জবাবদিহির অভাব রাজনীতিতে গভীর সংকট তৈরি করেছিল। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান জনগণের এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। তাই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সব স্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত এবং প্রতিটি কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। সংসদকে কার্যকর বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে, যেখানে বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনা এবং সরকারের জবাবদিহিতা থাকবে।
আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়, এই নীতি প্রতিষ্ঠা না হলে সুশাসন সম্ভব নয়। বিচার বিভাগকে সব ধরনের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে এবং বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা ও সততাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থা এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যেন তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং আইনের প্রয়োগ সব নাগরিকের জন্য সমান হয়। আমাদের এই মুহূর্তে দরকার সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির চর্চা করা। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে সব দল ও মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শত্রু হিসেবে না দেখে দেশের উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ ও আলোচনার সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, নারী ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলাও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির অংশ।
ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। এই সময়ে ধনী-গরিবের বৈষম্য ক্রমে বাড়ছে, যা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে। নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে, যা আয়বৈষম্য কমিয়ে আনে এবং সবার জন্য সমান অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করে। কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের উন্নয়নে সুষম নীতি গ্রহণ করতে হবে, যেন দেশের সব অঞ্চলের মানুষ উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে গুরুত্ব দিতে হবে।
২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের অগ্রভাবে ছিল তরুণরা। সুতরাং রাজনীতি সচেতন এই তরুণদের উপেক্ষা না করে রাজনীতিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের মেধা, শক্তি ও স্বপ্নকে কাজে লাগিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা এবং তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। রাজনীতিতে তরুণদের আকৃষ্ট করতে হবে এবং তাদের জন্য নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরি করতে হবে। প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন তরুণদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো উচিত।
মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দলের নেতৃত্ব নির্বাচন, নীতিনির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবারতন্ত্র ও ব্যক্তি পূজার পরিবর্তে মেধা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।
পরিশেষে বলা যায়, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমাদের মূলধারার রাজনীতিকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। জবাবদিহি, আইনের শাসন, সহনশীলতা, অর্থনৈতিক সমতা, তরুণদের অংশগ্রহণ, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি-এসবের বিনিময়ে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণ করা সম্ভব। আমরা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দেশ চাই, যেখানে ফ্যাসিবাদ ফিরবে না। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই যেখানে আর কোনো মায়ের বুক খালি হবে না।
