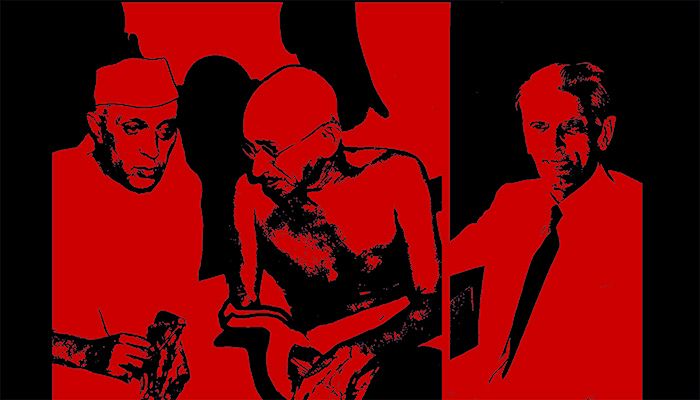
প্রতীকী ছবি
দ্বিজাতি তত্ত্ব ভারত ভাগের ক্ষেত্রে একটি প্রধান আলোচনার বিষয়। জিন্নাহকে এই দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভাবক বলা হয়। বহু বছর ধরে এই কথা ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করেছেন। ইতিহাস লেখকদের অনেকে কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে ভারত ভাগের সব দায় জিন্নাহর কাঁধে চাপিয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস গ্রন্থে বর্তমানেও তাই রয়েছে। পরবর্তীতে বহু ইতিহাসবিদ সত্যানুন্ধান না করে পূর্বের ইতিহাসকে মান্য করে, বারবার পুরনো কথাই বলে গেছেন। জিন্নাহ সেখানে ভারত ভাগের হোতা আর গান্ধী হলেন গণসংগ্রামী। কংগ্রেসের গণসংগ্রামের ভেতর দিয়ে ভারত স্বাধীন হয়েছে। কংগ্রেস হলো ধর্ম নিরপেক্ষ দল। জিন্নাহ সেখানে একজন কট্টর মুসলিম নেতা। জিন্নাহ যে জীবনের প্রথম পনেরো বছর কংগ্রেসের রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন, সে কথাটাও তাদের অনেকের ইতিহাসে উল্লিখিত নয়। জিন্নাহ যতদিন কংগ্রেসে ছিলেন, সেটি ধর্মনিরপেক্ষ দলই ছিল। কংগ্রেস গান্ধীর দখলে যাবার পর সেটি আর ধর্মনিরপেক্ষ থাকেনি। গান্ধীর ডাকা কংগ্রেসের আন্দোলনে ভারত স্বাধীন হয়নি।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি পরবর্তীকালে ভারত ভ্রমণে এসে কলকাতা রাজভবনে ছিলেন। রাজ্য পালের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার পেছনে গান্ধীর আন্দোলনের খুব সামান্যই ভূমিকা ছিল। বরং সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাবে ভারতে সামরিক বাহিনীর মধ্যে যেসব বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল, ব্রিটিশ সরকার তারপর আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করে ভারত শাসন করতে ভরসা পায়নি। ব্রিটিশ শক্তির ভারত ছেড়ে চলে যাবার সেটা ছিল মূল কারণ।(১) প্রধান কথাটি হলো দ্বিজাতি তত্ত্ব দিয়ে ভারত ভাগ হয়নি। জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভাবক নন। বরং জিন্নাহ সর্বদা চেয়েছিলেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য। তিনি সর্বদা বলতেন, হিন্দু মুসলমান যদি একসঙ্গে লড়তে না পারে ব্রিটিশ শক্তিকে দুর্বল করা যাবে না। তিনি ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মনেপ্রাণে এটিই বিশ্বাস করতেন।
জিন্নাহ যখন কংগ্রেসে ছিলেন তখনো এবং মুসলিম লীগের সভাপতি হবার পরও তিনি চেয়েছিলেন পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী হিসেবে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করতে। তিনি ইসলাম ধর্ম নিয়ে কখনো কথা বলেননি। নিজে ধর্মকর্ম করতেন না। মদ্যপান করতেন, শূকরের মাংস খেতেন। বরং গান্ধী গীতার উদাহরণ দিতেন, রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন কংগ্রেসের জনসভায় আর সর্বদাই গোরক্ষা আন্দোলন করার কথা বলে গেছেন। ভারতবর্ষে আজও গোরক্ষার নামে বছরের পর বছর ধরে দাঙ্গা লেগে আছে। সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায়, ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সতেরো বছরের ভারতে দাঙ্গার সংখ্যা পাঁচ হাজার চারশ’ একান্নটা।(২) জিন্নাহ বা মুসলিম লীগ যখন ভারত শাসন করছে না, তখনকার ঘটনা এটি। ভারত ভাগ হয়ে যাবার পর জিন্নাহ মুক্ত ভারতে তাহলে এত বেশি দাঙ্গা হবার কারণ কী? দাঙ্গার প্রধান একটি কারণ গো-হত্যা। গান্ধীর কট্টর ধর্মীয় উদ্যোগ হিসেবে গোরক্ষা কর্মসূচি ভারতে এখন ঘনঘন দাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই গান্ধীকে ভারতের রাজনীতিতে বিরাট ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখা হয়। তিনি যদি সত্যিই ভবিষ্যৎ ভারতের সর্বসাধারণের মঙ্গলের কথা ভাবতে পারতেন, তাহলে গোরক্ষা কর্মসূচি পরিহার করতেন।
জিন্নাহ ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের পক্ষে দীর্ঘকাল কথা বলেছেন। সব ঐক্যের জন্য কিছু শর্ত থাকে। মুসলিম লীগের দাবি ছিল সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণ আর ভারতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধান। মুসলিম লীগ সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থরক্ষাকারী দল ছিল। সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার দাবি কখনো অপরাধ হিসেবে বিবেচনা হতে পারে না; কিন্তু গান্ধী আর নেহরু বললেন, চাকরি-বাকরি আর অন্যান্য সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে সবাইকে পদ লাভ করতে হবে। পশ্চাদপদ মুসলমানের জন্য আসন সংরক্ষণ তারা মানতে রাজি ছিলেন না। চিত্তরঞ্জন দাশ কিন্তু বাংলা প্রদেশে চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ মুসলমানদের আসন সংরক্ষণ করার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখেন যা গান্ধী পছন্দ করেননি। কংগ্রেস এসময় মুসলিম লীগকে দেওয়া নানা প্রতিশ্রুতি বারবার ভঙ্গ করে। গান্ধীবাদী শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা যশোবন্ত সিংহ, বাম রাজনীতিক সুনীতি কুমার ঘোষ, আইনজ্ঞ বিমলানন্দ শাসমল, ইতিহাস গবেষক মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বইগুলো পাঠ করলে তা জানা যাবে। জিন্নাহ যখন মুসলিম লীগের দায়িত্ব নিয়ে সংখ্যালঘু এবং পশ্চাদপদ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার কথা বললেন, তখন তাকে সাম্প্রদায়িক বলা হলো। মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে চিহ্নিত করা হলো।
বর্তমান সময়ে বা বর্তমান বিশ্বে সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষা করাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয় আর সেটিকে ইতিবাচক আন্দোলন হিসেবে দেখা হয়। কংগ্রেস কিন্তু সেদিন জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের ভূমিকাকে সেভাবে বিচার করেনি। জিন্নাহকে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে দিয়েছিল। ভিন্ন দিকে আম্বেদকর যখন দলিত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেছেন, তখন তাকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়নি। শিখরা যখন তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য নানা প্রস্তাব রেখেছে, তখনো তাদের সাম্প্রদায়িক বলা হয়নি। মুসলিম লীগ আর জিন্নাহর রাজনীতিকে বলা হলো সাম্প্রদায়িক। ফলে দেখা যাবে এরকম নানা ভুল বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আরম্ভ হয়েছিল আর সেটা এখনো চলছে। জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ কিন্তু পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি আম্বেদকরের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল, কংগ্রেস যা পছন্দ করেনি। কংগ্রেস আম্বেদকরের দাবি-দাওয়া সামান্যও সমর্থন করেনি। দলিতদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়নি; কিন্তু ভীমরাও আম্বেদকরকে সাম্প্রদায়িক বলেনি, কারণ কংগ্রেস নেতারা তাকে হিন্দু বলেই মনে করত। সব অভিযোগ ছিল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আর মুসলমান সম্প্র্রদায়ের প্রতি।
দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা প্রথম শোনা যায় সাভারকারের মুখে। ১৯২৩ সালে সাভারকার ‘হিন্দুত্ব’ গ্রন্থে দাবি করেছিলেন ‘হিন্দুরা এক পৃথক জাতি’। পরের বছর ১৯২৪ সালের নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার নেতা লালা লাজপত রায় ‘ইরাবতী থেকে ব্রহ্মপুত্র’ নামে ধারাবাহিকভাবে ‘ট্রিবিউন’ পত্রিকায় তেরোটি প্রবন্ধ লেখেন, সেখানে তিনি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ভারত ভাগের কথা বলেছিলেন।(৩) তিনি সেখানে হিন্দু ভারত মুসলিম ভারত কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেন আর হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য দরকার বোধে বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগ করার কথা লিখেছিলেন।(৪) মুসলিম লীগ গঠনের প্রায় ছয় মাস আগেই ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সংগঠন শ্রীভারত ধর্মমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বছরেই পাঞ্জাবে অনুরূপ অপর একটি সংগঠন ‘হিন্দু সহায়ক সভা’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হিন্দু-পন্থী নীতি চালু করার আহ্বান জানানো হলো। ১৯০৭ সালে পাঞ্জাবে ‘হিন্দুসভা’ গঠন করা হয়। হিন্দুসভার পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে বলা হয় যে সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ অবিচলভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করাই নতুন সংগঠনের লক্ষ্য।
মুসলিম লীগ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলেছিল, হিন্দুসভাও হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার কথাই বলেছে; কিন্তু হিন্দুসভা যখন পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার স্লোগান দেয়, সেটা সাম্প্রদায়িক চিন্তা হিসেবে বিবেচিত হয়নি। যখন ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার দাবি জানায় তখন সেটিকে বলা হয় সাম্প্রদায়িক দাবি। মুসলিম লীগ তখন হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িক দল। রুশ দেশের দু’জন গবেষক দেখাচ্ছেন, লাহোরের ‘প্রতাপ’ পত্রিকায় হিন্দু মহাসভার নেতা লালা হরদয়ালের একটি প্রবন্ধে ভয়াবহ উগ্র আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায়। তিনি ঘোষণা করেন যে, হিন্দুস্থানের এবং পাঞ্জাবের হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। হিন্দু সংগঠন, হিন্দু রাজ, হিন্দুস্থানের মুসলমানদের হিন্দুধর্মে দীক্ষা প্রদান এবং আফগানিস্তান ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলো জয় করে সেইসব দেশের মানুষকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দান। না হলে হিন্দুরা সবসময় বিপদের মধ্যে থাকবে এবং হিন্দু জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।(৫) মুসলিম বিদ্বেষ তাহলে কাদের দিক থেকে প্রথম প্রচার করা হয়েছিল? বর্তমানে উল্লিখিত তথ্য বা ইতিহাস কী বলছে?
জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব আমদানি করেননি। ভারতবর্ষে দ্বিজাতি তত্ত্ব আমদানি করেছে হিন্দু মহাসভার সদস্যরা আর করেছে বাংলার বর্ণহিন্দু জমিদার আর সুবিধাভোগী শিক্ষিত সমাজ। হিন্দু মহাসভার ১৯৩৬ সালের এক বিবৃতিতে বলা হয়, হিন্দুদের মনে রাখা উচিৎ যে হিন্দুস্থান একমাত্র হিন্দুদের নিজস্ব বাসভূমি এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য হলো আর্য সংস্কৃতি এবং হিন্দু ধর্মের বিকাশ সাধন। ভারত একমাত্র হিন্দুদেরই দেশ এবং হিন্দু সংস্কৃতির বাহক।(৬) হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকার ১৯৩৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর হিন্দু মহাসভার সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন, ‘প্রধানত দুটি জাতি ভারতবর্ষে, হিন্দু এবং মুসলিম।’ তিনি পুনরায় ১৯৩৮ সালে বলেছিলেন, ‘ভারতবর্ষে-আমাদের হিন্দুস্থানে হিন্দুরাই হলো প্রধান জাতি আর মুসলমানরা সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠী।’(৭) জিন্নাহ তখন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে ছিলেন। তার মনে বিশ্বাস ছিল, কংগ্রেস আর গান্ধী মিলে এর একটি সুরাহা করবেন। ফলে তিনি হিন্দু মহাসভার উস্কানিকে তখন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সাভারকার সাঁইত্রিশ সালে আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদের তত্ত্বকে এক সম্পূর্ণ ও সর্বব্যাপী রূপ প্রদান করেন। তিনি ভারতে হিন্দুজাতির অস্তিত্ববিষয়ক তত্ত্বের মূল বক্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, সেই তত্ত্বের বুনিয়াদ হলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চারটি বিশ্বাস: হিন্দু, হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব এবং হিন্দুরাজ।
সাভারকারের মতে হিন্দুস্তানে উদ্ভূত যে কোনো ধর্মের মানুষই হিন্দু। যেমন হিন্দু, শিখ, বুদ্ধ, জৈন; কিন্তু মুসলমান আর খ্রিস্টানরা নয়। সেই সঙ্গে তিনি দাবি তোলেন যে হিন্দুরাই হিন্দুরাষ্ট্রের পুরোদস্তুর নাগরিক। হিন্দুদের পবিত্র ভূমির ওপর দাবি উত্থাপনকারী মুসলমানদের তিনি ‘বিদেশি’ আখ্যা দিয়ে ‘অখণ্ড ভারত’ ধ্বনি তোলেন। সাভারকারের মতে, স্বাধীন ভারতই জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র অথবা হিন্দুরাজই হতে পারে।(৮) কিছুদিন পর বলা হলো, হিন্দুরাই ‘প্রথম শ্রেণির নাগরিক’ আর মুসলিম সম্প্রদায় হলো ‘দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক’। অতএব, সর্বাগ্রে মুসলিমদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে হবে।(৯) মুসলমানদের ভারতে থাকতে হলে, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেই থাকতে হবে। কংগ্রেসের নেতা গান্ধী তখন মৃদুস্বরে সাভারকারের বক্তব্যের বা তত্ত্বের বিরূপ সমালোচনা করলেন। তিনি প্রথম কী বললেন? যদি ভারতে কোনো রাষ্ট্র বা হিন্দুরাষ্ট্র্রই গঠিত হয় তাহলে হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা সেখানে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের স্থানও পাকা করে দেবে।(১০) গান্ধী ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় এইসব কথা লিখেছিলেন। গান্ধী বললেন, যদি হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় মুসলমানদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা দ্বারা মুসলমানরা রক্ষা পাবে। গান্ধীর ভাষ্যমতে মুসলমানরা রক্ষা পাবে হিন্দুদের দয়ায়। গান্ধী সরাসরি ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শক্ত বিরোধিতা উপস্থাপন করলেন না। গান্ধীর নিজেরও হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মূলত তেমন আপত্তি নেই; কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্রে তিনি মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের হিন্দুধর্মের পরমত সহিষ্ণুতার মতো উদারতার ওপর ছেড়ে দেবেন।
জিন্নাহ এসব ঘটনায় উপলব্ধি করতে পারলেন, কংগ্রেসের কাছ থেকে মুসলমানরা কখনো সমমর্যাদা পাবে না। জিন্নাহ কখনো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেননি। সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে যেমন মুসলমানদের জন্য কিছু বাড়তি আসন সংরক্ষণ রাখতে চেয়েছেন, ঠিক একইভাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় তাদের জন্য বাড়তি আসন সংরক্ষণের কথা বলেছেন। সামগ্রিকভাবে ভারতে যেহেতু মুসলমানরা সংখ্যালঘু, মোট জনসংখ্যার চারভাগের এক ভাগ। জিন্নাহর দাবি ছিল কেন্দ্রীয় সভায় মুসলমানদের জন্য যেন চার ভাগের একভাগ নয়, এক-তৃতীয়ংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়। জিন্নাহ মনে করতেন তাতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ওপর আস্থা রাখতে পারবেন। কংগ্রেস এ ব্যাপারে কথা দিয়ে কথা রাখেনি। সাঁইত্রিশ সালের নির্বাচনে জিন্নাহ চেয়েছিলেন, কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ মিলে যৌথভাবে যেন প্রাদেশিক সরকারগুলো গঠন করা হয়- যাতে হিন্দু-মুসলমানরা নিজেদের আলাদা না ভাবে। কংগ্রেস নির্বাচনের আগে সে ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে তা রক্ষা করেনি।
ব্রিটিশ শাসকরা সব সময় ভারতের সাম্প্রদায়িকতাকে বড় সংকট বলে প্রচার করত। সুনীতি কুমার ঘোষ জানাচ্ছেন, জিন্নাহ সাঁইত্রিশ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারে যোগ দিয়ে সেই সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলটাকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, যদি কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যৌথভাবে সরকার গঠন করে তাহলে সকলে বুঝবে ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক প্রবণতা প্রধান সংকট নয়। তাতে করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্ব তাই কংগ্রেসের দিকে আন্তরিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।(১১) সর্বেপল্লী গোপাল লিখেছিলেন, সাঁইত্রিশ সালের নির্র্বাচনের আগে কংগ্রেস ও লীগ যে নির্বাচনি ইশতেহার দিয়েছিল সেখানে লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের মূলত কোনো পার্থক্য ছিল না।(১২) কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেস বিজয় লাভের পর পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো মুসলিম লীগকে সঙ্গে নিতে চায়নি। শরৎ বসু লিখেছিলেন, যদি সাঁইত্রিশ সালে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হতো হিন্দু-মুসলিম মতপার্থক্য অনেক কমে যেত।(১৩) কিন্তু কংগ্রেস মুসলিম লীগকে সঙ্গে রাখলোই না, সেই সঙ্গে গান্ধীসহ আরো অনেকে মুসলমানদের ব্যাপকভাবে কংগ্রেসে ঢোকা পছন্দ করলেন না। গান্ধী বলেছিলেন, তিনি ব্যাপকভাবে মুসলমানদের কংগ্রেসের সদস্য করার পক্ষপাতী নন যখন দুটি সম্প্রদায় পরস্পরকে বিশ্বাস করে না।(১৪)
যশোবন্ত সিংহ লিখেছেন, কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছিল। নিজের সাফল্য সম্পর্কে আগে নিশ্চিত ছিল না বলেই নির্বাচনী আঁতাতে গিয়েছিল। যখন ক্ষমতা পেল ‘সংখ্যায় ছোট, সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক’ সহযোগীকে ক্ষমতার ভাগ দেওয়া দরকার থাকল না। এটি একেবারেই বিশুদ্ধ সংখ্যাগুরুবাদ। তিনি আরও বলেন, যার বাস্তব পরিণাম হয়েছিল ভয়ংকর।(১৫) গান্ধী আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিচিত্র নারায়ণ শর্মা যিনি কংগ্রেস সরকারের প্রাদেশিক মন্ত্রী ছিলেন, তিনি লিখেছিলেন, ‘নির্বাচনে কংগ্রেস প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। আর কংগ্রেসের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পেল।’ তিনি আরো বলছেন, ‘মুসলমানদের উপেক্ষা করা হয়েছিল। আর তার দুষ্পরিণাম হলো প্রবল। পাকিস্তান জন্মের মূলে এই কারণ। দীর্ঘদিন যাবৎ আমার এই অভিমত পাকিস্তান সৃষ্টির মূল দায়িত্ব আমাদের-হিন্দু সম্প্রদায়ের। কংগ্রেসেরও।’(১৬) জিন্নাহর প্রস্তাব কংগ্রেস দ্বারা প্রত্যাখ্যান হবার কারণে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল নিজের দিনলিপিতে লিখেছিলেন, পাকিস্তান ছিল কংগ্রেসের সৃষ্টি, সরকার গড়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অস্বীকৃতি মুসলমানদের চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। জিন্নাহ প্রথম কংগ্রেসের এইসব নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখতে পারলেও পরে আর সামান্য আস্থা রাখতে পারেননি।
কংগ্রেসের নির্বাচন-পরবর্তী আচরণ প্রথমবার সম্প্রদায়-মনস্ক মুসলিমদের বিস্মিত এবং স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। তারা বুঝতে পারলেন, বর্ণহিন্দুরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কিন্তু মুসলমানরা দুর্বল, বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন। জওহরলাল বা গান্ধী বা কংগ্রেস যতই নীতিগত যুক্তি খাড়া করুক না কেন, মুসলিম লীগের সঙ্গে জোটে না যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য তার পরিণাম হলো ভয়াবহ।(১৭) মুসলমানরা নিজেরা এইবার মিলিতভাবে ভিন্ন পথে হাঁটতে শুরু করলেন। সন্দেহ নেই, এই সময় থেকেই মুসলিম লীগ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। সাঁইত্রিশ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস যে দু’বছর ক্ষমতায় ছিল, সেই সময়ে কংগ্রেসের বহু কৃষক নেতাসহ বামপন্থীরা কংগ্রেস সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বহু সাম্যবাদী তখন কংগ্রেস ছেড়েছিলেন। কংগ্রেস শাসিত বিহার, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজে কৃষক আন্দোলন দমনের জন্য সরকার একশ’ চুয়াল্লিশ ধারা ব্যবহার করে। দমন নিপীড়ন চালিয়ে বহু শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। কংগ্রেস এ সময় থেকে তার জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে, ভিন্ন দিকে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা আর সদস্য সংখ্যা দিনে দিনে কংগ্রেসকে ছাড়িয়ে যায়। ১৯৪০-৪১ সালে মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা ত্রিশ লাখের মতো, বিপরীত দিকে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লাখ থেকে কমে দাঁড়ায় চৌদ্দ লাখে।(১৮)
বারবার কংগ্রেস শর্ত ভঙ্গ করলে জিন্নাহ বুঝেছিলেন নিজেদের ভাগ্য এবার তাদের নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। কংগ্রেস বারবার শর্ত ভঙ্গ করায় জিন্নাহ রেগে গিয়ে বলেছিলেন, কংগ্রেস মুসলমানদের ধ্বংস করতে চায়। মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে জিন্নাহ ঘোষণা দেন যে, সমানে সমান না হলে কিংবা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভীতিবোধ না থাকলে দুটি দলের মধ্যে সম্মানজনক বোঝাপড়া সম্ভব হতে পারে না। দুর্বল পক্ষের এক তরফা শান্তির আবেদনে কেবল দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। ক্ষমতার দ্বারা দল পরিচালনা করতে না পারলে রক্ষাকবচ এবং সমঝোতা দাবির মূল্য ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতোই হয়। রাজনীতির অর্থই হচ্ছে ক্ষমতা- যা কেবল ন্যায়বিচার, সুন্দর ব্যবহার এবং সদিচ্ছার জন্য চিৎকার করলেই লাভ করা যায় না। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ‘এতদিন মুসলমানদের ভুলবশত সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আসলে তারা সংখ্যালঘু নয়। জাতীয়তার যে কোনো সংজ্ঞা অনুসারে মুসলমানরা একটি জাতি। ব্রিটিশ ভারতের মানচিত্র অনুযায়ী বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তানের মতো এদেশের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলমানরা-সেখানে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং ভারতের সমস্যাকে জিন্নাহ আন্তঃসাম্প্রদায়িকতা নয়, আন্তঃজাতিগত সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন।(১৯) জিন্নাহ জানিয়ে দিলেন, ভারতের মুসলমানরা শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, ভিন্ন একটি জাতি। মুসলমানরা যে একটি ভিন্ন জাতি এ কথাটা আগেই হিন্দু মহাসভার মুখ থেকে বের হয়েছিল। জিন্নাহ মুসলমানদের স্বার্থে এবার সেটি মেনে নিলেন। বর্ণহিন্দুদের দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি দেখে তিনি মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে ঘোষণা করলেন।
বর্ণহিন্দুরাই ত্রিশের দশকের শেষে জিন্নাহকে বাধ্য করেন মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। মুসলমানদের অবজ্ঞা করে হিন্দু মহাসভার হিন্দুত্বের ঘোষণা, গান্ধীর রামরাজত্ব আর গো-রক্ষার দর্শন এবং সর্বোপরি কংগ্রেস সরকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি জিন্নাহকে বুঝিয়ে দেয় বর্ণহিন্দুদের কাছে সংখ্যালঘু মুসলমানরা কখনোই ন্যায় বিচার পাবে না। কারণ তিনি দেখেছিলেন, সাম্প্রদায়িক বিভেদ টেনে কংগ্রেসের দুই নেতা নরিমান আর সৈয়দ মাহমুদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। কংগ্রেস বিজয় লাভ করার পর হিসাব মতো বিহারে সৈয়দ মাহমুদ এবং বোম্বাইয়ে পার্সি নরিমানের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা; কিন্তু তাদের দু’জনকে বাদ দিয়ে পরিবর্তে দু’জন হিন্দুকে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। মওলানা আজাদ পরবর্তীকালে এ ঘটনার নিন্দা করে বলেছিলেন, ‘কংগ্রেস তার প্রতিশ্রুত আদর্শ পুরোপুরি মেনে চলতে পারেনি। অনুতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, কংগ্রেসের জাতীয়তাবোধ তখনো সাম্প্রদায়িক বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুত্বের পরিবর্তে মেধার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন করার পর্যায়ে যেতে পারেনি।’(২০) জিন্নাহ এরকম ধারণা লাভ করার পর, বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। জিন্নাহর কট্টর সমালোচক শ্যামাপ্রসাদ বসু পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে জিন্নাহর পক্ষ নিয়ে দেখাচ্ছেন যে, ১৯০৬ সাল থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত সময়কালে জিন্নাহ ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী; কিন্তু গান্ধীর সময়কার কংগ্রেস নেতাদের কট্টোর একপেশে মনোভাবের কারণেই জিন্নাহ বাধ্য হলেন সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে।(২১) তিনি সংযুক্ত ভারতের ভেতরে মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাস বা ভূখণ্ড চাইলেন চল্লিশ সালে। শ্যামাপ্রসাদ বসু দেখাচ্ছেন, ‘লাহোর প্রস্তাব’-এর পরও জিন্নাহ ভারতের অখণ্ডতায় আস্থা হারাননি।(২২)
হিন্দুরা যখন মুসলমানদের জাতি হিসেবে আলাদা করে দিতে চেয়েছেন, জিন্নাহ বিরোধ এড়াবার জন্য ১৯৪০ সালে প্রথমবার তা স্বীকার করে নিয়েছেন মাত্র। সেইসঙ্গে আলাদা ভূখণ্ড দাবি করলেন যাতে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দমন পীড়নের মধ্যে তাদের থাকতে না হয়। সংখ্যাগুরু হিন্দু মানে হিন্দু সম্প্র্রদায় নয়, হিন্দু বলতে এখানে বর্ণহিন্দুদের কথা বলা হচ্ছে। জিন্নাহর লাহোর প্রস্তাব নিয়ে ভুল তথ্য রয়েছে কংগ্রেসের ইতিহাসে। জিন্নাহর লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবি তো দূরের কথা, পাকিস্তান বলে কোনো শব্দই ছিল না। মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের কার্যকরী সভা শেষ হয় গভীর রাতে; কিন্তু পরদিন সকল পত্রিকায় বলা হলো, মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। শ্যামাপ্রসাদ বসু দেখাচ্ছেন, লাহোর প্রস্তাবে সংবাদপত্রগুলোই ‘পাকিস্তান’ শব্দটি বসিয়ে দিয়েছিল।(২৩) হিন্দু প্রভাবিত পত্রিকাগুলো জিন্নাহর বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করল; কিন্তু পত্র-পত্রিকার ভুল সংবাদ প্রচার সাধারণ হিন্দু মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। জিন্নাহকে স্বভাবতই ঘটনাটি খুব বেকাদায় ফেলে দিয়েছিল। লাহোর প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ভুল সংবাদ প্রচারে কী সমস্যা হয়েছিল? মানুষ সর্বদাই পত্রিকার খবরকে খুব গুরুত্ব দেয়, বিশেষ করে সে-যুগে তা আরও বেশি দেওয়া হতো। পত্রিকার খবরের দিকে তাকিয়ে যারা দেশের রাজনীতির হালচাল বুঝতে চাইতেন, সেইসব শিক্ষিত সাধারণ মুসলমানরা মনে করলেন জিন্নাহ তাহলে তাদের জন্য পাকিস্তানই চাইছেন। স্বভাবতই এইরকম খবরে অনেক মুসলমানই খুশি হয়েছিলেন; কিন্তু প্রকৃত অর্থে জিন্নাহ পাকিস্তানের কথা উচ্চারণই করেননি।
ব্যাপারটি লক্ষণীয়। পত্রিকাগুলো কার ইঙ্গিতে ‘পাকিস্তান’ শব্দটি বসিয়ে দিয়েছিল সেটি একটি বিরাট প্রশ্ন। ভারতের বণিক সম্প্রদায়গুলোই তো পত্রিকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন। জিন্নাহর লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার সপ্তাহখানেক আগেই গান্ধী ভারত ভাগের কথা তুলেছিলেন। তিনি ১৯৪০ সালের পনেরো মার্চ রামগড় কংগ্রেসের সময় কংগ্রেস নির্বাহী কমিটির সদস্যদের প্রশ্ন করেছিলেন, যদি ভারতবর্ষকে হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতে ভাগ করার দাবি ওঠে তাহলে কংগ্রেসের নীতি কী হবে? পরে তিনি ১৭ মার্চ আবার লিখছেন, যদি মুসলমানরা ভারতকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে চায় তাহলে ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইচ্ছাকে কংগ্রেস জোর করে দমন করতে পারে না।(২৪) গান্ধী হঠাৎ এসব কথা বলছেন কেন? কথাটি হলো, মুসলমানরা যা দাবি করেনি, জিন্নাহ তখনো যে দ্বিজাতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি, সপ্তাহখানেক আগেই কংগ্রেসের সভায় বা তার লেখনীতে গান্ধী আগ বাড়িয়ে সে কথাটি বলছেন কেন? ভিন্ন একটি কারণ এর পিছনে ছিল। ঘনশ্যামদাস বিড়লাই এই দাবিটি রেখেছিলেন গান্ধী ও ভাইসরয় লিনলিথগোর কাছে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে। তিনি ভারতকে হিন্দু ফেডারেশন আর মুসলিম ফেডারেশনে ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি ক্রিপস মিশনের ক্রিপসের কাছে ১৯৩৯ সালে পৃথকভাবে হিন্দু ও মুসলমান জাতির জন্য ধর্মের ভিত্তিতে দুটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আগেই তাই গান্ধী প্রথম ভারত ভাগের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন।
ব্যাপারটি কি দাঁড়াল তবে? বণিক ঘনশ্যামদাসের আকাক্সক্ষাই গান্ধীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল লাহোর প্রস্তাবের আগেই; কিন্তু তিনি এমনভাবে বললেন, যেন মুসলমানদের দাবি ছিল সেটি। কথাটি নিজেই বারবার এভাবে উচ্চারণ করে মহাত্মা কি আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করার জন্য মুসলমানদের প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন? নিজেদের স্বার্থে সাংবাদিকদের কাছে কি আগাম কিছু বার্তা দিয়েছিলেন? সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ সালে হিন্দু মহাসভা যখন বারবার দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা উচ্চারণ করছিল, জিন্নাহ সম্ভবত তার পরিপ্রেক্ষিতেই বাধ্য হয়ে ১৯৪০ সালের উনিশে জানুয়ারি লন্ডনের ‘টাইম অ্যান্ড টাইড’ পত্রিকায় একটি লেখা লিখলেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন, ‘ভারতবর্ষে দুটি জাতি আছে এবং দুয়েরই মাতৃভূমি এক। তার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় উভয়ের শরিকানা থাকতে হবে।’(২৫) জিন্নাহ তার চিরন্তন বক্তব্যই পুনরাবৃত্তি করলেন, ভারতবর্ষ পরিচালনায় হিন্দু মুসলমান দু’পক্ষেরই অধিকার থাকতে হবে। তিনি হিন্দু মহাসভার দ্বিজাতি তত্ত্বকে বাতিল না করে বরং স্বীকার করে নিয়েই বললেন, হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি হলেও দুয়েরই মাতৃভূমি এক। দুয়ের মাতৃভূমি এক, মানে ভারতবর্ষ একসঙ্গে থাকবে। জিন্নাহর এ বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে সমন্বয়ের চেষ্টা, কাউকেই ছোট করা নয়। ভারতবর্ষকে আলাদা করার দাবিও নয়।
জিন্নাহর ‘টাইম অ্যান্ড টাইড’ পত্রিকার বক্তব্যে যেমন ভারত ভাগের প্রশ্ন নেই, লাহোর প্রস্তাবেও ছিল না। তিনি সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য স্বায়ত্তশাসিত একটি ভূখণ্ড দাবি করেছিলেন মাত্র। পাকিস্তান প্রস্তাব কথাটি ভুলভাবে বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংবাদে ছাপা হয়েছিল, যা বিতর্কের জন্ম দেয়। গান্ধী তার ওপর ভিত্তি করে ১৯৪০ সালের ছয়ই এপ্রিল হরিজন পত্রিকায় তো বটেই এবং তারপরেও এপ্রিল মাসেই একাধিকবার বলেছেন যে, মুসলমানরা ভারতবর্ষ ভাগ করতে চাইলে তিনি বাধা দেবেন না। মুসলমানরা ভারতবর্ষ ভাগ করতে চাইছে কথাটি গান্ধী বারবার বলছিলেন কেন? তিনি কি পরিকল্পিতভাবেই ভারত ভাগের দায় মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে নিজেই ভারত ভাগ করতে চেয়েছিলেন? মহাত্মা খুব ভালো করেই জানতেন যে, ঘনশ্যামদাস বিড়লাই ভারত ভাগ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মুসলমানদের দিক থেকে কেউ এ প্রস্তাবটি দেননি। তিনি তাহলে ঘনশ্যামদাস বিড়লার নাম ব্যবহার না করে মুসলমানদের নাম ব্যবহার করছেন কেন? কংগ্রেস এবং গান্ধী চলতেন বিড়লাসহ বড় বড় বণিকদের টাকায়। হ্যাঁ, ঘনশ্যামদাস বিড়লা যেভাবে হিন্দু এবং মুসলমানের দুটি ফেডারেশন চেয়েছিলেন, জিন্নাহ দুই বছর পর লাহোর প্রস্তাবে ঠিক তাই বলেছিলেন। ঘনশ্যামদাস ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ চেয়েছিলেন, জিন্নাহ ধর্মের ভিত্তিতে তা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য স্বায়ত্তশাসিত একটি ভূখণ্ড ভারত রাষ্ট্রের ভিতরে, ভারতকে বিভক্ত করে নয়।
জিন্নাহর ঘাড়ে যত দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হোক না কেন, দেখা যাচ্ছে ধর্মীয়ভাবে হিন্দু-মুসলমানকে বিভেদ করে দুটি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা বহু আগেই থেকেই চলছিল। ফলে এটি ভাবাই যেতে পারে পত্রিকায় পাকিস্তান কথাটি বসিয়ে দেওয়া নেহাৎ নির্দোষ সাংবাদিকতা ছিল না, ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করা হয়েছিল। জিন্নাহ তখন খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে, সেই জিন্নাহকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্যই এটি করা হয়ে থাকবে। জিন্নাহ সে ষড়যন্ত্রটা প্রথম টের পাননি বলেই পরবর্তী চাল চালতে ভুল করেছিলেন। জিন্নাহর সামনে তখন দুটি সংকট। মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে তিনি সাধারণ মুসলমানের বিশ্বাস বা দাবিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তিনি তা করতে পারতেন যদি তিনি কংগ্রেসের সহযোগিতা পেতেন। তিনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটি বুঝেছিলেন, মুসলমানদের সামান্যতম দাবি মেনে নেওয়ার অবস্থায় কংগ্রেস নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহঙ্কারে তারা মুসলমানদেরকে তো বটেই, মুসলিম লীগকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না।
কংগ্রেস বহুবার আলোচনায় বসে নিজেদের ইচ্ছাটাই চাপিয়ে দিতে চেয়েছে মুসলিম লীগের ওপর। মুসলিম লীগকে একেবারে পাত্তা না দেবার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের জোরটা কোথায়? তিন-চতুর্থাংশ হিন্দু জনগণ রয়েছে তার সঙ্গে। কংগ্রেসের সেই জোরটাই সবচেয়ে বড় জোর। জোর যার মুল্লুক তার। কংগ্রেসের সেই ক্ষমতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় লড়তে হচ্ছে জিন্নাহকে। কাজটা সহজ নয়। তিনি মুসলিম লীগেরও একচ্ছত্র অধিপতি নন। তিনি ইসলাম ধর্ম নিয়ে ভাবছেন না, কিন্তু মানুষ হিসেবে ভারতের বিরাট সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়কে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের পায়ের নীচে দলিত হতে দিতে চান না। পাকিস্তান শব্দটি যখন পত্রিকায় চলে এলো এবং জনগণের তাতে সম্মতি প্রকাশ পেল, জিন্নাহ অবশেষে তাই মনে করলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে লড়বার জন্য তিনি একটা শক্তিশালী অস্ত্র পেয়েছেন। মনে প্রাণে তিনি সবসময় ভারত ভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন; কিন্তু যখন দেখলেন, পত্র-পত্রিকাগুলো জিন্নাহর বিরুদ্ধে প্রচারণা হিসেবে পাকিস্তান আর দেশভাগের দায় তার ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে আর মুসলমান জনগণ তাতে খুশিই হয়েছে, মুসলমানরা পাকিস্তান পেতে চাইছে, জিন্নাহ তখন এটিকে নতুন অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। জিন্নাহ বিশ্বাস করতেন, গান্ধী এবং কংগ্রেস কখনো ভারত বিভাগ মেনে নেবেন না। জিন্নাহ সেরকম চাল চেলেছিলেন যাতে গান্ধী ভারত ভাগ ঠেকাতে মুসলমানদের ন্যায্য দাবিগুলো মেনে নেন। জিন্নাহ তখন ঘটনার পিছনের খেলাটা আন্দাজ করতে পারেননি। মনে করলেন, তিনি পাকিস্তানের দাবির পক্ষে থাকলে কংগ্রেস যেভাবেই হোক ভারত ভাগ ঠেকাতে চাইবে। নিজেদের একগুয়েমি ছেড়ে কংগ্রেস তখন মুসলমানদের সঙ্গে দাবিদাওয়ার প্রশ্নে আপোষ করতে রাজি হবে।
ভাইসরয় ওয়াভেল, আবুল কালাম আজাদসহ পরবর্তী বহু গবেষকই এই কথাটি স্বীকার করেছেন। জিন্নাহ ভারত ভাগ চাননি বলেই বারবার গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন সমঝোতায় আসবার জন্য, ভারত ভাগ চাননি বলেই ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। জিন্নাহ ভারত বিভাগ চাইলে, ১৯৪০ সালের পর ভাইসরয়ের দেওয়া প্রতিটি প্রস্তাব মেনে নিতেন। কারণ ভাইসরয়ের প্রস্তাব মেনে নিলেই তিনি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে নিজেই বহু সুবিধা লাভ করতে পারতেন। জিন্নাহর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল, গান্ধী কিছুতেই ভারত ভাগ চাইতে পারেন না, তিনি অবশ্যই মুসলিম লীগের সঙ্গে বসে মুসলমানদের যৌক্তিক দাবিগুলো বিবেচনা করবেন। গান্ধী যে শেষ পর্যন্ত জওহরলাল আর বল্লভভাই প্যাটেলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারত ভাগ মেনে নেবেন, এটি ছিল তার সম্পূর্ণ ধারণার বাইরে। গান্ধী যে ভারত ভাগের প্রশ্নে বহু আগেই একবার ঘনশ্যামদাস বিড়লার সঙ্গে এক পা এগিয়ে দিয়েছিলেন জিন্নাহর সে তথ্য জানা ছিল না। সুভাষচন্দ্র আর সাম্যবাদীরা তখন কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে গেছেন।
গান্ধীর সঙ্গে জিন্নাহর বারবার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা আর ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে। গান্ধী কয়েকবার রাজি হয়েছিলেন জিন্নাহকে পাকিস্তান দিতে। তিনি বললেন, বাংলা আর পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে বিভক্ত করে জিন্নাহ পাকিস্তান বানাতে পারেন। জিন্নাহ কিছুতেই বাংলা এবং পাঞ্জাবকে বিভাজন করার পক্ষে ছিলেন না বলে আলোচনা ব্যর্থ হলো। জিন্নাহ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত না করে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই মুসলমানদের জন্য স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারত যুক্তরাষ্ট্র যেখানে সবগুলো প্রদেশই হবে স্বায়ত্তশাসিত। সেখানে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আর কংগ্রেস চেয়েছে প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে। জিন্নাহ যদি ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান সৃষ্টি করে চলে যেতেন তাতে কংগ্রেসের আপত্তি হতো না; কিন্তু জিন্নাহ চাইছেন ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত কতগুলো মুসলিম প্রদেশ, কংগ্রেস সেটাই মানতে পারছিল না। জিন্নাহকে কিছুতেই প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে সরাতে না পারার জন্যই বারবার আলোচনায় বসতে হয়েছে গান্ধীকে। পাঞ্জাব আর বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে জিন্নাহ ক্ষুদ্র একটি অংশ নিয়ে আলাদা হয়ে যাক, কংগ্রেসের তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু সকল ক্ষমতা থাকতে হবে কেন্দ্রের হাতে যাতে যখন তখন প্রদেশগুলোকে দমন নিপীড়ন করতে পারে। ভারত ভাগের পর কাশ্মীরে বর্তমানে যা চলছে।
জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনা ভেঙে গেলেও গান্ধী তখনো আশা ছাড়লেন না। গান্ধী চাইছেন, জিন্নাহ যেন কংগ্রেসের দাবি মতো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেন। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার মানেই ভারতবর্ষের সব ক্ষমতা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের হাতে রয়ে যাবে। জিন্নাহ যেমন ছিলেন স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী নিয়মতান্ত্রিক মানুষ। গান্ধী ছিলেন ধার্মিক, নিজের বিশ্বাসকে তিনি ধর্মের মতো লালন করতেন। তিনি রামরাজত্ব চাইতেন বলে মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অনেক দাবির যথার্থতা বুঝতেন না। ভারত ভাগ সম্পর্কে গান্ধী বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিলেন। ফলে যতই আলোচনা হোক সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। বণিকদের স্বার্থের বাইরে যেমন তিনি যেতে পারতেন না, ভিন্ন দিকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দিনের শেষে তিনি স্বভাবতই একটি হিন্দুরাষ্ট্রের কথাই ভাবতেন যেখানে গো-হত্যা চলবে না। ফলে গান্ধী যতই উদার মন নিয়ে আপোষ আলোচনা চালাক না কেন সমাধানের সুযোগ ছিল না। কারণ তিনি তার গো-হত্যা বন্ধের দাবি ছাড়তে রাজি ছিলেন না। মুসলমানদের পক্ষে এ দাবি মেনে নেয়া মানে, নিজেদের ধর্মীয় এবং খাদ্য খাবার স্বাধীনতা বাদ দিয়ে গান্ধীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা ধর্মীয় ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা।
সারা দেশের মুসলমানরা যে মুসলিম লীগের সঙ্গে রয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য তার দরকার ছিল একটি নির্বাচন। জিন্নাহ বুঝতে পারছিলেন, সেক্ষেত্রে কংগ্রেস একটা ধাক্কা খাবে। সারা ভারতবর্ষের মানুষদের যে কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করে না, সেটা সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকারও ঠিক তাই ভাবছিল। ১৯৪৬ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, মুসলিম লীগ সব মুসলিম আসনে নব্বই শতাংশের মতো ভোট পেয়ে জয়ী হয়ে প্রমাণ করল যে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণভাবে তারাই করে। কংগ্রেস হিন্দু আসনগুলোতে ভালো করল, বাষট্টির মধ্যে সাতান্নটিতে বিজয়ী হয়ে। কংগ্রেস মুসলমানদের ন্যায্য দাবির প্রতি বারবার অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং হিন্দুত্বকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে নয় কোটি মুসলমান থেকে ততদিনে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। নির্বাচনের ফলাফল একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করল যে, দেশের মুসলমান ভোট দাতারা মুসলিম লীগের পিছনে আছেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলে একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ভারতের স্বাধীনতা দান এবং সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ক্যাবিনেট মিশনকে পাঠানো হলো। কংগ্রেসের সভাপতি আজাদ জানাচ্ছেন, ক্যাবিনেট মিশনে ‘স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আছেন এ জন্যও আমি সুখী হয়েছি, কারণ তিনি অবশ্যই আমাদের পুরনো বন্ধু।’(২৬) কংগ্রেস সভাপতি আজাদের এ বক্তব্য প্রমাণ করে, ক্যাবিনেট মিশনের লোকরা তাদের বন্ধু পক্ষ। ফলে জিন্নাহ ইংরেজদের দালাল ছিল কথাটা আর টিকছে না।
জিন্নাহর রাজনীতির মূল কথা ছিল ভারত ভাগ নয়। জিন্নাহ প্রধানত দাবি করেছিলেন, প্রদেশগুলো হবে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত। ভিন্নদিকে কংগ্রেস চাইতো, সংবিধানে সব ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রের হাতে। কংগ্রেসের কথা হলো, কেন্দ্র চাইলে প্রদেশগুলোর সংবিধান স্থগিত করে দিতে পারবে। মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের মূল বিরোধটা ছিল এখানেই। জিন্নাহ মনে করতেন, যদি প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসিত হয়, তাহলে যে প্রদেশগুলোতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে অন্তত বর্ণহিন্দুদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আধিপত্য করা সম্ভব হবে না। ভিন্নদিকে কংগ্রেস মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোর ওপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে, প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দিতে চাইছিল না। কংগ্রেস সে কারণেই মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব মেনে নিতে চায়নি। কারণ সেখানে তিনটি বিষয় ছাড়া সব ক্ষমতা রাখা হয়েছিল প্রদেশগুলোর হাতে। ক্যাবিনেট মিশন প্রথমত, দুটি প্রস্তাব রাখে; কিন্তু ক্যবিনেট মিশনের প্রথম দুটি প্রস্তাবই বাতিল হয়ে গেল। কারণ জিন্নাহ কলকাতা বাদ দিয়ে বা বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে এবং পাঞ্জাবকে টুকরা করে পাকিস্তান নিতে চাননি। জিন্নাহ বাঙালি এবং পাঞ্জাবি জনগোষ্ঠীকে ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা ভূখণ্ডে বিভক্ত করতে রাজি ছিলেন না। কংগ্রেসের আবার কেন্দ্রের হাতে স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন ‘ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র’ মেনে নিতে আপত্তি ছিল।
যখন লীগ আর কংগ্রেসের মধ্যে মিল হলো না তখন দু’পক্ষ নিজেদের পৃথক পৃথক বিকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করল। মুসলিম লীগের প্রস্তাব ছিল হিন্দু মুসলমান দুটি অঞ্চল নিয়ে সংযুক্ত ভারত রাষ্ট্র গঠিত হবে। দুটি অঞ্চলের কেন্দ্রের হাতে বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়, প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া বাকি সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছয়টি প্রদেশ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, বঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি অঞ্চল থাকবে। ছয়টি মুসলিম প্রদেশের জন্য পৃথক একটি সংবিধান রচনাকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। দুই অঞ্চলে পূর্বোক্ত দুই সংবিধান সভা স্থির করবে যে কেন্দ্রে কোনো আইনসভা থাকবে কিনা। কেন্দ্রকে রাজস্ব দেবার জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তাও দুই সংবিধান সভা স্থির করবে। তবে কোনোক্রমেই কেন্দ্রকে কর ধার্য করার অধিকার দেওয়া হবে না। দশ বৎসর কাল অতিবাহিত হবার পর কোনো প্রদেশ চাইলে কেন্দ্র থেকে পৃথক হয়ে যাবার অধিকারী হবে। জিন্নাহর এই প্রস্তাবে প্রদেশগুলোর জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা রাখা হয়েছিল। ফলে প্রদেশগুলো দশ বছর পর স্বাধীন হতে চাইলে কোনো রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বা যুদ্ধের প্রয়োজন পড়বে না। স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা এখানে বলা হয়নি।
ক্যাবিনেট মিশন এরপর ১৬ মে যে চূড়ান্ত প্রস্তাবটি দিয়েছিল তা জিন্নাহর মূলনীতির কাছাকাছি। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোকে তিনটি বর্গে ভাগ করা হয়। জিন্নাহ ভারতকে দুটি বর্গে ভাগ করেছিলেন, ক্যাবিনেট মিশন সেখানে তিনটি বর্গে ভাগ করল। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে মাদ্রাজ, বোম্বাই সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হবে ক বর্গ। ঠিক একইভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বালুচিস্তান নিয়ে গঠিত হবে খ বর্গ। বঙ্গ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হবে গ বর্গ। মিশনের চূড়ান্ত প্রস্তাবে বলা হলো, কেন্দ্রের আওতাভুক্ত বিষয়াবলি ছাড়া আর সব বিষয় এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশগুলোর ওপর বর্তাবে। কেন্দ্রকে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হবে তা ছাড়া আর সব ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যগুলোতে ন্যস্ত থাকবে। প্রদেশগুলোর নিজেদের মধ্যে দল গঠনের অধিকার থাকবে এবং এই দল বা প্রদেশগোষ্ঠীগুলোর স্বতন্ত্র প্রশাসন ব্যবস্থা ও আইনসভা থাকবে। ক্যাবিনেট মিশনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়, নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা কার্যকর হবার পর প্রদেশগুলোর যাকে যে বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার বাইরে চলে আসার অধিকার থাকবে।
কংগ্রেস সভাপতি আজাদ দশ-বারো বছর পর লিখছেন, তিনি মনে করেন না যে এই পর্বে ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ নিয়ে সংকট ছিল। বরং সংকটটা ছিল, ভারতের মধ্যকার নিজস্ব সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে। তিনি বলেন, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানগণ তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তখন খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। সত্য যে কয়েকটি প্রদেশে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। প্রাদেশিক পর্যায়ে এই সকল জায়গায় তাদের কোনো ভয় ছিল না; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের দিক থেকে মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিল। সেই জন্য তাদের মনে এই ভয় সর্বসময় তাড়িত করত যে হয়তো স্বাধীন ভারতবর্ষে তাদের অবস্থান এবং মর্যাদা সংরক্ষিত নাও হতে পারে।(২৭) জিন্নাহ যা বারবার বলতেন বা বিশ্বাস করতেন, আজাদ সে কথাটিই লিখছেন তার বইয়ে স্বাধীনতার দশ বছর পর। যদি আজাদের বক্তব্য মতো মুসলমানদের মনে ভয় থাকে নিশ্চয় তার কারণও থাকবে। সংখ্যাগুরুদের সম্পর্কে এই ভয়টির কথাই তো জিন্নাহ বারবার বলতেন। ফলে জিন্নাহ যে মুসলমানদের উস্কে দিয়েছিলেন সে কথাটি ঠিক নয়। মুসলমানদের মধ্যে সত্যিই একটি ভয় ছিল সংখ্যাগুরুদের সম্পর্কে।
কংগ্রেস নেতা আজাদের যে গ্রন্থ থেকে এই কথাগুলো জানা যাচ্ছে, তা তিনি লিখেছিলেন স্বাধীনতার দশ বছর পর। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় প্রদেশগুলো হাতে যে অধিক ক্ষমতা আর কেন্দ্রের হাতে খুব সামান্য ক্ষমতা থাকা দরকার ছিল আজাদ তার গ্রন্থে খোলাখুলি সে কথা স্বীকার করেন; কিন্তু গান্ধীসহ কংগ্রেস সে কথাগুলো মানতে চায়নি। তিনি লিখেছেন, ‘যদি এমন একটি সংবিধানের রূপরেখা গঠন করা হয়, যা এ নীতিকে রূপায়িত করবে, নিশ্চিত করবে যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে শুধু তিনটি বিষয় ছাড়া সব বিষয় প্রদেশ নিজেই পরিচালনা করবে। এতে করে হিন্দুদের আধিপত্যের আশঙ্কা মুসলমানদের মন থেকে দূর হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছাড়াও ভারতের মতো একটি দেশের জন্য এটি হবে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সমাধান। ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ, বিশাল জনসংখ্যা সংবলিত; যারা কমবেশি সমস্বত্ব এককে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বাস করে। তাই প্রয়োজন ছিল প্রদেশগুলোকে সম্ভাব্য ব্যাপকতর স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস দেওয়া।’(২৮) জিন্নাহর কথাগুলোই আজাদ তার বইয়ে হুবহু বলছেন। যা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় জিন্নাহর পথটাই আসলে সঠিক ছিল। যদি মওলানা দশ বছর আগে কথাগুলো চিন্তা করতে পারতেন তাহলে ভারত ভাগ হবার প্রয়োজন ছিল না, অবশ্য কংগ্রেসের নেতারা তার সঙ্গে এক মত হলে। কংগ্রেসের এ ব্যাপারে আজাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করার সম্ভাবনা কমই ছিল। কংগ্রেসের সভাপতি আজাদের বক্তব্যে এটিই প্রমাণিত হবে ভারত ভাগের দায় জিন্নাহর নয়।
ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করতে রাজি হলো না। গান্ধীর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল, কোনো প্রদেশকেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বর্গে যোগ দিতে বাধ্য করা চলবে না। কংগ্রেসের সব আপত্তির পেছনে প্রধান কারণ ছিল এই যে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায়। কংগ্রেস আসলে আসামকে গ বর্গে অর্থাৎ মুসলিম প্রধান বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করাটা মেনে নিতে পারছিল না। ফলে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বাদ দিয়ে কংগ্রেস হিন্দুস্বার্থ রক্ষায় সংকীর্ণতার পরিচয় দিচ্ছিল। অথচ সংবিধান রচনার পর আসাম চাইলেই গ বর্গ হতে বের হয়ে যাবার স্বাধীনতা তার ছিল। ব্রিটিশ শক্তি যে সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে মুসলিম লীগের বহু দাবি মেনে নিয়েছিল সেটা কংগ্রেসের অনেকের পছন্দ হয়নি। কংগ্রেসের কাছে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা না থাকা। কংগ্রেস যখন বলে প্রদেশগুলোর স্বাধীকার নষ্ট হতে পারে বর্গকর্র্র্র্তৃক তাদের সংবিধান প্রণীত হলে, তখন কংগ্রেসের এই বক্তব্য মায়াকান্নার মতো শোনায়। যারা প্রদেশের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সব ক্ষমতা দিতে চায় কেন্দ্রকে তাদের মুখে কি এ কথা আদৌ মানায়? দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস মনে করল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে আলাদা বর্গে রাখার মানে হলো ভবিষ্যতে সেগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। যদি প্রদেশগুলোর জনগণ ভবিষ্যতে স্বাধীন হতে চায় তাতে কংগ্রেসের এত আপত্তি কেন? সে সিদ্ধান্ত নেবার ভার তো প্রদেশের জনগণের।
মুসলিম লীগেরও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা নিয়ে কিছু আপত্তি ছিল। সব আপত্তি সত্ত্বেও ছয়ই জুন মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। জিন্নাহ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু আপত্তি সত্ত্বেও এ কথাও স্বীকার করেছিলেন, সংখ্যালঘু সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান হতে পারে না। পাকিস্তান সৃষ্টি সম্পর্কে প্রস্তাবে কিছু না থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে গান্ধীবাদী শৈলেশ কুমার সে সম্পর্কে বলছেন, লীগের এই স্পষ্ট প্রতীয়মান পরিবর্তিত ভূমিকার পিছনে জিন্নাহর বিশেষ অবদান ছিল।(২৯) জিন্নাহ ভারত থেকে কখনো সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে যাবার কথা বলেননি। জিন্নাহ হিন্দু প্রধান এবং মুসলিম প্রধান প্রদেশের ভিত্তিতে ভারতকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করার কথা বলেছিলেন। জিন্নাহর মূল যে দাবি প্রদেশগুলোর হাতে স্বায়ত্তশাসন বা অবশিষ্ট ক্ষমতা দান সেটা ক্যাবিনেট মিশন মেনে নিলে তিনি ক্যাবিনেট মিশনের যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পক্ষে প্রস্তাবে সম্মতি জানান। জিন্নাহর তরফে এটি এক বিরাট বিবেচনার পরিচায়ক। লীগ কাউন্সিলের তেরো জন সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেও বাকিরা জিন্নাহর কথা মেনে নিলেন। মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি দুটি প্রস্তাবই গ্রহণ করল।
সূচনাতে গান্ধীজি ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধী বলেছিলেন, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় রয়েছে দুঃখপূর্ণ দেশকে দুঃখযন্ত্রণাহীন দেশে পরিণত করার বীজ। হরিজন পত্রিকায় লিখেছিলেন, ‘ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভাইসরয় ও ক্যাবিনেট মিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় দলিলপত্র চারদিন ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে এমন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার যা করতে পারতো তার সর্বোত্তম দলিল এটি।’ কংগ্রেস তাহলে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করল না কেন? গান্ধী পরিকল্পনার পক্ষে কথা বলে তাহলে আবার সিদ্ধান্ত পাল্টালেন কেন? ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় যেভাবে আসাম এবং বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তার বিরোধিতা করলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বারদোলাই। তিনি ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ বাদ দিয়ে নিজের সুবিধার কথা ভেবে তার বিরোধিতায় স্থির রইলেন। গান্ধীও তার মত পাল্টে ফেললেন এবং তিনি বারদৌলিকে সমর্থন দিলেন। গান্ধী বারদৌলির মতো হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় মত পোষণ করলেন। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার স্বার্থে জওহরলাল এবং আজাদও এই ক্ষেত্রে গান্ধীর মত পরিবর্তন করাতে পারলেন না।(৩০) গান্ধী সম্পর্কে আজাদই এ তথ্য দিচ্ছেন তার গ্রন্থে।
সংখ্যালঘুর রাজনৈতিক অধিকার দিয়েই ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যেত; কিন্তু যারা সেটা দিতে চাইলেন না, ভারত ভাগের দায় কি তাদের নয়? সংখ্যালঘুরা তাদের মুক্তির জন্য সংখ্যাগুরুদের শাসন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবেই। ক্যাবিনেট মিশন বা আজাদ বা জিন্নাহর দাবিগুলো সেখান থেকে ভারতকে রক্ষা করার জন্য ভিন্ন সূত্র দিয়েছিল। দ্বিখণ্ডিত ভারত নয়, চাইলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা মেনে নিয়ে জিন্নাহ চাইলেন, মুসলমানদের নিয়ে ভারতের ভিতরেই থেকে যেতে যেখানে প্রতিটি প্রদেশ স্বশাসন লাভ করবে। কংগ্রেসের নেতারাই শেষ পর্যন্ত তা মানতে পারলেন না। ভারত ভাগের দায় তবে কার? কাদের কট্টোর মনোভাবের কারণে ভারত দ্বিখণ্ডিত হলো! আজাদ আরও লিখেছেন, ‘দশ বছর পর পেছনে তাকিয়ে আমি স্বীকার করছি যে জনাব জিন্নাহ যে কথা বলেছিলেন তাতে জোর ছিল। চুক্তিতে কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলই ছিল এবং কেন্দ্র, প্রদেশসমূহ ও বর্গসমূহের মধ্যে বণ্টনের ভিত্তিতেই কেবল লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেস সন্দেহ উত্থাপন করে সঠিক বা বুদ্ধিমানের কাজ কোনোটিই করেনি। যদি ভারতের ঐক্যের পক্ষে কংগ্রেস দৃঢ় হতো তবে পরিকল্পনাটি সন্দেহাতীতভাবে তার গ্রহণ করা উচিত ছিল।’(৩১)
ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ বা বর্জন করার সঙ্গে মূলত ভারত ভাগের ব্যাপারটা পরবর্তীতে চূড়ান্ত হয়েছে। দ্বিজাতি তত্ত্বকে ঘিরে আর সেটা প্রাধান্য পায়নি। মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হিসেবে ভারত ভাগকে অনেক বেশি তরান্বিত করেছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন খুব দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইলেন, যত দ্রুত সম্ভব। ভাইসরয় জানতেন, কংগ্রেসে গান্ধীর আর প্রভাব নেই কিন্তু জনগণের মধ্যে তার বিশাল প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে গান্ধী আর জিন্নাহ যদি আবার একমত হন, ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে পারেন। হয়তো ভারত ভাগকে আটকে দিতে পারে, যা মাউন্টব্যাটেন চাচ্ছিলেন না। জিন্নাহ তখনো বাংলা আর পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত করার বিরুদ্ধে, তিনি পুরো পাঞ্জাবকে পাকিস্তানে রেখে পুরো বাংলা ভারতকে দিতে রাজি। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন, ‘ইওর এক্সেলেন্সি বোধ হয় জানেন না যে একজন মানুষ আগে একজন বাঙালি বা পাঞ্জাবি, পরে সে হিন্দু মুসলমান। ধর্ম যাই হোক, তার পরিচয় সে বাঙালি বা পাঞ্জাবি। তার ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, তার অর্থনীতি সবই এক। সে ক্ষেত্রে পাঞ্জাব বা বাংলা ভাগ করা মানে পাঞ্জাবি বা বাঙালিদের ভাগ করা। এর ফলে নতুন করে রক্তপাত হবে, দাঙ্গা হবে।’(৩২) ফলে ভাইসরয়ের মনে আশঙ্কা ছিল, বিলম্ব করলে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। মাউন্টব্যাটেনের দেশভাগের গোটা কৌশলটাই ছিল কাউকেই থামার বা ভাবার সময় না দিয়ে দ্রুতগতিতে দায়টা সেরে ফেলা। মাউন্টব্যাটেন তিন মাসের মধ্যে সবকিছু করা স্থির করলেন।
যখন ভারত বিভক্ত হলো, তখন ভয়াবহ দাঙ্গার কারণ কী? মাউন্টব্যাটেনের দ্বিচারিতা আর নেহরুর ক্ষমতা লাভের জন্য পাগল হয়ে যাওয়া। ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকে কথা ছিল ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করে সেটাকে দশ মাস এগিয়ে নিয়ে এলেন কেন? তিনি কংগ্রেসের নেহরু, কৃষ্ণমেনন আর কতিপয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। তিনি কিছুতেই অবিভক্ত ভারত চাননি। তিনি বুঝেছিলেন, অভিভক্ত ভারত ব্রিটিশ শক্তিকে আর পাত্তা দেবে না। জিন্নাহ আর গান্ধী যাতে হঠাৎ অবিভক্ত ভারতের পক্ষে এক হয়ে না দাঁড়াতে পারেন, ভাইসরয় হিসেবে সেজন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন মাউন্টব্যাটেন। নেহরুও এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কারণ ইতিপূর্বে একবার গান্ধী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে ভারতকে অবিভক্ত রেখে জিন্নাহকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের কাছে খবরটা জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে তখন নেহরু বলেছিলেন, ‘বুড্ডার মাথা ঠিক নেই’। কবে আবার গান্ধী মত পাল্টে ফেলেন, তাই নেহরু ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করতে সামান্য দেরি চাইছিলেন না। কংগ্রেসেরও বহু নেতাও তাই চাইছিলেন। অবিভক্ত ভারতে ঘটনাচক্রে জিন্নাহ প্রধানমন্ত্রী হবে, কংগ্রেস নেতাদের সেটা না চাইবারই কথা। ফলে ভারত ভাগের সীমানা টানার জন্য কিছুতা সময় দরকার ছিল। মাউন্টব্যাটেন সে সময় পর্যন্ত দিতে রাজি হননি।
দশ মাস আগে স্বাধীনতা দেবার কৃতিত্ব নেবার জন্য সবকিছু অবাস্তবভাবে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে করা হয়েছিল। জুন মাসের তীব্র গরম এড়িয়ে রেডক্লিফ কিছুটা সময় চেয়েছিলেন বিরাট ভারতবর্ষের এতবড় একটা সীমানা নির্ধারণে, কিন্তু সে সময় তাকে দেওয়া হয়নি। চিঠি আছে নেহরুর, কীভাবে দ্রুত সীমানা টানার কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাউন্টব্যাটেনকে তাড়া দিচ্ছিলেন তিনি। মওলানা আজাদ জানতেন এর ফল খারাপ হবে। মাউন্টব্যাটেন সৈন্যবাহিনীর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পাকিস্তানের ভাগে এক-চতুর্থাংশ সৈন্য যাবে আর ভারতের ভাগে তিন-চতুর্থাংশ। মওলানা আজাদ দাঙ্গা ঠেকাবার জন্য ভাইসরয়কে বলেছিলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যেন বিভক্ত না করা হয়। কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনী কখনো সাম্প্রদায়িক আচরণ করেনি। ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনী দাঙ্গা ঠেকাবার কাজে ভূমিকা রাখতে পারবে। মাউন্টব্যাটেন শুনলেন না তার কথা। বললেন গর্বের সঙ্গে, যতক্ষণ আমি আছি সামান্য রক্তপাত ঘটবে না। কারো সাহস হবে না রক্তপাত ঘটাতে; কিন্তু আজাদ তার সঙ্গে একমত হননি।
স্বাধীনতা ঘোষণার কয়েক দিন আগে রেডক্লিফ সীমানা টেনে তা জানিয়ে দিলেন ভাইসরয়কে। কমান্ডার ইন চিফ অচিনলেক ভাইসরয়কে বললেন, স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই যেন সকল সাধারণকে ভারত-পাকিস্তানের সীমানা জানিয়ে দেওয়া হয়। যাতে মানুষ ধীরে সুস্থে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কাকে কোথায় যেতে হবে। ভাইসরয় তা করলেন না। মোটেই তার কথা আমলে নেননি, ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল পুরোপুরি অস্পষ্ট সীমান্ত ধারণার ভিত্তিতে।(৩৩) তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন আগে, সীমানা ঘোষণা করলেন তার একদিন পর। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরই মাউন্টব্যাটেন সীমানা নির্দেশ করতে আগ্রহী ছিলেন যাতে সব দায়দায়িত্ব নবগঠিত দু-দেশের ওপর বর্তায়।(৩৪) যশোবন্ত সিংহ মন্তব্য করেন, সাম্রাজ্যের অবসান নিশ্চয় ব্রিটিশদের হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়েছিল। কথাটা তারা প্রকাশ করতে পারছিল না; কিন্তু ভিতরের ক্রোধকে প্রশমিত করতে ভারতকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল ভাইদের মধ্যে তীব্র বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে। ব্রিটেনের ক্ষোভের বা তার ভুলের মাশুল দিতে হলো ভারতবাসীকে।
ভারত ভাগের ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে গেল। ছোটাছুটি আরম্ভ হলো যাদের সীমানার ওপর পারে যেতে হবে। খুলনা ছিল প্রথম ভারতের অংশ, মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানের। দলিলপত্রে আছে, খুলনায় উড়েছিল প্রথম ভারতের পতাকা, মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের। মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠান হয়েছিল পাকিস্তানকে স্বাগত জানিয়ে; কিন্তু নেহরুর দাবিতে রেডক্লিফের লাইন অমান্য করে মাউন্টব্যাটেন সেটা স্বাধীনতা ঘোষণার পর আবার পাল্টে দিলেন। কারণ মুর্শিদাবাদ দরকার ভারতের জলপ্রবাহ ঠিক রাখতে। ফলে এভাবে মাউন্টব্যাটেনের এমন খেয়ালখুশিতে সবকিছুর মধ্যে হ-য-ব-র-ল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ দিশেহারা হয়ে স্থান পরিবর্তন করতে গিয়ে, হাতে সামান্য সময় পেল না। মওলানা আজাদ স্পষ্ট করেই বলতে চান, মাউন্টব্যাটেন ইচ্ছাকৃত এটি করেছিলেন। কথাটা আরো অনেকে বলেছেন। মাউন্টব্যাটেন চাইছিলেন, ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে সারাজীবনের ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীল করে রাখতে। কাশ্মীরকে তিনিই একটা সমস্যা হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা আর রক্তপাতের উদাহরণ সৃষ্টি করে সারাবিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিলেন, ভারতের মানুষ কত অসভ্য বর্বর। ব্রিটিশ শাসন সেখানে দরকার ছিল, না হলে তারা আরো অসভ্য থেকে যেত।
তথ্যসূত্র:
১. লাডলীমোহন রায় চৌধুরী, ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ বিভাগ, কলকাতা: দে‘জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃ. ১২-১৩
২. সুকান্ত পাল, ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃ. ৬৪-৬৫ এবং আরও দ্রষ্টব্য, শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ৮১-৮২
৩. মৃণাল কান্তি চট্টোপাধ্যায়, জাতীয়তাবাদী জিন্নাহ, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃ. ১৪১
৪. যশোবন্ত সিংহ, জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা, বঙ্গানুবাদ, কলকাতা: আনন্দ ২০০৯, পৃ. ১১৪
৫. এ জি বেলস্কি, ‘হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ: ঐতিহাসিক উৎস এবং তত্ত্বাদর্শগত ও রাজনৈতিক নীতি’, এডি লিতম্যান ও আরবি রিবাকভ সম্পাদিত, হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় হিন্দু সমাজ, কলকাতা: ভস্তক, ১৯৯১, পৃ. ৪০-৪২
৬. এ জি বেলস্কি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
৭. এ জি নূরানি, সাভারকার ও হিন্দুত্ব, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট বুক লিমিটেড, ২০০৪, পৃ. ২৬
৮. এ. জি বেলস্কি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৪-৪৫
৯. সুজিত সেন, ‘সাম্প্রদায়িকতা: সংজ্ঞা ও বিভিন্ন ধরন- সম্পর্কিত কিছু কথা’, সুজিত সেন সম্পাদিত, বিষয় সাম্প্রদায়িকতা, কলকাতা: মিত্রম, ২০০৮, পৃ. ৮১
১০. এ. জি বেলস্কি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
১১. সুনীতি কুমার ঘোষ, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি- রাজনীতি, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ২০৪
১২. ঐ
১৩. শরৎ বসুর স্মৃতি সংরক্ষণ দলিলপত্র, পৃ. ১৮১-১৮২
১৪. সুনীতি কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯; আরও দ্রষ্টব্য, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি পেপারস, ফাইল ৪২/১৯৩৬
১৫. যশোবন্ত সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫
১৬. জিন্না: পাকিস্তান নতুন ভাবনা গ্রন্থের লেখক শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া বিচিত্র নারায়ণ শর্মার ১৪ জুলাই ১৯৮৪ সালে লেখা চিঠি।
১৭. যশোবন্ত সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০
১৮. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশন, কৃষেন্দু রায় অনূদিত, কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ৪০৩ ও ৪৮৩
১৯. হাসিনা আখতার, জিন্নাহ গান্ধী সম্পর্ক, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৩, পৃ. ২০৩
২০. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলী অনূদিত, ঢাকা: স্বপ্নীল প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ. ১৮-২০
২১. শ্যামাপ্রসাদ বসু, জিন্না: ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম সাম্প্রদায়িকতা, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ১১৪-১১৫
২২. ঐ
২৩. ঐ
২৪. সুনীতি কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩-২২৪
২৫. ঐ
২৬. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬
২৭. ঐ, পৃ. ১৬৭
২৮. ঐ, পৃ. ১৬৭-১৬৮
২৯. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জিন্না: পাকিস্তান নতুন ভাবনা, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৪, পৃ. ২১২
৩০. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০
৩১. ঐ, পৃ. ২১৩
৩২. ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক লাপিয়ের, ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট, রবিশেখর সেনগুপ্ত অনূদিত, ঢাকা:পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ১২২-১২৩
৩৩. যশোবন্ত সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২
৩৪. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ৯১৪
