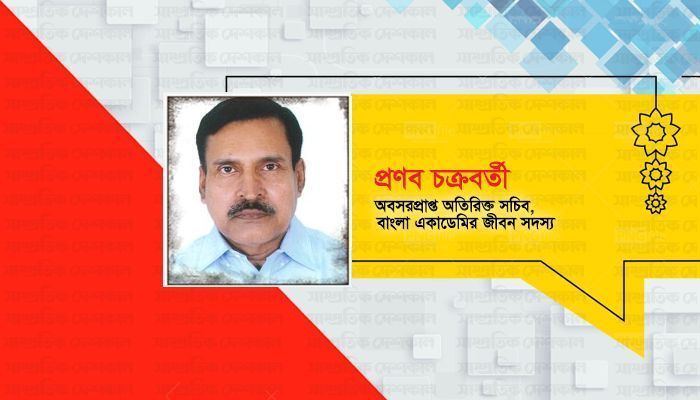
প্রণব চক্রবর্তী
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট (ন্যাটো) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৩০টি দেশ এই জোটের সদস্য। ন্যাটোর ভাষ্য, ‘রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্যোগের মাধ্যমে জোটের সব সদস্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের মূল লক্ষ্য।’
এ জোট গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশাল দেশ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের (ইউএসএসআর) আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের মিত্ররা বৃহত্তর রাজনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে ন্যাটোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।
বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল। ২০২০ সালে জোটে যোগ দেয় সর্বশেষ সদস্য উত্তর মেসিডোনিয়া।
তথাকথিত সহযোগী দেশ ইউক্রেন, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং জর্জিয়া এই জোটে যোগ দেওয়ার ইচ্ছার কথা আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে। ইউক্রেন ধারাবাহিকভাবে ন্যাটোর সদস্য হওয়ার আগ্রহের কথা জানিয়েছে। এমনকি, এই আগ্রহের কথা তাদের সংবিধানেও উল্লেখ করা হয়েছে।
জোটে যোগ দিলে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন হবে। ন্যাটোর প্রতিষ্ঠা চুক্তি অনুযায়ী, যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণকে সব মিত্রদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যার ফলে একে অন্যকে সুরক্ষিত রাখতে সদস্য রাষ্ট্ররা দায়বদ্ধ।
রাশিয়ার পুতিনের সোজাসাপ্টা বক্তব্য-তাদের প্রতিবেশী ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম শরিক ইউক্রেন কখনোই ন্যাটোতে যোগ দিতে পারবে না। এ ছাড়াও তারা ন্যাটোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, পূর্ব ইউরোপের সব ধরনের সামরিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম বন্ধ রাখতে। বস্তুত, ন্যাটো পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে বলে দাবি করছে রাশিয়া।
উল্লেখ্য, নতুন কোনো দেশকে সদস্য পদ দিতে হলে ন্যাটোর ৩০ সদস্যের সবাইকে সে বিষয়ে একমত হতে হবে।
তবে পশ্চিমা পরাশক্তিরা রাশিয়ার এসব দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা যুক্তি দেন, রাশিয়া ইউক্রেনের পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তে নাক গলাতে পারে না। তারা ন্যাটোর ‘খোলা দরজা নীতির’ কথা উল্লেখ করে জানান, যে কোনো ইউরোপীয় রাষ্ট্র ন্যাটোর সদস্যপদ চাইতে পারে।
পুতিনের যুক্তি, পশ্চিমের শক্তিরা মস্কোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাঁর মতে, স্নায়ুযুদ্ধের শেষের দিকে রাশিয়ার সঙ্গে ন্যাটোর মৌখিক চুক্তি হয়েছিল যে, তারা ইউরোপের পূর্বদিকে তাদের প্রভাব আর বিস্তার করবে না। তবে ন্যাটো এ ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতির কথা এ যাবৎ মেনে নেয়নি। ন্যাটোর পাল্টা অভিযোগ, রাশিয়া ইউক্রেনের সীমানায় ১ লাখেরও বেশি সেনা মোতায়েন করে চাপ সৃষ্টি করছে।
ফলে, ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের মিত্ররা মস্কোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এসব কূটনৈতিক তৎপরতা তেমন কোনো সাফল্য আনেনি। ওয়াশিংটন ও ন্যাটো ক্রেমলিনের মূল দাবিগুলো মেনে নেয়নি, আর রাশিয়া ও তাদের দাবিতে অনমনীয় থাকছে। ফলে পূর্ব ইউরোপের উত্তেজনা কমছে না।
কিয়েভের একাধিক মিত্র (যারা ন্যাটো সদস্য) ইতিমধ্যে অস্ত্র দিয়ে দেশটিকে সহায়তা করছে, যাতে তারা সম্ভাব্য কোনো আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। তবে এ তালিকায় নেই জ্বালানি গ্যাসের উৎস হিসেবে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল জার্মানি। যুক্তরাষ্ট্রও জানিয়েছে যুদ্ধ বাঁধলেও তারা ইউক্রেনের সহায়তায় সেনা পাঠাবে না।
যত সামরিক প্রস্তুতিই থাকুক, ইউক্রেন একা কোনোভাবে রাশিয়ার সঙ্গে পেরে উঠবে না। এমনকি ন্যাটোর সাহায্য নিয়ে লড়তে গেলেও আত্মরক্ষা কঠিন হবে। এর বড় কারণ দেশটির ভেতরে বিভক্ত সত্তা। ভাষা ও সংস্কৃতির বিভেদ। পশ্চিমাঞ্চল যতটা রাশিয়া বিরোধী, পূর্বাঞ্চল ততটাই রাশিয়াপন্থি। এরকম বিভক্ত অস্তিত্ব নিয়ে মহা শক্তিধর মস্কোকে মোকাবেলা করা সহজ নয়।
দীর্ঘদিন সোভিয়েত কাঠামোয় রাশিয়ার অধীন থাকায় ইউক্রেনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে কম। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের প্রতি মানুষের আস্থাও কম। যে কারণে নির্বাচন এলে ব্যবসায়ী, অভিনেতা ইত্যাদি পেশাজীবীরা লোকরঞ্জনবাদী কথাবার্তা বলে রাষ্ট্রের পরিচালক হয়ে যান। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপের ত্রিমুখী টানাপড়েনের মধ্যে দেশকে ভূ-রাজনীতির খেলায় বিজয়ী করার মতো রাজনৈতিক সামর্থ্য বর্তমান নেতৃত্বের আছে বলে মনে করে না কেউ।
রুশ-ইউক্রেন সংঘাতের বড় ফায়দা যাচ্ছে চীনের ঘরে। এ মুহূর্তে চীনের প্রায় ১৫ ভাগ আমদানি (মূলত কৃষিপণ্য) এবং ১৫ ভাগ রফতানি হচ্ছে ইউক্রেনের সঙ্গে। কিয়েভের প্রধান বাণিজ্যিক বন্ধু এখন তারা। আগে ইউক্রেনের সঙ্গে মূল বাণিজ্য হতো রাশিয়ার। ২০২০ থেকে সে জায়গা দখল করেছে বেইজিং। আবার ইউক্রেনের মতোই রাশিয়ার সঙ্গেও তাদের বাণিজ্য বেড়েছে কয়েকগুণ।
রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ নিষেধাজ্ঞার ফায়দা পাচ্ছে বেইজিং। চীন যদিও এখানকার সংঘাতে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে কথা বলে; কিন্তু ক্রিমিয়া নিয়ে জাতিসংঘের ভোটাভুটিতে তারা অনুপস্থিত ছিল। যুদ্ধ বাঁধলেও তারা এগিয়ে আসবে না, এমনটিই পর্যবেক্ষকদের ধারণা।
ইউক্রেনকে এখন বিশ্বব্যাপীশীতল যুদ্ধের নিকৃষ্ট এক বলি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এখানকার মানুষের দুর্ভাগ্য তারা মস্কো ও ওয়াশিংটনের রেষারেষির শিকার হয়েছে। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী অহংয়ের এক বৈশ্বিক ট্র্যাজেডিও বলা যায় ইউক্রেন সংকটকে। জয়-পরাজয়ের যুদ্ধ নয়, বরং সমাপ্তিহীন মরণ সংঘাতে মেতেছে এই অঞ্চল। যুদ্ধাস্ত্রের প্রদর্শনী ও তা বিক্রয়ের বিরাট সুযোগ এসে গেল শক্তিশালী দেশগুলোর হাতে।
অন্যদিকে মলডোভা, বেলারুশ এবং কাজাখস্তান এখন পুরোপুরি রাশিয়ার বলয়ে চলে গেছে। এখন ইউক্রেন নিয়ে টানাটানি চলছে। রাশিয়া ইউক্রেনকে হাতছাড়া করতে চাইছে না। আবার আমেরিকা ইউক্রেনকে রাশিয়ার হাতে দিতে চাইছে না; কিন্তু ইউক্রেন সেই ২০১৪ সালে রাশিয়ার হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। এখন যদি ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য হয়, তাহলে রাশিয়ার মাথায় হাত।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেউই রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে বলে আলামত মিলছে না। যদিও রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে আমেরিকা; কিন্তু তাতে কি ইউক্রেন রক্ষা পাবে? যদিও ইউক্রেনকে রাশিয়ার হাত থেকে রক্ষা করার আদৌ কোনো ইচ্ছা আমেরিকার আছে কিনা সে ব্যাপারে অনেকের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাশিয়াকে অর্থনৈতিক অবরোধ দিলে রাশিয়ার চেয়েও বেশি সংকটে পড়বে ইউরোপ। কারণ ইউরোপের জ্বালানির সিংহভাগ আসে রাশিয়া থেকে।
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমেরিকা একদিকে ইউরোপ এবং ন্যাটোকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে; অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে দর কষাকষি করেছে; কিন্তু কোনোটাই সফল হয়নি। ইউক্রেন থেকে আমেরিকার দূতাবাসের কর্মকর্তাদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও বলেছে তাদের ডিপ্লোম্যাটদের ইউক্রেন ছাড়তে; কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে- তাদের ডিপ্লোম্যাটদের ইউক্রেন ছাড়া দরকার তবে ইউক্রেনের এই যুদ্ধ পরিস্থিতিকে জিইয়ে রেখে বিশ্বের অনেক বিষয় নিয়ে রাশিয়া-আমেরিকার মধ্যে অনেক চুক্তি/ বোঝাপড়ার সম্ভাবনা আছে। হতে পারে রাশিয়ার নিরাপত্তার গ্যারান্টি, তুরস্কের ওপর থেকে আমেরিকার খবরদারি কমানো, গ্রিসে আমেরিকার ব্যাপক অস্ত্র বিক্রিতে বিরতি দান কিংবা ইরান, সিরিয়া বা মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি এবং চীন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ঐকমত্য ইত্যাদি।
রাশিয়ার ইউক্রেন দখলের পরিকল্পনা থেকে সরে আসার কারণে হয়তো বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে জার্মানিতে যে গ্যাস পাইপ লাইন নিচ্ছে রাশিয়া, সেখানে আমেরিকা বাদ সাধবে না। হাইপারসনিক মিসাইল ব্যবহার নিয়ে কোনো চুক্তিও হতে পারে। আফ্রিকায়প্রভাব বিস্তার নিয়েও সমঝোতা হতে পারে। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে ইউক্রেনের এই উত্তেজনা আসলে ইউক্রেনের জন্য নয়।
রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণকারী সাজলেও আমেরিকা ন্যাটোর মুখোশ পরে হাজির। সুবিধাটা এই ন্যাটোর ব্যানারে অনেক দেশকে জড়ো করা গেছে। আমেরিকার ইমেজ দাঁড়িয়েছে ন্যাটো ব্যাটসম্যানের মতো। সবসময় সাদা চোখে বোঝা মুশকিল কী করতে চাইছে! আবার রাশিয়াও কম যায় না। তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বলেছে তারা ইউক্রেনের ক্ষতি চায় না। ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধনের পর এ কেমন বুলি রাশিয়ার, তা বোঝা সহজ নয়।
এটি স্পষ্ট রাশিয়া এতদিন যাবৎ বলে কয়ে যা করাতে পারছিল না, তা এক লহমায় আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হলো; কিন্তু গরিবের ভাবী অর্থাৎ ইউক্রেনের যে অশেষ ক্ষয়ক্ষতি তা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির জন্য কয়েক দশকের বিপর্যয় ডেকে আনবে। ঘরহারা, স্বজনছাড়া মানুষ যে ট্রমার শিকার হলো. তা কি সারা জীবনে মুছবে? আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি। মানুষের জীবন যদি ন্যূনতম মর্যাদাবহন না করতে পারে কী হবে এই বিপ্লব দিয়ে? ন্যাটো বা পুতিনের তাতে কি কিছু যায় আসে না?
লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব
