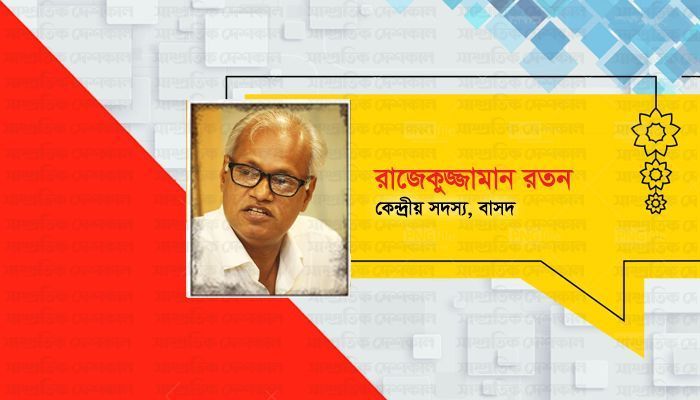
কোনো মানুষই চায় না দুঃসময় দীর্ঘস্থায়ী হোক। মানুষের প্রত্যাশা থাকে সুসময়টা দ্রুত আসুক এবং স্থায়ী হোক। সেটা ব্যক্তি জীবনে যেমন সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি। মানুষ বাঁচার চেষ্টা করে একাকী, স্বপ্ন দেখে নিজের মতো করে প্রধানত নিজের জন্য দুঃখ ভোগ করে একাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃসময়ের মুখোমুখি হলে সহায়তা প্রত্যাশা করে অন্যের কাছে। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেমনি মানুষ ভাবে সমাজে কি প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই? সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে প্রথমেই দলে দলে মানুষ আসে না। অনেক সময় একাকীই দাঁড়াতে হয় প্রতিবাদের পথে। তারপর পাশে এসে দাঁড়ায় একে একে অনেকে। একাকী মানুষ আর্তনাদ করতে পারে, কিন্তু একত্র হলেই গড়ে তোলে আন্দোলন।
মানুষের আকাঙ্ক্ষা দৃশ্যমান না হলেও ক্ষোভের তীব্রতা যে কত ভয়ংকর হতে পারে, সেটা দেখা গেছে এবারের আন্দোলনে। সরকারি স্থাপনা ও ক্ষমতাসীনদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে অতীতে বহুবার। কিন্তু এবার থানা জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে অনেক। পিটিয়ে হত্যা করেছে পুলিশকে, ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতার বাড়িঘর ভেঙে-চুরে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিয়েছে ছাত্রলীগকে। গত ১৫ বছর যাদের কাছে মাথা নিচু করেছিল, সেই মাস্তানদের ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে।
চারদিকে এত সাহসের ঘটনা ঘটছিল যে, মানুষ ভয় পেতে ভুলে গিয়েছিল। সবচেয়ে বড় ঘটনা, মানুষ ঘেরাও করতে গিয়েছিল গণভবন, প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার কথা শুনে মানুষ তা দখল করে নিয়েছিল। লুটপাট ন্যক্কারজনক ও অগ্রহণযোগ্য হলেও মানুষের ক্রোধের তীব্রতাটাও বিবেচনাযোগ্য। আগুনে পুড়েছে ৩২ নম্বর, ভস্মীভূত হয়েছে অনেক স্মৃতিবিজড়িত স্থান। ভবিষ্যতে মানুষ এসব বেদনার সঙ্গে স্মরণ করবে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, ক্রোধ কতটা তীব্র হলে মানুষ এসব জ্বালিয়ে দেয় আর নিজেদের দোর্দ- প্রতাপশালী মনে করে। আর যারা ভেবেছিল তাদের কেউ সরাতে পারবে না, তারা পালিয়ে যায়।
গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসকের পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর ৮ আগস্ট বিপুল আশা আর উদ্দীপনায় শপথ নিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। এক হাজার ৫০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু, ২২ হাজারের বেশি আহত, পাঁচ শতাধিক অন্ধ হয়ে যাওয়া, শত শত মানুষের পঙ্গুত্ববরণের মাধ্যমে যে অভ্যুত্থানের বিজয়, তা নিয়ে আলোচনার সময় এখন এসেছে। সমাজের নানা অংশের মানুষের নানা চাওয়া থাকলেও মানুষ মোটাদাগে যা চেয়েছিল তা হলো দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ করো, মানুষের ওপর নানা বাহিনীর নিপীড়ন বন্ধ করো, দ্রব্যমূল্য কমাও আর মানুষকে নিয়ে উপহাস ও তামাশা বন্ধ করো। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তিকে জবাবদিহির আওতায় আসতে হবে। সব চাওয়া কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এই দাবিতে- ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান চাই, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন চাই।
স্বাধীনতার পর ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরও জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন করার সংস্কৃতি এখনো তৈরি হয়ে ওঠেনি। জনগণের কাছে জবাবদিহির দায় না থাকায় টাকা, পেশিশক্তি আর রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তি ব্যবহার করে সংসদে একদল ‘মানি মেকার’ এবং ‘রুল ব্রেকার’ তৈরি হয়েছে। নির্বাচিত বা অনির্বাচিত উভয় ক্ষেত্রেই ভিন্নমত দমন করে তৈরি হয়েছে একদলীয় নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা।
সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হলেও রাষ্ট্রের তিন বিভাগের (সংসদ, নির্বাহী ও বিচার) মধ্যে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স না থাকায় ক্ষমতার পৃথকীকরণের অনুপস্থিতি ঘটেছে। সব ক্ষমতা হয়ে গিয়েছিল এক ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা হয়ে গিয়েছিল দলীয় কর্মচারী বা সরকারি কর্মকর্তা। জনগণের সার্বভৌমত্ব লেখা ছিল সংবিধানের পাতায়, নাগরিক অধিকার ছিল দূরের ছায়ার মতো। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, আয়না ঘরে নির্যাতন, দুর্নীতির মাধ্যমে প্রভূত সম্পদ অর্জন, বিদেশে টাকা পাচার- কোনোটাই তো সংবিধানসম্মত ছিল না। কিন্তু সংবিধান এসব থেকে ক্ষমতাসীনদের নিবৃত রাখতে পারেনি। গণতন্ত্রের কথা বহুল উচ্চারিত হলেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি।
আন্দোলন, সংসদ বর্জন ছাড়া নির্বাচন আদায় করার দৃষ্টান্তও কম। ক্ষমতা ছাড়তে না চাওয়া যেন ক্ষমতাসীন দলের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্রের ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও পুঁজিপতিরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চান। কিন্তু এক দলের শাসনের ধারাবাহিকতা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকেও বিনষ্ট করে ফেলেছে। সরকার ও রাষ্ট্র একাকার হয়ে সঙ্গে নাগরিকের সামাজিক চুক্তিকে উপহাসের বিষয়ে পরিণত করে ফেলেছে। বঞ্চনা, অনিশ্চয়তা আর অপমান মানুষের ক্ষোভের তীব্রতা বাড়িয়েছে। ফলে গণ-অভ্যুত্থান ছিল ক্ষমতাসীনদের নিপীড়ন থেকে মুক্তির ‘সামাজিক সম্মতি’।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের আন্দোলনে তাই শ্রমিক-জনতা দলে দলে যুক্ত হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী এই চাওয়া মুক্তিযুদ্ধের মৌল ভিত্তি তথা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের ঘোষণার সঙ্গে ছিল সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। জনগণ দেখেছে, ক্ষমতাসীনরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর জনগণের সঙ্গে করেছে প্রতারণা। ফলে মুক্তিযুদ্ধের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ২০২৪-এর আন্দোলনে নতুন করে জেগে উঠেছে। যার প্রকাশ ঘটেছে গ্রাফিতিতে, দেওয়ালে দেওয়ালে আর মাথায় বাঁধা জাতীয় পতাকায়।
প্রত্যাশা পূরণে তিন মাস যথেষ্ট সময় নয়, কিন্তু শুরু করার জন্য একেবারে কম সময়ও নয়। মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলাকে স্বস্তিদায়ক করা আর মানুষের মনে ভরসা দেওয়া যে তাদের পাশে সরকার আছে, এটা এই মুহূর্তের কাজ। অভ্যুত্থানের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা তো করতে হবে, তার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি কর্মপরিকল্পনা ও রোড ম্যাপ প্রণয়ন করে যত দ্রুত সম্ভব দেশে একটি সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে দেশ ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে গণতান্ত্রিক সরকারের পথে নতুন যাত্রা শুরু করবে। ভবিষ্যতে যাতে ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়, ক্ষমতা কাঠামোর সকল স্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত থাকে, সে জন্য সংবিধানের কিছু সংশোধন অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু বিশাল কাজের ফিরিস্তি করে সময়ক্ষেপণ যেমন সন্দেহ তৈরি করবে, তেমনি সমাজে অস্থিরতার জন্মও দেবে। পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যেও দমনমূলক মানসিকতা লক্ষ করা যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে- এই আশঙ্কা বাড়ছে।
ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি তিন মাসেও, ফলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ হয়নি। বকেয়া মজুরি আদায়ের জন্য শ্রমিকদের বিক্ষোভ করতে হচ্ছে, দখলবাজির হাত বদল হয়েছে, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির ঘটনা ঘটছে, বিজয়ী হয়েছি এই মনোভাব থেকে নিয়মবহির্ভূত কাজ করার প্রবণতা বেড়েছে- এগুলো ভালো দৃষ্টান্ত নয়। কিন্তু মানুষ আশা করে, এই সরকার জনগণের পক্ষে থাকবে, শ্রমিকের ওপর দমন-পীড়ন চালাবে না, কৃষকের পাশে থাকবে, সাধারণ মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করবে। মানুষের প্রত্যাশা যেন মার না খায়- এই দায়বোধ থেকে জনগণের ন্যূনতম চাওয়া পূরণে দেরি করা চলবে না।
মানুষ রাষ্ট্রের সংস্কার চায়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তার সংসারটাও তো চালাতে চায়। দ্রব্যমূল্যের আঘাত আর বাজার সন্ত্রাস থেকে রেহাই চায়। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে মুক্তভাবে লুটপাট চায় না। এসব নিয়ে আলোচনা খুব বেশি হচ্ছে না। মানুষের আশঙ্কা, দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখা, সন্তানের শিক্ষা আর কাজ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা আর সম্মানের সঙ্গে বাঁচা- এই ন্যূনতম চাওয়াগুলো যেন সংস্কারের বড় বড় কথার আড়ালে শূন্যে মিলিয়ে না যায়।
