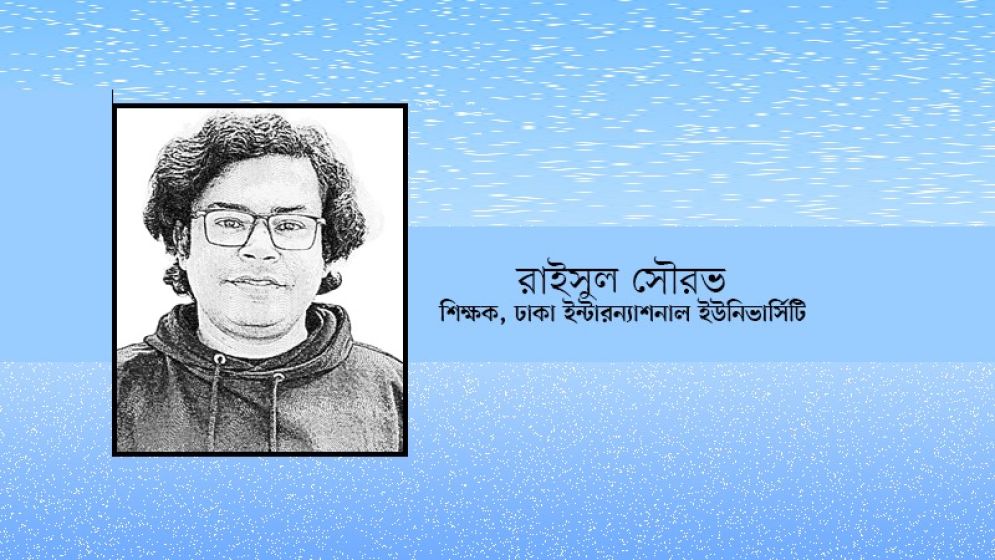
প্রধান উপদেষ্টা স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ককে আনুষ্ঠানিকভাবে স্টারলিংকের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা শুরু করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই আলোচনা দেশের আপামর জনগণের মধ্যে ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল যে এর মাধ্যমে হয়তো সরকারের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তে এখন থেকে যখন-তখন ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা লোপ পাবে। স্টার লিংক স্যাটেলাইট-ভিত্তিক সিস্টেমের মাধ্যমে বিশ্বের ১০০টির বেশি দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা দিয়ে থাকে, যার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সংকটের সময়ও গ্রাহক নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা পায়। প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেস সচিবও ইন্টারনেট বন্ধ রোধে একই প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি করেছিলেন।
গত জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান দমন করতে তৎকালীন সরকার দেশব্যাপী টানা পাঁচ দিন এবং মোবাইল ইন্টারনেট ১০ দিন উদ্দেশ্যমূলকভাবে বন্ধ রেখেছিল। তা ছাড়া সে সময় সরকার টেলিফোনে আড়ি পাতা ও ব্যক্তিগত ফোনালাপ জনসমক্ষে প্রকাশ করে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের জন্য সমালোচিত ছিল।
জনগণ প্রত্যাশা করেছিল ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের ফলে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার আগের সরকারের মতো ব্যক্তি বা স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে আড়ি পাতা বা ইন্টারনেট বন্ধ রাখার সুযোগ রেখে আইন তৈরি করবে না। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও টেলিযোগাযোগ আইনের খসড়ায় আড়ি পাতা এবং স্টারলিংকের ইন্টারনেট সেবার জন্য বিটিআরসি কর্তৃক প্রণীত খসড়া নির্দেশিকায়ও বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি উল্লেখ ছাড়াই ইন্টারনেট সেবা বন্ধের সুযোগ রাখা হয়েছে।
ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের ফলে ইন্টারনেটে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার এবং টেকসই উন্নয়ন ব্যাহত হয়, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের স্বীকৃত দলিলানুসারে নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য মানবাধিকার ব্যাপকভাবে ব্যাহত করে। রাজনৈতিক দল, আন্দোলনকারী বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিক্ষোভ আয়োজন, তাদের বক্তব্য প্রচার এবং সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য ইন্টারনেটে নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশগম্যতা অপরিহার্য।
সে কারণে ২০১৬ সালে জাতিসংঘ ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতাকে একটি মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ২০২১ সালে ইন্টারনেটে মানবাধিকারের প্রচার, সুরক্ষা এবং উপভোগ শীর্ষক একটি অবাধ্যতামূলক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৪২টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশও তখন এই প্রস্তাবের পক্ষে জাতিসংঘে ভোট দিয়েছিল। মানবাধিকার পরিষদ সব রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের ১৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহের ধারণার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করা থেকে বিরত থাকা এবং বিদ্যমান বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার আহ্বান জানায়।
তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রায়ই ভিন্নমত ও বিক্ষোভ দমাতে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় এবং জনস্বার্থ, জাতীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং জনশৃঙ্খলার অজুহাতে এ ধরনের অবৈধ পদক্ষেপকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে। ইন্টারনেট ব্যবহারে বাধা ভিন্নমত দমন এবং বিক্ষোভ দমনে দেশে দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। তবে কিছু দেশে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কীভাবে নেওয়া হবে এবং কোন কর্তৃপক্ষ, কখন, কেন ও কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে এসব আদেশ দিতে পারবে তা নিয়ে নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও কাঠামোবদ্ধ আইন রয়েছে।
মানবাধিকারের ওপর ইন্টারনেট বন্ধের প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। ইন্টারনেট সরাসরি বন্ধ করা ছাড়াও নানাভাবে ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তিতে বাধা তৈরি করা যেতে পারে; যেমন- ইন্টারনেটের উচ্চমূল্য, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের ওপর বিধিনিষেধ, ইচ্ছাকৃত গতি কমানো, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ইন্টারনেট ব্যবহার থেকে বঞ্চিত রাখা, মোবাইল ইন্টারনেট ২জি ট্রান্সফার গতিতে সীমাবদ্ধ করা, আধেয় (কনটেন্ট) নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি।
তাই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো তথ্য নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে ইন্টারনেট বন্ধ করাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। আংশিক বা সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউটের মাধ্যমে জনগণের তথ্যের অবাধ প্রবাহে প্রবেশগম্যতা সীমাবদ্ধ করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনানুসারে তথ্যপ্রাপ্তি ও প্রচারব্যবস্থার ওপর যেকোনো বিধিনিষেধ আরোপ করতে হলে তিন পর্বের আইনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। অর্থাৎ সে বিধিনিষেধ ১) আইনগত, ২) বৈধ এবং ৩) আনুপাতিক হতে হবে এবং যে রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার সীমিত করার চেষ্টা করবে, সে রাষ্ট্রকেই ওই তিন স্তরের পরীক্ষা যথাযথভাবে প্রমাণ করার দায়িত্ব নিতে হবে।
ওই নীতি অনুসারে সরকারের যেকোনো বিধিনিষেধ আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। তবে এ উদ্দেশ্যে শুধু আইন থাকলেই হবে না। আইনে এ-সংক্রান্ত বিধান সুনির্দিষ্টভাবে থাকতে হবে। উপরন্তু, আইনে এ ধরনের বিধিনিষেধের পরিধির ওপর কঠোর তদারকি বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হবে এবং এর যেকোনো অপব্যবহার রোধ করার জন্য বিচারিক প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
তিন পর্বের পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব বৈধতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সুরক্ষিত অন্যান্য অধিকারের ওপর যেকোনো সীমাবদ্ধতা কী লক্ষ্যে আরোপ করা হচ্ছে তা অবশ্যই স্পষ্টরূপে চিহ্নিত থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে সরকারকে আরো প্রমাণ করতে হবে কেন ওই যুক্তিসংগত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা অপরিহার্য।
সাধারণত কোনো রাষ্ট্র যখন আংশিক বা সম্পূর্ণ ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, তখন তাদের কর্মকাণ্ডের আইনি ভিত্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নড়বড়ে থাকে। ইন্টারনেট বন্ধের ওপর জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত হাই কমিশনের ২০২২ সালের একটি প্রতিবেদনানুসারে ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ৫৫টি দেশের ২২৮টি ঘটনার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট বন্ধের আনুষ্ঠানিক কারণ অজ্ঞাত।
তিন স্তর পরীক্ষার তৃতীয় উপাদান আনুপাতিকতার মানদণ্ড অনুসারে যেকোনো বিধিনিষেধকে সর্বনিম্ন হস্তক্ষেপমূলক বিকল্প হতে হবে এবং এর ফলে নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা যাবে না। বিধিনিষেধের কার্যকারিতা এবং এর মাধ্যমে সংঘটিত ক্ষতির একটি যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে যে, ওই বিধিনিষেধের ফলে ইন্টারনেট বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে অ্যাক্সেসে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল কি না এবং এটি দ্বিতীয় উপাদানে বর্ণিত আইনি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বনিম্ন বিধিনিষেধমূলক পদ্ধতি ছিল কি না।
সময়কাল এবং ভৌগোলিক সীমা যা-ই হোক না কেন, ইন্টারনেট বন্ধের ফলাফল সাধারণত মাত্রাতিরিক্ত হয়। কেননা ইন্টারনেট বন্ধ কেবল মত প্রকাশের অধিকারকে হ্রাস করে না বরং অন্য মৌলিক অধিকারগুলোকেও বাধাগ্রস্ত করে।
তা ছাড়া বিটিআরসির খসড়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্টারলিংক ও অন্যান্য এনজিএস এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশের আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ের (আইআইজি) সঙ্গে সংযুক্ত স্থানীয় গেটওয়ের মাধ্যমে সব স্যাটেলাইট ডাটা স্থানান্তর করতে হবে। যদিও স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো স্থানীয় গেটওয়ের মাধ্যমে ডেটা স্থানান্তরিত না হওয়া। ফলে সরকারের নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকিও এ ব্যবস্থায় কমে আসে। তাই খসড়া নির্দেশিকা অনুসারে জাতীয় অবকাঠামোয় একে অন্তর্ভুক্ত করলে তা এর ভিন্নসত্তা ও স্বায়ত্তশাসনকে দুর্বল করবে এবং সরকারের অন্যায্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা দৃঢ় করবে।
অধিকন্তু, এই নিয়মানুসারে সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে এমনকি স্যাটেলাইট গ্রাহকদের ইন্টারনেটও বন্ধ করে দেওয়া যাবে; যেমনটি আগের সরকার করত। সুতরাং, সরকারের এসব বিধান পরিবর্তন করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং সরকারি হস্তক্ষেপ ও নজরদারি সীমিত করা উচিত।
জাতিসংঘ কর্তৃক অবাধ ইন্টারনেট পাওয়া মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার পরও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা আমাদের সরকারি কর্তৃপক্ষের আচরণ ও মনোজগতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। তবে ২০২৪-এর শিক্ষার্থী-জনতার আত্মত্যাগের পর বর্তমান সরকারের ইন্টারনেট বন্ধের বিধানসংবলিত খসড়া আইন জরুরি ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে ওপরের মানদণ্ডগুলো নিশ্চিত করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ রোধ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নতুন উদ্ভাবনকে বাধাগ্রস্ত না করে বরং আলিঙ্গনের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে হবে।
