গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সংবিধানের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রশ্নটি গতি পেয়েছে
সাইফুল হক
প্রকাশ: ১৭ জুলাই ২০২৫, ১৩:৫৩
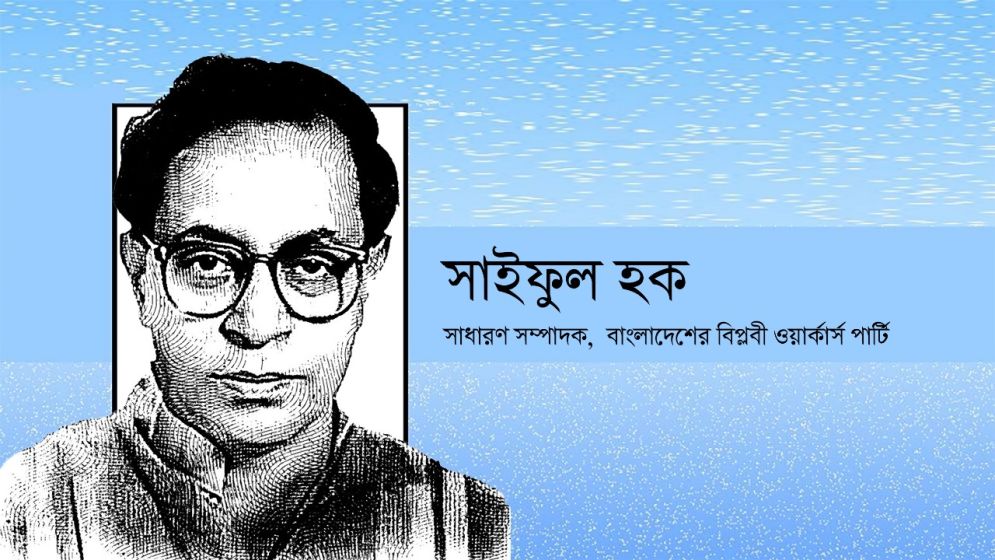
ছাত্র-শ্রমিক-জনতার মিলিত গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর হলো। কিন্তু এখনো ক্রান্তিকাল চলছে। বিপ্লবের পেছনে যেমন প্রতিবিপ্লব হাঁটে, তেমনি অভ্যুত্থানের পেছনে প্রতি-অভ্যুত্থান হাঁটে। এই এক বছরে ‘গণেশ উল্টে দেওয়ার’ অনেক চেষ্টা হয়েছে। সেদিক থেকে অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের টিকে থাকা একটা বড় সাফল্য। তা ছাড়া সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকারে দৃশ্যমান চেষ্টা অন্তর্বর্তী সরকারের আরেকটি বড় সাফল্য বলা যায়। রেমিটেন্স পাঠানোর হার গত দেড় বছরের তুলনায় এখন বেশ ভালো পর্যায়ে রয়েছে। আরকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়, গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। উদ্যোগটাও কিছুটা দৃশ্যমান।
গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং সংবিধানের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের যে প্রশ্নটি সামনে এসেছে, তা একটি নির্দিষ্ট গতি পেয়েছে। ঐকমত্য কমিশনসহ অনেক সংস্কার কমিশন হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বিভিন্ন খাতে সংস্কার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছে। সে আলোচনায় অন্যান্য দলের মতো বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টিও নিয়মিত অংশ নিচ্ছে। অনেক বিষয়ে আমরা এক ধরনের ঐকমত্যে আসতে পেরেছি। বিশেষ করে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে। ‘আস্থা ভোট এবং অর্থবিল’ বাদে বাকি প্রশ্নে সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে ভূমিকা রাখতে পারবেন, কথা বলতে পারবেন। এ ছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে এসেছি, সেটি হলো একজন ব্যক্তি তার জীবনকালে ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। এই ঐকমত্যগুলো যদি আলোর মুখ দেখে, তবে তা হবে গণতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামে এক চমৎকার নিদর্শন।
বিচার ও সংস্কারের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচন’। যে নির্বাচনটির জন্য দেশের মানুষ এত বছর ধরে অপেক্ষা করছে, তা সম্পন্ন করা। যদিও নির্বাচনের ব্যাপারে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে। তা সত্ত্বেও সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দ্রুত নির্বাচনে যেতে হবে। সরকার জানিয়েছে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার যদি বিদায় নেয়, তবে শত সমালোচনার মধ্যেও সরকারকে নিশ্চয় আমরা সাধুবাদ জানাব।
সরকারের সাফল্যের চেয়ে দুর্বলতা ও ব্যর্থতার তালিকা বেশ লম্বা। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরোধিতা করেই গণ-অভ্যুত্থানের সূত্রপাত। সরকার এতগুলো কমিশন করেছে, কিন্তু বৈষম্য বিলোপে কোনো কমিশন করেনি। বৈষম্য কেবল সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নয়-ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহরের মাঝে বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্যের বিলোপ জরুরি। কোনো এক অজানা কারণে বৈষম্য বিলোপের লক্ষ্যে সরকার কোনো দৃশ্যমান উদ্যেগ গ্রহণ করেনি, বরং গত এক বছরে বিভিন্ন খাতে বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩০ থেকে ৩৫ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে এসেছে। মানুষের কর্মহীনতা বেড়েছে।
সরকার ঘটা করে বিনিয়োগ সম্মেলন করেছিল। এখনো ‘এফডিআই’-এর আশাব্যঞ্জক কোনো অগ্রগতি হয়নি। বিনিয়োগ সম্মেলনের ফলে ভবিষ্যতে কোনো সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হবে কি না জানি না, কিন্তু পুরো ব্যাপারটি এখনো ‘আশাবাদের’ পর্যায়ে রয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তদের মধ্যে যে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে তার বিরুদ্ধে গত এক বছরে কিছুই করা হয়নি। বলা যেতে পারে বিগত সরকারের ব্যবস্থাটা কার্যত অক্ষুণ্ন রয়েছে। মাফিয়া, দুর্বৃত্ত ও লুটেরাদের সঙ্গে সরকারে যুক্ত ব্যক্তিরা, রাজনৈতিক দল, সংগঠন বিভিন্ন চেহারায় লেনদেনের মধ্য দিয়ে একটা বোঝাপড়ায় দেখা যাচ্ছে। ফলে চোখে ধুলো দেওয়ার মতন দুদককে দিয়ে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এটাই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা যে, অর্থনীতি যদি গোটা সমাজের মূল ভিত্তি হয়, অর্থনীতির ঘনীভূত বহিঃপ্রকাশ যদি রাজনীতি হয়, সে অর্থনীতি যদি দুর্বৃত্তকবলিত থাকে তাহলে রাজনীতির মধ্যে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনা দুঃসাধ্য।
একটি গণ-অভ্যুত্থান মানুষকে মুক্ত করে। গণতন্ত্রের পরিধি বৃদ্ধি করে, নারীর অধিকার বাড়িয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। অন্যদিকে গণ-অভ্যুত্থানের স্ববিরোধিতা সামনে এসেছে, মানুষের জানমাল ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। গত ১০ মাসে ‘মব সন্ত্রাসের’ শিকার হয়ে প্রায় ২০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। সরকার এক বছরের মধ্যে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। মানুষের চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা আমরা দেখছি। নারী তো বটেই, সমাজের নানা অংশের মানুষও নিরাপত্তাহীন। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কথিত বিপ্লবের নাম করে একটা মব সন্ত্রাস দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। একটা অরাজকতা এখনো পুরো দেশে চলছে। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সুযোগটা গ্রহণ করছে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকা এক ধরনের লুম্পেন ফ্যাসিবাদী মাফিয়া শক্তি।
আওয়ামী লীগের নেতারা কথায় কথায় বলত, সরকারের পতন হলে কয়েক লাখ মানুষ প্রতিহিংসার শিকার হয়ে প্রাণ হারাবে। গণ-অভ্যুত্থানের পর এই কথাটা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সম্প্রীতির অসাধারণ এক পরিচয় দিয়েছে। এ অর্জনটি অনেক বড়। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী আমাদের মধ্যে যে ঐক্যটি ছিল, গত এক বছরে সেটি অনেকটাই বিনষ্ট হয়েছে। হ্যাঁ এটা ঠিক, আন্দোলনের ঐক্যটি পরবর্তী সময়ে একই মাত্রায় থাকবে না, এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে একে-অপরের উগ্র বিরোধিতা, হিংসাশ্রয়ী তৎপতা বাড়ছে। বিভিন্ন প্রশ্নে দ্বিমত থাকবে, মতপার্থক্য থাকবে; কিন্তু রাজনীতিতে হিংসার আশ্রয় নেওয়া যাবে না।
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় হয়ে আসা দখলদারি-চাঁদাবাজি মানুষকে আওয়ামী-দুঃশাসনের স্মৃতি নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। যেটা খুবই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাগ্যের। যেটুকু সংস্কার হয়েছে তাতে আশা করা যায়, জুলাই মাসের মধ্যে ন্যূনতম ঐকমত্যের ভিত্তিতে আমরা জুলাই সনদ স্বাক্ষর করতে পারব। তারপর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেট জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতির পালা। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদি সরকার যেতে পারে তাহলে বাংলাদেশকে রক্ষা করার একটা শেষ সুযোগ থাকবে। নির্বাচন যদি কোনো কারণে পিছিয়ে যায় বা অনিশ্চিত হয়ে যায় তাহলে আমাদের বহুমাত্রিক ঝুঁকিটা বাড়বে।
বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ অব্যাহত। গত এক বছরে নতুন করে দুই লাখের মতো রোহিঙ্গা এখানে ঢুকেছে, তিন পার্বত্য জেলাকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতা দৃশ্যমান।
অন্যদিকে দেশের সব সীমান্ত দিয়ে ভারত পুশ ইন করেছে নিয়মিত। পুশ ইনের শিকার অনেকেই ভারতীয় নাগরিক, যারা ধর্মে মুসলমান। এই বিষয়গুলো দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে সত্যিই উদ্বেগের। এই পুশ ইনের মাধ্যমে ভারত এখানে একটা বার্তা দিতে চাইছে ‘বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান এবং অন্তর্বর্তী সরকার আমরা মানি না।’ এটা ভারতের একটা পুরোনো কৌশল, চাপে রেখে বশ্যতা শিকার করানো। বাংলাদেশ সরকারের দিক থেকেও কিছু দায় আছে। ভারতের সঙ্গে নানা বিষয় দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশীর সঙ্গে কাজের জন্য ন্যূনতম যে সম্পর্ক দরকার, সে বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগ আমরা লক্ষ করিনি। ভারতের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে দ্বন্দ্ব আছে। সমতা, ন্যায্যতা ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে আমরা এগুলো সমাধান করব। কিন্তু আমরা তো নিশ্চয়ই যুদ্ধ করব না। বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের দরকষাকষি সম্পর্কটা গড়ে তুলতে হবে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে। সে জায়গাটিতে সরকার সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি।
ব্যক্তির বিচারের যেমন সুযোগ আছে, দলের বিচারেরও সুযোগ আছে। আওয়ামী লীগ যে নৃশংসতা ঘটিয়েছে তার জন্য আইনগতভাবে আওয়ামী লীগের বিচারের একটা অবকাশ আছে। সেই প্রক্রিয়ায় না হেঁটে সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। এটা কার্যকর কোনো পন্থা নয়। একটি সংগঠিত দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে জনমানব থেকে মুছে দেওয়া যায় না। এ ধরনের শক্তিকে মোকাবিলা করতে হয় রাজনৈতিক, আদর্শিক ও সাংগঠনিকভাবে। আওয়ামী লীগকে যেভাবে নিশ্চিত করা হলো, মনে হচ্ছে যেন এটা ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছে। সরকারের আগের বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগকে তারা নিষিদ্ধ করবে না, কিন্তু সে জায়গাটা তারা ঠিক রাখতে পারেনি। এক ধরনের ম্যানুফ্যাকচার তৎপরতার মধ্য দিয়ে একটা জমায়েত করে দু-এক দিনে তারা আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করল। যেটা আখেরে ভালো ফলাফল বয়ে আনবে না। আওয়ামী লীগ গত এক বছরে তাদের কোনো অপরাধের দায় নেয়নি, ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। তাদের মধ্যে কোনো অনুশোচনা নেই, বরঞ্চ তারা পুরোনো জামানাকেই নানাভাবে ডিফেন্ড করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সুতরাং আওয়ামী লীগের তো নিশ্চয়ই দল হিসেবে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর প্রশ্ন আছে। বিচারের পাশাপাশি সরকার এর বাইরের জনগোষ্ঠীকে দেশের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ করার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে পারে। যেমনটা করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা, ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলেশন কমিশন অথবা ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস কমিশনের’ মধ্য দিয়ে।
যদি পেছনে তাকাই, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী দক্ষিণ পন্থার এক ধরনের উত্থান ঘটেছে। এই উত্থান মতাদর্শের দিক থেকে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে এবং কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে। এটা হচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের আরেকটি স্ববিরোধিতার জায়গা। দক্ষিণপন্থি অগণতান্ত্রিক শক্তি নানাভাবে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে উঠে এসেছে। এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের একটি পরোক্ষ মদদ রয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য অনেকটা বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি দায়ী। একসময় বলা হতো জার্মানিতে শ্রমিক শ্রেণির পার্টি যথাসময়ে বিপ্লব করতে পারেনি বলে শাস্তি হিসেবে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও কথাটা অনেকখানি প্রাসঙ্গিক। আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এখানকার বাম প্রগতিশীল বিপ্লবী শক্তিরই গোটা লড়াইয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানা বিভ্রান্তি, দোলাচলে এবং আপসকামী ভূমিকায় তা সম্মিলিতভাবে সম্ভব হয়নি। যে কারণে এর সুযোগটা গ্রহণ করেছে বিভিন্ন দক্ষিণপন্থি এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। এখন এটা নিয়ে আফসোস করার কিছু নেই, নতুন প্রেক্ষিত তৈরি হয়েছে। সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে এটা মনে করার কারণ নেই। দেশের বিপ্লবী বামপন্থি দেশপ্রেমিক শক্তির মগজের সংস্কারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্কারটা করতে না পারলে এখনকার দিনের যে চ্যালেঞ্জ, তার গভীরতা বুঝে কাজগুলো এগিয়ে নেওয়া যাবে না। ফলে আপাতত লক্ষ্যটা খুব সীমিত এবং এর মধ্য দিয়ে বাম প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক শক্তি তাদের চেতনার যে বোধ, এর মধ্য দিয়ে এগোতে পারলে ভবিষ্যৎকে আমরা ধারণ করতে পারব। অতীতের ভুলগুলোকে আমরা শোধরাতে পারব
অনুলিখন : বখতিয়ার আবিদ চৌধুরী
