মাওবাদী নিধন : উন্নয়নের মুখোশে মোদির রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস
কবীর আলমগীর
প্রকাশ: ৩০ জুলাই ২০২৫, ১২:৪০
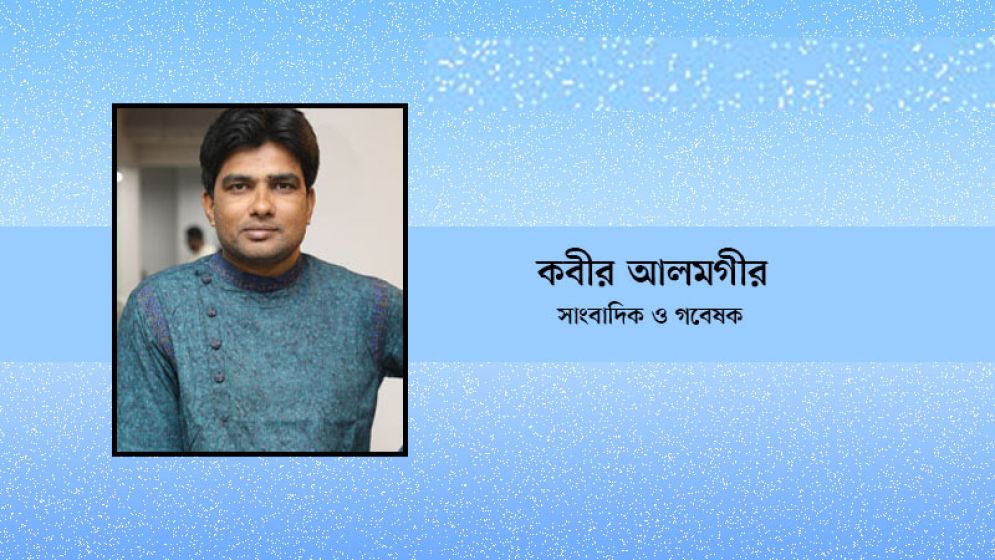
ভারত সরকার গত দুই দশকে মাওবাদী আন্দোলনকে দমন করার নামে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে। এই প্রয়াস আধিপত্যবাদী ভারতের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের গভীর নমুনা। মাওবাদীদের ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন গ্রিন হান্ট’ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ‘অপারেশন কাগার’ পর্যন্ত যে হত্যাযজ্ঞ চলছে, তা আসলে ভারতের করপোরেটপন্থি রাষ্ট্রনীতির অংশ। সরকার ‘অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা হুমকি’ হিসেবে যাদের চিহ্নিত করেছে, তাদের তালিকার শীর্ষে রয়েছে মাওবাদী আন্দোলন।
মাওবাদী আন্দোলন মূলত আদিবাসী ও দরিদ্র জনগণের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সশস্ত্র আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার সামরিক কৌশল হাতে নিয়েছে। এর মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী নরেন্দ্র মোদি সরকার ‘মাওবাদী নিধন প্রজেক্ট’ বাস্তবায়ন করছে। ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে মাওবাদীদের নির্মূল করতে চায় ভারত। এর সর্বশেষ রূপ হচ্ছে ‘অপারেশন কাগার’। এর মাধ্যমে গত মে মাসে হত্যা করা হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার (সিপিআই-মাওবাদী) সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশভা রাও ওরফে বাসভরাজকেও। শীর্ষ এই নেতাকে হত্যা ‘যুগান্তকারী সফলতা’ হিসেবে দেখছে ভারত।
মাওবাদী আন্দোলন ভারতে নতুন নয়। এর শিকড় ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলনে, যেখানে কৃষকেরা জমির মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অস্ত্র তুলে নেয়। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল ও জঙ্গল সান্যালের নেতৃত্বে ভূমিহীন কৃষকরা জমির মালিকানা দাবি করে। নকশাল আন্দোলনের আদর্শ ছিল চীনের মাও সেতুংয়ের পিপলস ওয়ার বা ‘জনযুদ্ধ’ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, গ্রামীণ অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে হবে। ভারতের মাওবাদীরা মনে করত, গণতান্ত্রিক নির্বাচন একটি ভ্রান্তপথ এবং আসল মুক্তি শুধু সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি ছড়িয়ে পড়ে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্রসহ একাধিক রাজ্যে। এই অঞ্চলগুলোকে বলা হয় ‘লাল করিডর’।
মাওবাদীরা ‘পিপলস আর্মি’ বা জনযুদ্ধের সংগঠন হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করে। যারা ধনী মালিকশ্রেণি, বহুজাতিক করপোরেট প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসী, দলিত, কৃষক, দিনমজুর সমাজের প্রান্তিক এই শ্রেণিগুলোর অধিকার আদায়ের চেষ্টা মাওবাদী লড়াইয়ের প্রধান ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের নামে বনজমি দখল, খনি লিজ ও সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সময়ের পরিক্রমায় এটি শুধু সশস্ত্র সংগঠনে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি বিকল্প রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা সশস্ত্র কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলো একত্রিত হয়ে ২০০৪ সালে গঠন করে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মাওয়িস্ট)। এটি ছিল মূলত সিপিআই (এমএল), পিপল ওয়ার গ্রুপ এবং মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টারের একীভূত রূপ। মাওবাদী আন্দোলন বিকাশের পেছনে যে কারণগুলো কাজ করেছে সেগুলো হলো ভূমিহীন কৃষকদের জমির দাবি, আদিবাসীদের বনজমির অধিকার হরণ, করপোরেট খনি প্রকল্পের আগ্রাসন, রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি ও বিচারহীনতা, দলিত-আদিবাসীদের ওপর সামাজিক নিপীড়ন। এই আন্দোলনের ভিত্তি মূলত গ্রামীণ ও বনাঞ্চল-ঘেরা অঞ্চল, যেগুলো খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ। মাওবাদীরা এসব এলাকায় বিকল্প শাসনব্যবস্থা (জনতা সরকার), পিপলস কোর্ট এবং গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। ফলে তারা শুধু সশস্ত্র গোষ্ঠী নয়, বরং একটি ছায়া রাষ্ট্রের রূপ।
ভারত সরকার বারবার মাওবাদী আন্দোলনকে ‘সন্ত্রাসবাদ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২০০৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মাওবাদীদের ‘ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি’ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে মাওবাদী দমন প্রকল্প শুরু হয়। রাষ্ট্রের চোখে মাওবাদীরা অস্ত্রধারী এবং রাষ্ট্রবিরোধী, তাই তাদের বিরুদ্ধে সেনা, আধা-সেনা (ঈজচঋ, ঈঙইজঅ, ইঝঋ), পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা একত্রিত হয়ে দমন অভিযান শুরু করে। নানা সময়ে এই অভিযানগুলোর বিভিন্ন নাম থাকলেও ‘অপারেশন গ্রিন হান্ট’ এবং ‘অপারেশন কাগার’ সবচেয়ে আলোচিত। ২০২৩ সালে শুরু হওয়া অপারেশন কাগার একটি নিখুঁত সামরিক প্রজেক্ট, এতে ড্রোন, থার্মাল ইমেজিং, স্যাটেলাইট নজরদারি, সাইবার মনিটরিং এবং গোপন পুলিশি অপারেশন একত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অপারেশনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো ‘ঃধৎমবঃবফ শরষষরহম’ বা বিচারবহির্ভূত হত্যা। ২০২৪-২৫ সালে ছত্তিশগড়ে একাধিক মাওবাদী নেতা তথাকথিত এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা আদালতে মামলা ছিল না। বস্তুত এই হত্যাকাণ্ডগুলোকে গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক ভাষায় ‘সফলতা’ হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই হত্যাকাণ্ড রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরই আরেক রূপ।
কেন মাওবাদীরা ভারত সরকারের টার্গেট? কারণ তারা রাষ্ট্রের একুশ শতকের ‘উন্নয়ন মডেল’-এর জন্য বড় বাধা। খনিজসম্পদ সমৃদ্ধ বনভূমিতে রাষ্ট্র চাইছে বিদেশি বিনিয়োগ আনতে, খনি খনন, বাঁধ নির্মাণ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন গড়তে। অস্ত্রধারী মাওবাদীরা এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। ফলে ভারত মনে করছে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থে তাদের নির্মূল করা জরুরি। আবার মাওবাদী আন্দোলন কেবল সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, এটি একটি বিকল্প রাজনৈতিক দর্শনও। ভারতের ভয় বুঝি এখানেই। মাওবাদীরা সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা, নির্বাচনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে ‘জনগণের গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। ফলে রাষ্ট্র মাওবাদীদের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে। ভারতের মূলধারার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তির চোখে আদিবাসীরা ‘উন্নয়নহীন’ বা ‘সুশাসনবিহীন।’ যখন আদিবাসীরা অস্ত্র তুলে নেয় এবং নিজেদের বনজমি রক্ষা করে, তখন তা রাষ্ট্রের চোখে বিদ্রোহ হয়ে যায়। মাওবাদীরা এই আদিবাসীদের সঙ্গে সংহতি গড়ে তুলেছে। ফলে মাওবাদীদের দমন মানে আদিবাসীদের দমন বটে।
ভারত সরকার পরিকল্পিতভাবে মাওবাদী নেতাকর্মীদের হত্যা করছে, তার পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে। মাওবাদীরা ভারতীয় সংসদীয়ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনÑসবকিছুকেই পুঁজিবাদের হাতিয়ার বলে তা প্রত্যাখ্যান করছে। তারা নিজেদের বিকল্প রাষ্ট্রীয় কাঠামো (জনতা সরকার, পিপলস কোর্ট, গেরিলা আর্মি) গড়ে তুলেছে, এটি ভারতের রাষ্ট্রকাঠামোর জন্য এক চ্যালেঞ্জ। ফলে রাষ্ট্র চায় এই বিপ্লবী রাজনৈতিক বিকল্প শক্তিকে গোড়াতেই শেষ করে দিতে।
মাওবাদীদের ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে উপস্থাপন করে সরকার আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সমর্থন পাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব ‘জঙ্গি দমন’ এজেন্ডার পক্ষে থাকে, আর দেশের অভ্যন্তরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই দমনকে ‘অপরাধ দমন’ হিসেবে দেখে। এই ভাষাগত রাজনীতি ও কৌশল রাষ্ট্রকে হত্যা ও নিপীড়ন বৈধ করার সুযোগ দেয়। ভারতের করপোরেট গণমাধ্যম মাওবাদীদের ‘উগ্রবাদী’, ‘চরমপন্থি’, ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে প্রচার করছে। সাধারণত ‘৫ জন মাওবাদী এনকাউন্টারে নিহত’ বলে প্রচারিত হলেও পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, এরা আদিবাসী কিশোর, দিনমজুর বা মহিলা। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের এই প্রপাগান্ডা রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের সামাজিক বৈধতা তৈরি করে। রাষ্ট্র যদি সত্যিই শান্তি ও নিরাপত্তা চায়, তাহলে দরকার মাওবাদী নেতাদের সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক সংলাপ। দরকার আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। দরকার মুনাফাভিত্তিক খনি-নীতি বন্ধ করা।
অপারেশন কাগারের আওতায় বহু মাওবাদী নেতাকর্মী ও সাধারণ গ্রামবাসীকে ‘এনকাউন্টার’-এর নামে হত্যা করা হয়েছে। এটাই বিতর্কের মূল জায়গাÑহত্যা আগে, তদন্ত পরেÑএ ধরনের রাষ্ট্রীয় কৌশল আইনের শাসন এবং গণতন্ত্রের বিপরীত। ‘লাল করিডর’ অঞ্চলগুলোর বেশির ভাগ অধিবাসী আদিবাসী। তাদের জমি, বন, জীবিকা মাওবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কের অজুহাতে দখল করা হচ্ছে। অপারেশন কাগারের সময় বহু গ্রামে সেনা ক্যাম্প বসানো হয়েছে, যা আদিবাসীদের ভয়ভীতির মধ্যে রাখে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এটি কি শুধুই মাওবাদী নিধনের অপারেশন, না কি এটি আদিবাসী ভূমি ও সম্পদ দখলের এক নতুন উপায়? অপারেশন কাগার পরিচালিত হচ্ছে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। ফলে নিহতদের তালিকা, পরিচয়, হত্যার পরিস্থিতি নিয়ে কোনো স্বচ্ছ তথ্য দেওয়া হয় না। এই গোপনীয়তা থেকেই সন্দেহ জন্ম নিচ্ছে, সরকার কি ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য আড়াল করছে?
খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে মাওবাদীদের হটিয়ে করপোরেট কোম্পানিগুলোর জন্য ‘পরিষ্কার জায়গা’ তৈরি করাই আসল উদ্দেশ্যÑএমন অভিযোগও উঠেছে। বিশেষ করে যেসব জায়গায় অপারেশনের পরপরই খনি অনুমোদন বা প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্র ও করপোরেটের যোগসাজশ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আবার সামরিক অভিযানে শুধু মাওবাদী নয়, নিরপরাধ আদিবাসী যুবক বা শিশুদের ‘মাওবাদী’ বলে হত্যা করছে ভারত সরকার, যা সহিংসতা ও প্রতিশোধের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। যতই হত্যা বাড়ে, ততই মাওবাদী প্রতিরোধও আরো সহিংস হয়। এটি ‘পুপষব ড়ভ ারড়ষবহপব’। বিচারবহির্ভূত হত্যা নতুন প্রতিশোধের জন্ম দেয়। ফলে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়, শান্তির সুযোগ সংকুচিত হয়।
মাওবাদীদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে যে, বহু মানুষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে বিকল্প রাজনৈতিক পথ খুঁজছে। কিন্তু যদি রাষ্ট্র কেবল হত্যা ও দমন করে, তাহলে এই বিকল্প চিন্তা আর প্রকাশের সুযোগ পায় না। ফলে রাজনৈতিক চিন্তার বৈচিত্র্য ধ্বংস হয় এবং রাষ্ট্র ক্রমে একনায়কতান্ত্রিক পথে এগোয়। ভারত সরকার মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, তা কেবল দেশটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়; বরং এটি রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৌশল। আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করা, মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সংলাপই কেবল পারে সংঘাতময় পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে। সামরিক কৌশল স্বল্পমেয়াদে হয়তো কিছু সফলতা এনে দিচ্ছে; কিন্তু এই আগ্রাসনের ফল দীর্ঘ মেয়াদে আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।
