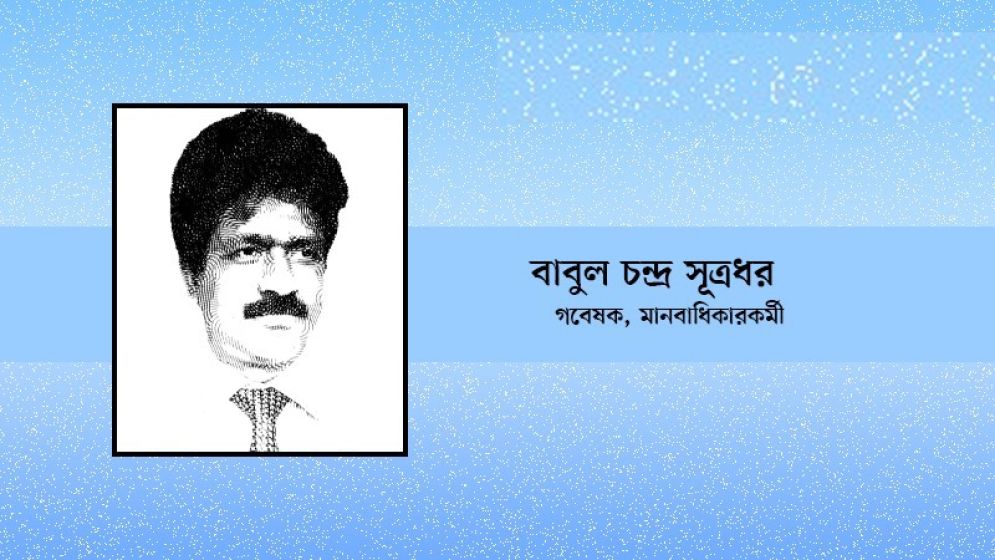
মানুষ প্রকৃতির সন্তান-এ সত্যটি যেকোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সান্নিধ্যে গেলে অতি সহজে উপলব্ধি করা যায়। তারা এখনো তাদের বুনিয়াদী জীবনধারাকে আঁকড়ে ধরে রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতার প্রভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় বহু পরিবর্তন সাধিত হলেও ঐতিহ্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে তারা ব্যতিক্রম বটে। এ জন্যই তো তারা আদিবাসী-‘আদি’ নিয়ে বসবাসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।
সরকারি গেজেট অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস; গেজেটে তাদের নাম ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’। জনগোষ্ঠীর নাম ও সংখ্যা নিয়ে অবশ্য আদিবাসী নেতৃত্ব ও সরকারের মধ্যে তথ্যগত বেশ গরমিল আছে। ২০১০ সালের এক জরিপের প্রতিবেদন অনুসারে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ও গোগ্রাম ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বসবাসরত পাঁচটি আদিবাসী (সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাই, পাহাড়িয়া ও রাজোয়াড়) জনগোষ্ঠীর পেশাগত পরিচিতি হচ্ছে প্রান্তিক কৃষক ১৫.৫ শতাংশ, কৃষি শ্রমিক ৭০.০ শতাংশ, রিকশা/ ভ্যানচালক ১.০ শতাংশ, মাটি কাটার কাজ ০.৯ শতাংশ, ও অন্যান্য ১২.৫ শতাংশ। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব আদিবাসীর ৮৭ শতাংশই ভূমিহীন। আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন পর্যায়ে অবস্থান করে তারা এখনো
প্রকৃতিকে প্রতিপালক হিসেবে শ্রদ্ধা করেন, তা সহজেই বোধগম্য। এসব জনগোষ্ঠীর লোকজন দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ততটা সংযুক্ত হতে পারেনি, তা বলাই যায়। তাই কেউ কেউ এই সামান্যকরণে আসতে চান যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও দারিদ্র্য প্রত্যয় দুটি একে অন্যের পরিপূরক।
তাদের আবার অবস্থানগত দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে; যথা-সমতলের আদিবাসী ও পাহাড়ি আদিবাসী। বাংলাদেশের সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বৃহত্তম হলো সাঁওতাল, যাদের বেশির ভাগই বসবাস করেন দেশের উত্তরের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায়। তন্মধ্যে আবার রাজশাহী, নওগাঁ ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সাঁওতালদের বসতির আধিক্য দেখা যায়।
সাঁওতাল জনগোষ্ঠী আগা-গোড়াই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। এখনো কৃষিই তাদের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভরসা। জানা যায়, খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলের কঠিন মাটিকে সাঁওতালরাই একদা কৃষিকাজের উপযোগী করে তুলেছিল। সাঁওতাল নারী-পুরুষ সবাই কঠোর শ্রমসাপেক্ষ চাষাবাদে সমানতালে কাজ করে থাকেন। আমরা এখন আলোচনা করতে চাই, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর তিনটি খাদ্যশস্যভিত্তিক ফসলি বা প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট উৎসব নিয়ে, যেগুলো অতিশয় নিষ্টার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। মাঠে ধানের বীজ বপন থেকে গোলায় ধান উঠানো পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে উৎসবগুলো চলতে থাকে। উৎসবগুলো হচ্ছে-
এরো : সিম : কৃষি সভ্যতার ধারক সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কৃষিকর্মের সূচনাপর্বের উৎসবটির নাম এরো : সিম। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাসে এটি পালিত হয়। ধানের চারা বা বীজ মাঠে বপন করার প্রাক্কালে আয়োজিত এই উৎসবটি আসলে প্রার্থনামূলক; ফসল যেন ভালো হয়, সারা বছরের খাবারের সংস্থান যেন নিরাপদে সাধিত হতে পারে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ না আসে, এ জন্য প্রার্থনা করা হয় ঈশ্বরের সমীপে। ঘরে ঘরে মুরগি বলি দিয়ে, মাংস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে সবাই মিলে আহার করা হয়।
হারিয়াড় সিম : শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট) মাসে ধানের চারা সবুজ হয়ে যাওয়ার পর পালিত হয় এই উৎসব। এখানেও শিশুরূপ চারাগাছগুলো যেন নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারে, সে জন্য প্রার্থনা করা হয়। মুরগি বলি দিয়ে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে পরে খিচুড়ি সহযোগে আহার করা হয়।
জান্থাড় : অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে ধান গোলায় তোলার সময় পালিত হয় জান্থাড়। বাঙালি সমাজে পালিত নবান্ন উৎসবের অনুরূপ জান্থাড় অনুষ্ঠানে নানা ধরনের বাহারি খাবার পরিবেশন করা হয়, যাতে নিকটাত্মীয়দেরও নিমন্ত্রণ করে আনা হয়ে থাকে। গোলা ভরা ধানে যেন সারা বছর সুখে-শান্তিতে খাওয়াদাওয়া চলতে পারে, সে জন্য প্রার্থনা করা হয় জান্থাড় উৎসবে। এ উপলক্ষে কোথাও কোথাও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
উৎসবপ্রিয় সাঁওতালদের সারা বছরই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান বা পরব লেগে থাকে। বর্ণিত ফসলি উৎসবগুলো ছাড়া তাদের প্রধান উৎসবের মধ্যে রয়েছে মাঘ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) মাসে চন্দ্রোদয়ের মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের নতুন বছরের শুরু হয়। নতুন বছরের শুভ সূচনার উৎসবটির নাম ‘মাঘ সিম’। পূজা-পার্বণ ও নানা আয়োজনে সারা বছরের জন্য মঙ্গল কামনা করে এই উৎসব পালিত হয়। ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তের মধ্যে যখন শাল, পলাশ, মহুয়া প্রভৃতি ফুল ফুটতে শুরু করে, তখন পালিত হয় ‘বাহাবঙ্গা’। একই সময়ে পাঁচ বছর পর পর বাহাবঙ্গাকে একটু বড় আকারে পালন করা হয় যার নাম মা: মড়ে। আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) নাচ-গানের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করা হয়; এই উৎসবটির নাম দাসায় দাঁড়ান। পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) পালিত হয় সহরায় উৎসব, ধান কাটা শেষ হওয়ার পরবর্তী চন্দ্রোদয় থেকে পাঁচ দিন ধরে এটি চলমান থাকে। এই উৎসবটি ভারতের কিছু অঞ্চলে কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসেও পালিত হয়ে থাকে। পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) মাসে পালিত হয় ‘সাকরাত’, যা বাঙালি সমাজের পৌষ পার্বণ (মকর বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি) সময়কে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়।
বলা আবশ্যক, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উৎসবগুলো নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, তারা কত নিষ্ঠার সঙ্গে উৎসবগুলো পালন করেন, তা প্রত্যক্ষ না করলে হয়তো ততটা উপলব্ধি করা যাবে না। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী সবাই যেন উৎসবের মূল প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে থাকেন, যা তাদের আচার-আচরণে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। অবশ্য যেকোনো সাংস্কৃতিক উৎসব জীবনাচরণের মৌল অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে। ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি কোনো না কোনো মৌলিক চাহিদা বা কামনা-বাসনার পরিণতি হিসেবে উৎসবের উৎপত্তি সাধিত হয়। বাঙালির জীবনে পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ ও বসন্তবরণ সামাজিক, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস রাজনৈতিক, ঈদ ও পূজা ধর্মীয় এবং নবান্ন ও হালখাতা অর্থনৈতিক উৎসব হিসেবে পরিগণিত, যা এতদঞ্চলের অধিবাসীদের সার্বিক জীবনচর্যা থেকেই উৎসারিত হয়েছে। প্রাক-ইতিহাস পর্ব বাদ দিলে প্রাচ্য বা প্রতীচ্য, প্রাচীন বা আধুনিক, সব সমাজব্যবস্থায়ই উৎসবের উপস্থিতি ছিল ও আছে। আবার কালের প্রবাহে কোনো কোনো উৎসবে নানা পরিবর্তনও এসেছে।
সাঁওতালদের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টতার একটি বড় প্রমাণ হলো বিভিন্ন সাজসজ্জায় গাছের পাতা, ফুল ও ডালের ব্যবহার। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তারা আজ পর্যন্ত গাছগাছড়ার ওপর নির্ভরশীল যা বনজ, ভেষজ বা লোকচিকিৎসা নামে সমধিক পরিচিত। এটিও প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য যে, বন-জঙ্গল উজাড় হয়ে যাওয়ায় তাদের খাদ্যের উপাদান বেশ কমে এসেছে। তাদের আবাসিক ঘরও মাটির তৈরি; তাদের আদিম প্রযুক্তির মাটির দ্বিতল ঘরগুলো সৌন্দর্যের প্রতীক, যা ভিনদেশি লোকজন মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন, জানতে চান এর নির্মাণশৈলী; ছবি তুলে সংগ্রহে রাখেন অনেকে।
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কাকনহাটের লালদীঘিপাড়ায় সমাজকর্মী শ্রীমতী লিপি টুডুর সঙ্গে কথা হয় ফসলি উৎসবমালা সম্পর্কে।
তিনি বলেন, ‘এখনো আগের মতোই এসবের আয়োজন হয়। তবে আয়োজন অনেকটা সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। প্রথমত, সাঁওতালদের নিজস্ব ফসলি জমির পরিমাণ খুবই কম; দ্বিতীয়ত, এখন আর সব মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল নয়, সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও কর্মক্ষম পুরুষ ও নারীর কেউ কেউ অন্যান্য অনেক পেশায় যোগ দিয়েছেন। ফলে টাকার অঙ্কে মানুষের আয় বেড়েছে, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে আরো বেশি, মানুষের প্রয়োজনের তালিকাও অনেক বড় হয়ে গেছে। তাই আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজনে বেশ ভাটা পড়ে গেছে। তবুও কৃষির সঙ্গে জড়িত সবাই এই উৎসবমালা পালন করে।’
ধান আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। জমির মালিক যেই হোক, ধানের আবাদ ভালো হলে সবার জন্যই মঙ্গল, সবার জন্যই খাবারের মাধ্যমে জীবন ধারণের নিশ্চয়তা আসে। এ ধারণা থেকে জমিজমা হারিয়েও সাঁওতালরা ফসলের ভালো ফলনের জন্য প্রার্থনামূলক এই পরবগুলো ভক্তিভরে পালন করে। আধুনিক উন্নয়ন অধ্যয়নে ‘খাদ্য নিরাপত্তা’ বলে সারা বিশ্বে যে বিশাল আলোচনা ও প্রচারণা পরিলক্ষিত হয়, তা সাঁওতালদের অনুভবে বহু আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। শুধু তা-ই নয়, আধুনিককালের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) লক্ষ্য নং-১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) লক্ষ্য নং-১, ২ ও ৩-এর মৌল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে তাদের এই উৎসব ও প্রার্থনা অতিশয় সাযুজ্যপূর্ণ।
সাঁওতালদের এই প্রার্থনা সফল হোক। শত সমস্যা, অশান্তি, দারিদ্র্য ও অনটনের মধ্যেও সব মানুষের খাদ্যের সংস্থান নিশ্চিত হোক। তাদের অন্তরের গানটিও সত্য হোক :
সাঁওতালি ভাষার গান বাংলা অনুবাদসহ
জম আবন ক্রুয়াবন (খেয়ে দেয়ে পান করে)
রিসকি রে বন তাঁহেনা (আনন্দে দিন কাটাব)
জিয়ন গাড়া রেয়া (জীবননদীর জলপান করে)
দা: বন ঞুয়া (মহানন্দে কাটাব)।
