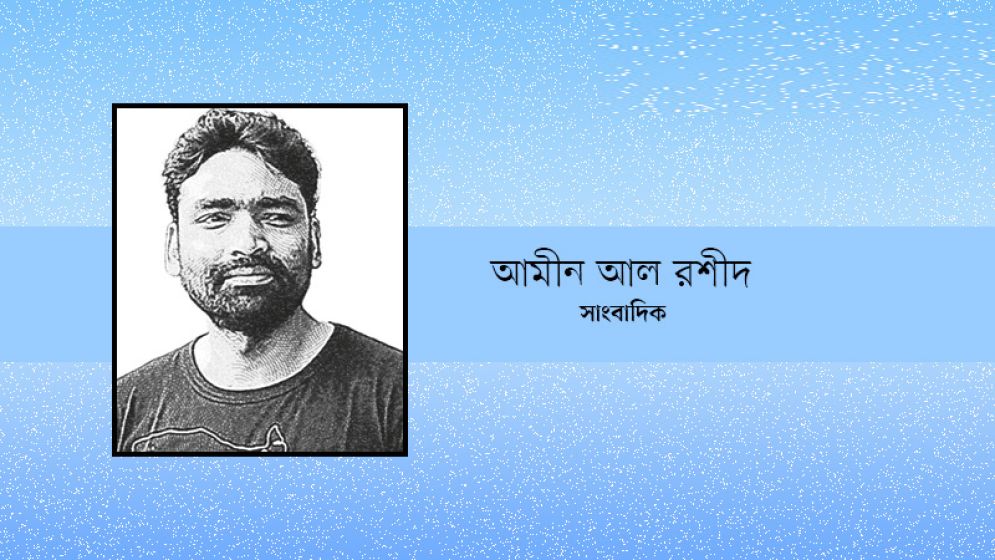
বাংলাদেশে এখন যে পদ্ধতিতে ভোট হয় বা ভোটাররা এখন যেভাবে জাতীয় নির্বাচনে তাদের প্রত্যেকের আসনে একটি নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দেন, তাতে ভোট গণনা শেষে যিনি সবার চেয়ে বেশি ভোট পান, তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। কেউ বিজয়ী প্রার্থীর চেয়ে মাত্র এক ভোট কম পেলেও তিনি পরাজিত বলে গণ্য হন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ‘ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (এফপিটিপি)’। অর্থাৎ যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনিই জয়ী এবং বাকি সবাই পরাজিত।
পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই পদ্ধতিতে ভোট হয় এবং এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। যদিও জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এই প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবিতে সরব হয়েছে। বিএনপি এই পদ্ধতির বিরোধী। তারা মনে করছে, নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তনের এই দাবি মূলত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র।
যদিও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আগামী দিনের রাজনীতিতে পিআর পদ্ধতিই হবে সবচেয়ে বড় বিতর্কের ইস্যু। শোনা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারও এই পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে, যাতে জুলাই অভ্যুত্থানের সামনের সারিতে থাকা তরুণদের দল এনসিপির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থীকে সংসদে আনা যায়।
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সেখানে এনসিপি যদি ১০ শতাংশ ভোটও পায়, তাহলেও সংসদে তারা ৩০টি আসন পাবে। আর ৩০টি আসন পেলে তাদের দলের সিনিয়র সব নেতাই সংসদে যেতে পারবেন।
সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে প্রতিটি দলই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে একটি প্রার্থী তালিকা নির্বাচন কমিশনে দেয় এবং তালিকাটি গোপন রাখা হয়। প্রতিটি দল যে পরিমাণ ভোট পায় সেই আলোকে ওই তালিকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিনিধি পায়। যেমন-বিদ্যমান ৩০০ আসনের সংসদ নির্বাচনে যদি কোনো দল ১ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে আনুপাতিক হারে তারা সংসদে ৩টি আসন পাবে। এরপর প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার গঠনের জন্য মোট প্রাপ্ত ভোটের ৫১ শতাংশ যে দল পাবে তারা সরকার গঠন করবে। কোনো দল এককভাবে ৫১ শতাংশ না পেলে একাধিক দল মিলে জোট গঠন করেও সরকার গঠন করতে পারে। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে ভোটাররা ভোট দেন দলকে, কোনো ব্যক্তিকে নয়। কারণ আনুপাতিক হারে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করতে গেলে সংসদে ছোট-বড়-মাঝারি সব দলেরই সদস্য থাকবে। এতে অনেক শক্তিমান প্রার্থী বাদ পড়বেন।
তবে পিআর নিয়ে আলোচনা বা বিতর্কের মূল কারণ অন্য জায়গায়। সেটি হলো, ধরা যাক নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের ৪০ শতাংশ ভোট পেল বিএনপি, তাহলে সংসদে তারা আসন পাবে ১২০টি। তখন কি তালিকার এক থেকে ১২০ নম্বরের প্রার্থী সংসদে যাবেন এবং ১২১ নম্বর থেকে ৩০০ পর্যন্ত ১৮০ জন প্রার্থী বাদ হয়ে যাবেন? যদি তাই হয় তাহলে দলগুলো এই তিনশ প্রার্থীর ক্রম ঠিক করবে কীভাবে, কীসের ভিত্তিতে বা কোন মানদণ্ড বিবেচনায়? কোনো দলই ৩০০ আসন পাবে না। সুতরাং যাদের নম্বর শুরুর দিকে থাকবে না, তারা কি দলের পক্ষে কাজ করবেন? কারণ শুরুর দিকে নাম না থাকা মানে তার সংসদের যাওয়া অনিশ্চিত। যদিও এই তালিকাটি গোপন থাকবে বলে প্রার্থীরা জানবেন না যে, কার নাম কত নম্বরে। কিন্তু বাংলাদেশের যে নির্বাচনী সংস্কৃতি, তাতে কেন্দ্রীয় নেতাদের বাইরে জেলা-উপজেলা পর্যায়ের নেতাদের নাম যে প্রথম দিকে থাকবে না, সেটি ধারণা করাই যায়।
পিআর পদ্ধতির একটি বড় সমস্যা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এই পদ্ধতিতে নির্বাচনের সুযোগ পান না। সবাইকে কোনো না কোনো দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে ভোটারটা ভোট দেন দলকে, ব্যক্তিকে নয়।
পিআর পদ্ধতিতে একই জেলা থেকে তিন থেকে চারজন এমপি হয়ে যেতে পারেন। আবার অনেক জেলা থেকে একজনও নাও হতে পারেন। ধরা যাক, কোনো একটি জেলায় বড় দলের একাধিক নেতা আছেন। সে ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে এমপি দিতে গিয়ে হয়তো ওই বড় নেতাদের সবাই সংসদে যাবেন। আবার অনেক জেলা থেকে একজনও নাও যেতে পারেন।
পিআর পদ্ধতিতে ভোট দিতে হয় দলকে, প্রার্থীকে নয়। ফলে ভোটাররা জানবেন না তিনি কাকে ভোট দিচ্ছেন বা কে তার প্রার্থী। ভোটার জানবেন না ভোটের পরে তার আসনের দায়িত্বে কে থাকবেন? আর নির্বাচিতরা যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো আসনের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন না, ফলে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে তাদের তেমন কোনো যোগাযোগও থাকে না। জনগণের প্রতি তাদের ওই অর্থে কোনো দায়বদ্ধতাও থাকে না।
একাডেমিক্যালি বলা হয়, এমপিদের কাজ স্থানীয় উন্নয়ন নয়, বরং তারা শুধু আইন প্রণয়ন করবেন। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটি একটি কেতাবি কথা। এখনো এই দেশে এমপিরাই স্থানীয় উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করেন। আইন প্রণয়ন তাদের প্রধান কাজ হলেও জনগণ মনে করে উন্নয়নকাজ ‘এমপি সাহেবের’ মাধ্যমেই হবে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করা গেলে এমপিদের খবরদারি কমবে। কিন্তু সেটি করতে গেলে প্রক্রিয়াটি শুরু করার পরও তার ফল পেতে অনেক সময় লাগবে। রাতারাতি সবকিছু বদলে দেওয়া যায় না। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের পরে অনেক দলের নেতাদের কথা ও বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হয়, তারা এক বছরেই বাংলাদেশকে জার্মানি বানিয়ে ফেলতে চান।
তা ছাড়া বিশ্বের অন্য কোন কোন দেশে এই পদ্ধতি চালু আছে এবং তাদের অভিজ্ঞতা কেমন, তার সঙ্গে বাংলাদেশকে মেলানো কঠিন। কেননা বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশ, যেখানকার রাজনীতি অত্যন্ত জটিল।
এই বাস্তবতা নিশ্চয়ই নির্বাচন কমিশনের বিবেচনায়ও রয়েছে। যে কারণে গত ২৬ জুলাই খুলনা অঞ্চলের নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়সভার শুরুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনও বলেছেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সংবিধান ও আইন বদলাতে হবে। আইন বদলানো না পর্যন্ত ইসি পুরোনো নিয়মেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
তার মানে নির্বাচনী ব্যবস্থাটি যদি সত্যিই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটি হতে হবে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। মানুষের মতামতের প্রতিফলন সেখানে থাকতে হবে। আর এ রকম একটি বিরাট সিদ্ধান্ত একটি অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার একটি অধ্যাদেশ বা প্রজ্ঞাপন দিয়ে চালু করে দেবে, এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কোনো একটি দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি হতে হবে সংসদে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কোনো একটি দল সংবিধান সংশোধন করে এ রকম একটি ব্যবস্থা চালু করে দেবে, সেটিও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সংসদে এটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে হবে। সংসদের বাইরেও নাগরিক সমাজের মতামত নিতে হবে। লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের মতামত নিতে হবে। সর্বোপরি গণভোট নিতে হবে এবং সেই গণভোট হতে হবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও রাষ্ট্রীয় প্রভাবমুক্ত। অর্থাৎ অতীতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যে তিনটি (১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৯১) গণভোট হয়েছে, তার সবই বিতর্কিত। সেগুলোর ফলাফল ছিল নির্ধারিত। সুতরাং বিতর্কিত গণভোটের মধ্য দিয়ে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তও জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।
