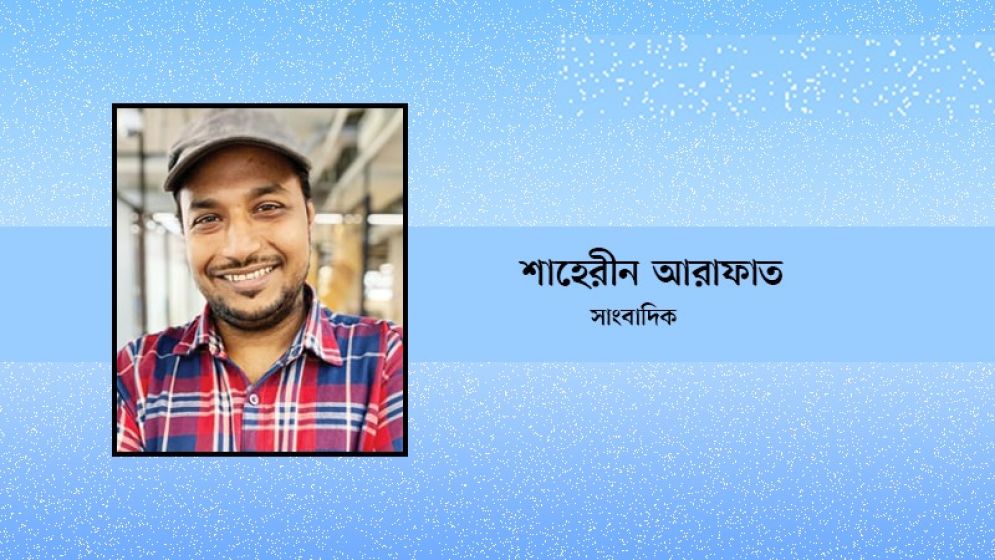
বছর ঘুরে আবার এসেছে ৫ আগস্ট। ২০২৪ সালের এই দিনে বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন একটি অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। শেখ হাসিনার দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান ঘটে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। এর পর থেকেই ‘জুলাই ঘোষণা’ দেওয়ার দাবি উঠতে থাকে। এদিকে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কয়েক মাস ধরে দফায় দফায় আলোচনার পরও বহু মৌলিক ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি। যে বিষয়গুলোতে আপাতদৃষ্টিতে ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো নিয়ে ‘জুলাই সনদ’ ঘোষণা করা হলেও বাস্তবায়নেও অনিশ্চয়তা রয়েছে।
মূলত, যে ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ আজকে সামনে এসেছে, তা প্রকৃতপক্ষে অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া জনগণের বৃহত্তর অংশকে উপেক্ষা করে, কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অর্জিত আপসমূলক সমঝোতা। এই সনদে জনগণের গাঠনিক ক্ষমতা ও সরাসরি অংশগ্রহণের কোনো প্রতিফলন নেই। বরং এটিকে ‘মৌলিক সংস্কার’ আখ্যা দেওয়া হলেও তা প্রকৃত অর্থে সংস্কারের নামে পুরোনো কাঠামোকে চালু রাখারই এক ছল।
সনদে স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দল ও প্রতিনিধিদের চরিত্র পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, এটি একটি পরিকল্পিত ‘এক্সিট প্ল্যান’-এর অংশ, যেখানে সরকার নিজেকে সুরক্ষিত রাখার পথ খুঁজেছে। ‘পটভূমি’ অংশে বলা হয়েছে, ‘জনগণের মননে রাষ্ট্রকাঠামো পুনর্গঠনের প্রবল অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়েছে।’ অথচ ৩ আগস্টে দেওয়া ঐতিহাসিক এক দফা ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিলÑহাসিনা সরকারের পতন ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপই একমাত্র লক্ষ্য। এই ঘোষণার কোনো উল্লেখ সনদে নেই। এই ফাঁক গলেই রাষ্ট্র সংস্কারের নামে তামাশা ঢোকানো হয়েছে।
সংসদীয় কমিটির চেয়ার বিতরণ
সনদে বলা হয়েছে, সরকারি হিসাব, অনুমিত হিসাব, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ অধিকারÑএই চারটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির সভাপতির দায়িত্ব বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের দেওয়া হবে। আসন সংখ্যার অনুপাতে অন্য কমিটিগুলোও তাদের দেওয়া হবে। এতে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ বাড়বে ঠিকই, কিন্তু কাঠামোগতভাবে কিছুই বদলাবে না। সংসদীয় সার্বভৌমত্ব, নির্বাহী প্রধানের ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যবস্থা বহাল রেখে বিরোধীদের হাতেই কিছু চাবি তুলে দেওয়া-এই সংস্কার মৌলিক তো নয়ই, বরং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার পুরোনো কৌশল।
সনদে আরো উল্লেখ রয়েছে-নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে সংস্কার, রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের বিধিতে সংশোধন, বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (বিভাগীয় হাইকোর্ট বেঞ্চ), উপজেলা পর্যায়ে নিম্ন আদালত স্থানান্তর, জরুরি অবস্থা জারির আগে মন্ত্রিসভার অনুমোদন, প্রধান বিচারপতি নিয়োগে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়তা, নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটির কথা। এই ছয়টি সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে। কিন্তু এসবই সীমিত প্রশাসনিক রদবদল-কোনোভাবেই মৌলিক রাষ্ট্র সংস্কার নয়।
একটি তুলনামূলক ভালো প্রস্তাব হলো-একজন ব্যক্তি একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দলপ্রধান হতে পারবেন না-এ বিষয়ে তিন-চতুর্থাংশ দল একমত। কিন্তু বিএনপি এতে সায় না দেওয়ায় এর বাস্তবায়ন নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থেকেই যায়। আরেকটি প্রস্তাব হলো-একজন ব্যক্তি তার সারা জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পুরোনো ফ্যাসিস্ট কাঠামো অক্ষত রেখে কেউ পাঁচ বছর থাকুক আর ১০ বছর, তাতে জনগণের জীবনে কিছুই বদলাবে না।
স্বাধীন পুলিশ কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অসম্পূর্ণ প্রস্তাব। পুলিশ প্রশাসন এখনো চলছে ১৮৬১ সালের ঔপনিবেশিক আইন ও ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ওপর ভিত্তি করে। এ ব্যবস্থায় জননিরাপত্তা নয়, বরং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণই মুখ্য। সুতরাং এসব আইনের সংস্কার ছাড়া পুলিশের কার্যক্রমে সত্যিকারের রূপান্তর সম্ভব নয়।
মুখে সংস্কার, কাজে ক্ষমতার রক্ষণাবেক্ষণ
জুলাই সনদের সব সংস্কার প্রস্তাবের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এগুলো মূলত ফ্যাসিবাদী-ঔপনিবেশিক-লুটেরা কাঠামো অক্ষত রেখে কিছু ‘চেক অ্যান্ড ব্যালান্স’ যোগ করার কায়দা। এমনকি নব্বইয়ের দশকের তিন জোটের রূপরেখাও এর তুলনায় অধিক পরিণত ও প্রগতিশীল ছিল।
এই সনদে থাকা উচিত ছিল, কীভাবে ফ্যাসিবাদী-ঔপনিবেশিক-মাফিয়া কাঠামো ভেঙে নতুন রাষ্ট্র গঠন করা যায়, তার একটি স্পষ্ট রূপরেখা। কিন্তু এখানে বলা হয়নি, এই সনদকে কীভাবে আইনগত ভিত্তি দিয়ে বাস্তবায়ন করা হবে।
গণভোট প্রশ্ন
সনদের ‘বাস্তবায়নের অঙ্গীকার’ অংশে বলা হয়েছে, নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার দুই বছরের মধ্যে সংস্কার বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলছে, সংসদের ওপর সংস্কার বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিলে তা মূলত সরকারি দলের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে পড়ে। আশির দশকের স্বৈরাচারবিরোধী তিন জোটের রূপরেখাও ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকারে এসে বাস্তবায়ন করেনি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও একই পথে হাঁটছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে না তুলে কেবল ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়-এই সহজ সত্যটিও রাজনৈতিক দলগুলো বুঝতে চায় না।
এ কারণে নির্বাচনের আগেই এই সনদকে বাস্তবায়নের জন্য গণভোটে পাঠানো জরুরি। জনগণের সরকার নির্বাচনের পাশাপাশি জনগণ নিজেরাই সনদের প্রতি মত দেবে-এই পদ্ধতিই গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ।
গণভোটের সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে-১. রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হওয়া সংস্কার প্রস্তাবগুলো আপনি সমর্থন করেন কি না? ২. দলগুলোর ঐকমত্য হওয়া এবং না হওয়া-সব সংস্কার প্রস্তাব আপনি সমর্থন করেন কি না? যে প্রস্তাবে সর্বাধিক সমর্থন আসবে, সেটিই হবে জনগণের অনুমোদিত জুলাই সনদ। আর এই গণরায় হবে সংসদ বা সরকারের ঊর্ধ্বে।
আগামী সংসদ সংস্কার করবে না; বরং গণরায়ে অনুমোদিত সংস্কার হবে সংসদের বৈধতার ভিত্তি। বর্তমান সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ আর দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অজুহাতে যে সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার অবসান ঘটিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করাই হবে প্রকৃত পরিবর্তনের পথ।
সংসদকে ‘সার্বভৌম’ ঘোষণা করেই বারবার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অভিজাতনির্ভর ও দলকেন্দ্রিক করে তোলা হয়েছে। জনগণ সেখানে কেবল ভোটদাতা, নীতিনির্ধারক নয়। ফলে ফ্যাসিস্ট সরকারপ্রধান চলে গেলেও ফ্যাসিস্ট কাঠামো টিকে থাকে।
যা থাকা দরকার ছিল
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল এক ঐতিহাসিক গণজাগরণ। কিন্তু তার পরও কাক্সিক্ষত কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেনি। বরং নানা উপদেষ্টা কমিটি, সংস্কার কমিশন ইত্যাদির মাধ্যমে অভিজাতগোষ্ঠী নিজেদের মতো করে সংস্কার চাপিয়ে দিতে চাইছে। অথচ এখানে থাকতে পারত গণ-অভিপ্রায়ের প্রতিধ্বনি, যা সংবিধানে নথিবদ্ধ থাকবে-
১. নতুন সংবিধান প্রণয়নের প্রস্তাব, যেখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিত হবে।
২. বিশেষ ক্ষমতা আইন ও নিবর্তনমূলক আইনগুলো বাতিলের ঘোষণা, যার ফলে বলপ্রয়োগনির্ভর রাষ্ট্রযন্ত্র বহাল থাকে।
৩. র্যাব, এনটিএমসি, ডিজিএফআইয়ের গণবিরোধী কর্মকাণ্ডে রাশ টানার প্রস্তাব।
৪. রাষ্ট্রযন্ত্র, নিরাপত্তা সংস্থা ও সামরিক গোয়েন্দা কাঠামোর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ।
৫. গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণভোট ও জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের প্রস্তাব।
৬. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, নাগরিক পরিষেবা, অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ার ঘোষণা।
রাজনৈতিক দলগুলো এরই মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সামাজিকমাধ্যমে সম্ভাব্য প্রার্থীদের পোস্টারও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জনগণ এখনো অপেক্ষায়তাদের অভিপ্রায় ও চেতনার প্রতিফলন কোথায়?
