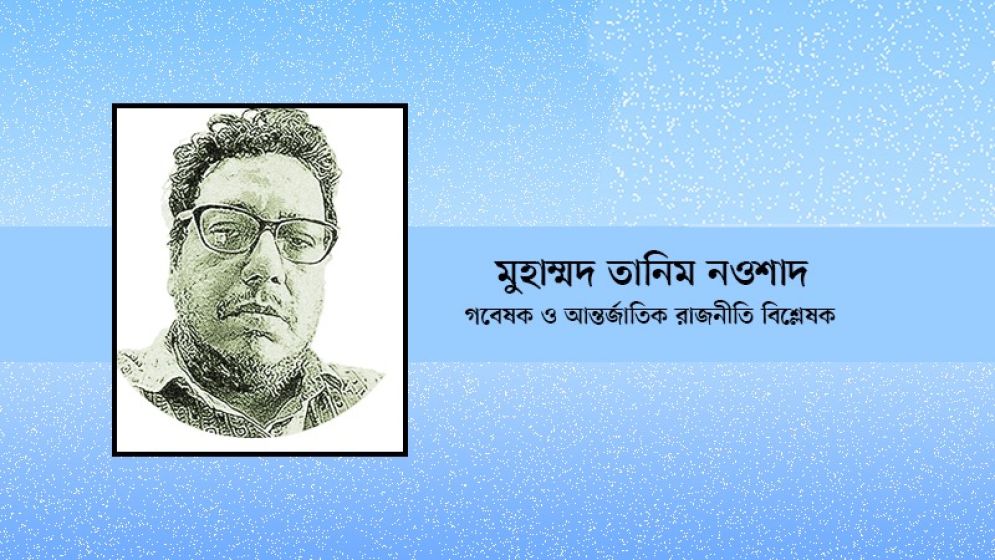
‘রাধা’ ও ‘রাধিকা’ নামের উৎপত্তি নিয়ে হিন্দু ধর্মে এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে নানা বিতর্ক রয়েছে। হিন্দু ধর্ম এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনেক পণ্ডিত এই নামের উৎপত্তি এবং এর ব্যুৎপত্তি বিভিন্নভাবে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন। তারা মূলত সংস্কৃত ভাষা, বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি এবং সংহিতা থেকে এই নামের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বলা বাহুল্য যে এই পুরাণ এবং সংহিতাগুলোও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। কিছু কিছু জায়গায় নামটির সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ গর্গ সংহিতার কথা বলা যায়। এর গোলক খণ্ডের ১৫তম অধ্যায়ে ঋষি গর্গ রাধা নামের সম্পূর্ণ অর্থ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ঋষি গর্গ এক গোপ দম্পতিকে বলেছিলেন, তিনি গন্ধমাদন পর্বতে নারায়ণের মুখ থেকে এই ব্যাখ্যাটি শুনেছেন, যা সামবেদের ভাবার্থ নির্দেশ করে। রাধা নামের র-কার এসেছে আদিগোপী রমা থেকে, যা আদতে দেবী লক্ষ্মী, ধ-কার অর্থ ধরা, আ-কার অর্থ বিরজা নদী, যাকে যমুনাও বলা হয়। বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে আমরা এর আরেকটি নাম পাই-‘কালিন্দী’। এই চারটি কার শ্রীকৃষ্ণের চারটি তেজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে; লীলা, ভূ, শ্রী ও বিরজা। আসলে এরা শ্রীকৃষ্ণের চার পত্নী। কুঞ্জমন্দিরে এরা সবাই রাধার মাঝে বিলীন হয়ে যান। তাই তিনি সম্পূর্ণা।
অন্যদিকে আমরা জানি, শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য থেকে বৈষ্ণব শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নিয়েছিলেন। এই দাক্ষিণাত্য ছিল প্রাচীন বৈষ্ণবদের একটি শাখা আলবারদের বাসস্থান। বৈষ্ণব ভজনসংগীত নিয়ে তাদের আবির্ভাবকাল খ্রিষ্টীয় পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন। শশীভূষণ দাসগুপ্ত তাই জানিয়েছেন তার বইতে (দাশগুপ্ত ২০১৫ : ১২১)। আর ক্ষুদিরাম দাস তাদের আবির্ভাব কাল দাক্ষিণাত্যে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বলে উল্লেখ করেছেন (দাস ২০০৯ : ১৫)। আলবারদের যে চার হাজার ভজন-সংগীত রয়েছে তা ‘দিব্য-প্রবন্ধম’ নামে প্রসিদ্ধ। অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিতেও কৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে লীলার বিবরণ আছে (দাস ২০০৯ : ১৫)। বলে রাখা ভালো যে, অনেকেই জানেন রাধা নাম ‘ভাগবত পুরাণে’ অনুপস্থিত। অনেকের মতে, রাধা গোপীদের মধ্যে কৃষ্ণের বিশেষ প্রণয়িনী এবং প্রধানা গোপী হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছেন মূলত জয়দেবের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ‘গীত-গোবিন্দের’ কল্যাণে। আলবারদের ভজন-সংগীতেও রাধার নাম নেই। এখানে আমরা তামিল গানগুলোতে রাধার জায়গায় যাকে পাই তার নাম ‘নাপ্পিন্নাই’, যা আদতে একটি ফুলের নাম। রাধা যেমন কৃষ্ণের নিকটাত্মীয়া, নাপ্পিন্নাইও তাই। আর নাপ্পিন্নাইও রাধার মতোই সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতিমা। তিনিও রাধার মতোই লক্ষ্মীর অবতার এবং এক গোপী, আর রাধাও তো গোপীই ছিলেন। জেএসএম হুপারের Hymns of the Alvars থেকে মহিলা কবি অন্ডালের একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম, যেখানে এই বক্তব্যগুলোর প্রতিফলন পাওয়া যাবে;
O Lady Nappinnai, with tender breasts
Like unto little cups, with lips of red
And slender waist, Lakshmi,
awake from sleep!
Proffer thy bridegroom fans and mirrors now,
And let us bathe! Ah,
Elorembavay!
(উদ্ধৃতি শশীভূষণ দাশগুপ্তের, বাংলা ১৩৯৬ সংস্করণ : ১২১-২২)
রাধা ও কৃষ্ণের লীলাভূমি গোকূলের মতোই ওই সমাজে নারীরা অনেক স্বাধীনতা ভোগ করতেন। নারীরা নিজেদের বর নিজেরাই পছন্দ করতেন। ‘বৃষ-বশীকরণ’ উৎসবে বীর পুরুষেরা ক্ষিপ্ত বৃষকে স্বহস্তে বশ করতেন, তাদের মধ্যে যে কন্যা যাকে পছন্দ করতেন তাকে নিজের বিয়ের মাল্য দান করতেন। আর গোপবালা নাপ্পিন্নাইও তার প্রেমিককে একই কায়দায় বরণ করেছিলেন (দাশগুপ্ত বাংলা ১৩৯৬ সংস্করণ :
১২২-১২৩)। প্রশ্ন হলো নাপ্পিন্নাই এর নাম রাধা হলো কী করে? আমার মতে, বঙ্গাঞ্চলে বা ওড়িশায় নাপ্পিন্নাই নামটি শুনতে কিছুটা খটোমটো। তাই হয়তো তাকে ডাকা হতো কৃষ্ণের প্রধান আরাধ্যা রূপে। কারণ অনেক বর্ণনায় আমরা পাই, ভগবান কৃষ্ণও রাধার আরাধনা করেন। কারণ কিছু ঐতিহ্যে তিনি বিশ্বজগতের মা। পরে সেখান থেকে আ উহ্য হয়ে গেছে, ধ-এর পরে উচ্চারণের সুবিধার্থে য-ফলা বাদ গেছে। আমরা জানি, কখনো কখনো কোনো এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় অনুপ্রবেশ করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বরবর্ণ উহ্য হয়। এটি এক ধরনের এলিসন বা বিলোপ। যারা ধ্বনিগত বিবর্তন এবং নৃ-ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন, তারা এর সঙ্গে বেশ পরিচিত। যেমন ইব্রাহীম নামটি আফ্রিকার তিউনিশিয়াসহ অনেক জায়গায় ‘ই’ বিয়োগে উচ্চারিত হয় ব্রাহীম। প্রাচীনকালের পারস্য সম্রাট আনুশিরভানকে ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে ডাকা হয় নুশিরভান নামে। ভারতবর্ষের আগড়ওয়াল পদবিটি অনেক জায়গায় গাড়ওয়াল নামে পরিচিত; যেমন-ভারতীয় অভিনেত্রী সিমি গাড়ওয়াল ইত্যাদি। যিশুর এক নাম ‘ইমানুয়েল’, যার অর্থ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে। পুরাতন নিয়মে যিশাইয় ৭:১৪ পদে দেখতে পাই নবী যিশাইয় (Isaiah) মশীহের নাম উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা প্রথমে এখানে একজন কুমারীর গর্ভে মশীহের (Messiah) জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাই। কিন্তু ইহুদি অনুবাদকরা এটিকে তরুণী অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে নতুন নিয়মে আমরা মথি ১:২৩ পদে নামটি আবারও পড়ি, যেখানে কুমারী মেরিয়ামের গর্ভে খ্রিষ্টের অদূর ভবিষ্যতে জন্মের কথা বলা হয়েছে। এই নাম আইবেরিয়ান উপদ্বীপে অর্থাৎ স্পেন ও পর্তুগালে উচ্চারিত হয় ‘মানুয়েল’। একইভাবেই কিন্তু আমরা কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তিকে বলছি হ্লাদিনী শক্তি। আর একইভাবে কৃষ্ণের প্রধান দয়িতা ও আরাধিকা (যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ কর্তৃক ভজিতা ও আরাধিতা) ‘আ’ বিয়োজনে হয়েছেন রাধিকা । আরাধিকা শব্দটি সংস্কৃত, হিন্দিসহ ভারতীয় নানা ভাষাতেই আছে। সংস্কৃত ও হিন্দিতে আরাধিকা অর্থ উপাসিকা। কিছু ওয়েবসাইট বলে যে আরাধিকা মানেও পুজিতা। অর্থ বুঝতে আমি দুটি ওয়েবসাইটের আশ্রয় নিয়েছি (নিচে দ্রষ্টব্য)। তবে এসব অবশ্য আমার অনুমান হলেও যুক্তিভিত্তিক অনুমান।
রাধার নাম যে, ‘রা’ ও ‘ধা’ এই দুই ধাতুর সন্ধি (রা+ধা) থেকে এসেছে, যেখানে ‘রা’ মানে ভক্তের ভক্তি বা মুক্তিপ্রাপ্তি আর ‘ধা’ মানে হরির দিকে ধাবিত হওয়া ইত্যাকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় (দাশগুপ্ত বাংলা ১৩৯৬ সংস্করণ : ১১৪), এগুলো আমার মতে, পরবর্তিকালের করা কষ্টকল্পিত অনুমান এবং ভক্তিবিলাসীদের কর্ম। আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে ক্ষুদিরাম দাসও একমত (দাস ২০০৯ : ৫২)। অন্যত্র শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলছেন যে, ‘রাধ্্’ ধাতু পরিচরণ বা সেবন অর্থে গৃহীত। আর আমরা মনে করি, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের দেহ-আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ সেবন। ‘রাধিত’ বা ‘আরাধিত’ বলতে বোঝায় পুষ্পের দ্বারা অলংকৃত বা অভ্যর্চিত। সেই একই অর্থে কৃষ্ণ রাধারূপ পুষ্পের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে অভ্যর্চিত (দাশগুপ্ত বাংলা ১৩৯৬ সংস্করণ : ১০৮-৯)।
রাধা নামের এই ব্যাখ্যাও বলা চলে স্বপ্নবিলাসীদের অতিবুদ্ধির ফল, এটিও কষ্ট করে ধর্মীয় সাযুজ্য বজায় রেখে একটি নামকে অর্থপ্রদ করার চেষ্টা। অন্যদিকে নাপ্পিন্নাইয়ের প্রেমিকের (পরে স্বামী) নাম ওই তামিল অঞ্চলে ছিল ‘মাল’ (Pattanaik 2007 : https://devdutt.com/articles/a-milkmaid-called-radha/) বা ‘মায়োন’ বা ‘মায়বন’ (ভাদুড়ী বাংলা ১৪২২ সংস্করণ : ৪৬), যে নাম ও সেই সঙ্গে নাপ্পিন্নাইয়ের নাম খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর তামিল মহাকাব্য শিলপ্পড়িকারমে বিবৃত আছে (Pattanaik 2007 : https://devdutt.com/articles/a-milkmaid-called-radha/)। আর এই মায়োন বা মায়বনও নাপ্পিন্নাইয়ের কাপড় আর গয়না চুড়ি করে নগ্না নাপ্পিন্নাইকে লজ্জিত করেছিলেন (ভাদুড়ী বাংলা ১৪২২ সংস্করণ : ৪৬)। এর সঙ্গে কৃষ্ণের গোপীদের বস্ত্রহরণের কাহিনির সাদৃশ্য আছে। ফলে দাক্ষিণাত্য থেকেই রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার কাহিনিটি এসেছে এ কথাটি হয়তো বলা অমূলক হবে না। দেবদূত পাটনায়েক লিখেছেন,“পঞ্চম শতাব্দীতে তামিল মহাকাব্য ‘শিলাপাডিকারাম’ একজন নাপ্পিনাইয়ের কথা উল্লেখ করে, যিনি মালের (কৃষ্ণের স্থানীয় নাম) প্রেয়সী ছিলেন। পণ্ডিতদের বিশ্বাস, তিনিই রাধার আদি রূপের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রিয়তমা এই গোয়ালিনীর ধারণাটি ধীরে ধীরে উত্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের লেখা সংস্কৃত কাব্য গীতা গোবিন্দের রচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, যেখানে গোপাল দেবতা এবং তার গোয়ালিনী প্রেমিকার আবেগ এমন একটি ভাষা এবং শৈলীতে উদযাপিত হয়, যা সমগ্র ভারতকে আলোড়িত করেছিল। (Pattanaik 2007)”
আর ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন যে, বৈষ্ণব শাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যে ‘ভাগবত পুরাণ’ তারও জন্ম দাক্ষিণাত্যেই (দাস ২০০৯ : ১৫)। ফলে দাক্ষিণাত্য থেকেই কৃষ্ণ ও গোপীদের প্রেমলীলা ও প্রণয়োপাখ্যানের আমদানি হয়েছিল এই অনুমানের শক্ত ভিত্তি তৈরি হয় এবং সেখান থেকেই পরে উত্তরে এই প্রেমকাহিনি বিস্তৃতি লাভ করে বলে অনুমিত হয়। রাধা নামটি প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম আমরা পাই খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা হাল সাতবাহনের ‘গাহা-সত্তসঈতে’ (ভাদুড়ী বাংলা ১৪২২ সংস্করণ : ১২৩)। এই গাহা-সত্তসঈকে সংস্কৃতে ডাকা হয় ‘গাথা সপ্তশতী’ নামে। যদিও Peter Khoroche I Herman Tieken-এর ইংরেজি অনুবাদ Poems on Life and Love in Ancient India : HālaÕs Sattasaī (Khoroche, Tieken 2009ed.) তে আমি রাধা নাম খুঁজে পাইনি।
গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র :
গর্গ সংহিতা (বাংলা, ১৯৩৩)। গোলোক খণ্ড, ১৫তম অধ্যায়, পঞ্চানন তর্করত্ন দ্বারা সম্পাদিত। বঙ্গবাসী ইলেকট্রিক মেশিন।
দাশগুপ্ত, শশীভূষণ (বাংলা ১৩৯৬ সংস্করণ)। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লি., কলকাতা। দাস, ড. ক্ষুদিরাম (২০০৯)। বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ. দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।
ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ (বাংলা ১৪২২ সংস্করণ)। মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
Khoroche, Peter, Tieken, Herman (2009 ed.). Poems on
Life and Love in Ancient India : HālaÕs Sattasaī. State University of New York
press.
