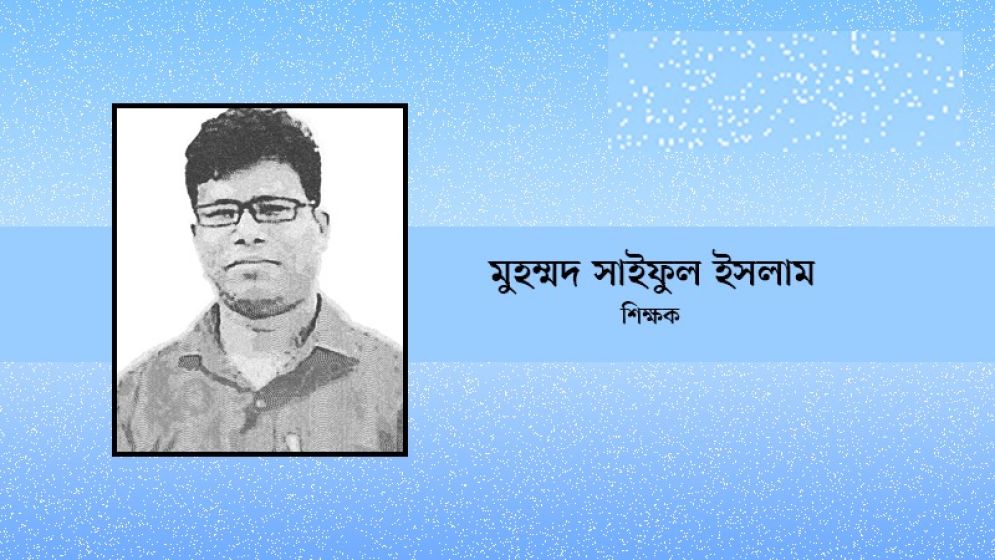
লেখকের কাজ কী? এ জিজ্ঞাসায় দার্শনিক আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) বলেন, একজন লেখক সমাজের অতন্দ্র প্রহরী, সামাজিক সংগ্রামে নিরত ব্যক্তি। তিনি আরো বলেন, ‘এই সংগ্রামে কর্মীর চেয়ে ভাবুক, রাষ্ট্রনেতার চেয়ে শিল্প রচয়িতার দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়। বস্তুতপক্ষে আরো বেশি, কারণ শিল্পী-সাহিত্যিকের মন হচ্ছে সমাজের সূক্ষ্মতম বীণাযন্ত্র। সামাজিক দুঃখের আওয়াজ সর্বাগ্রে ধ্বনিত হবে সেই বীণার তারে এবং তারই ঝংকারে সাড়া জাগবে দেশজোড়া মানুষের চিত্তে। দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথও তাকেই সবার আগে দেখতে হবে ও সবাইকে দেখাতে হবে।’ কী বলতে চেয়েছেন আইয়ুব? চিন্তাভাবনা করাটাই একজন লেখকের প্রধান কাজ। জীবনকে আবিষ্কার করাই তার স্বধর্ম। তবে একজন লেখকের একটি অসহায়ত্বের দিক বিবেচনাযোগ্য।
দুই
কোনো একজন লেখকের লেখা পড়ে কেউ মানুষ হয়েছেন কিংবা কোনো সমাজের বিরাট পরিবর্তন হয়েছে-এমন কথা শোনা যায়নি। বই প্রসঙ্গে যারা বড় বড় কথা বলেন, তাদের কথা কান পেতে শোনা যেতে পারে। কিন্তু যখন কেউ বলেন, ফরাসি বিপ্লবের মূলে ছিল রুশো-ভলতেয়ার, তখন বলতে হয়, এ হচ্ছে নিতান্ত পুঁথি পড়া লোক, মনুষ্যচরিত্র তাদের জানা নেই। ফরাসি বিপ্লবের মূলে ছিল বুরবোঁ শাসকশ্রেণির অত্যাচার, রুশো-ভলতেয়ারের গ্রন্থ নয়। আমেরিকার বিপ্লবের মূলে ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণির নৃশংসতা, রুশবিপ্লব জারের চরম নিগ্রহের ফল, মার্কসের তত্ত্ব নয়। শেকসপিয়র, গ্যেটে, তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ মানুষের চরিত্র পাল্টাতে পারেননি, অথচ লেখক হিসেবে পৃথিবীতে এরাই শ্রেষ্ঠ।
সক্রেটিসের কালে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কোলাহল কম ছিল না। তখনকার নাগরিকরা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে সেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মেতে উঠত। কিন্তু সেই অন্ধ মত্ততা সক্রেটিসকে স্পর্শ করেনি। নিজেকে তিনি অনায়াসে সেই মত্ততা থেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। কেননা রাজনীতি বিশ্লেষণে তার লেখকসত্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ন্যায়, সত্য ও বিবেকনিষ্ঠা। ন্যায়ের প্রশ্নে তার বিবেকী জিজ্ঞাসা ধারালো তরবারির মতো উঁচিয়ে থাকত। এই কারণে আজকের দিনেও আমরা অনেকে সক্রেটিসের চিন্তাভাবনার কথা বেশ গর্বের সঙ্গে বলতে পছন্দ করি, কিন্তু তার দীক্ষিত সংকল্পে ও নিয়তির কথা উচ্চারণ করলেও, নিজে গ্রহণ করি না। তিনি দীক্ষিত ছিলেন এক অমোঘ নিয়তিতন্ত্রে। তন্ত্রটা কী?
সত্য, ন্যায় ও বিবেক তার কাছে ছিল এক পরম নিয়তি। গভীর অধ্যয়ন ও মনননিষ্ঠা এই নিয়তির দ্বারা চালিত। প্রত্যেক লেখক-শিল্পীর জীবন-যাপনে,আচার-আচরণে, কথায় ও লেখায় এসবের প্রকাশ ঘটে চলে। সাধারণের সঙ্গে ওঠাবসায় আর চলাফেরায় তিনি বাধাহীন, কিন্তু আচরণে তার স্বাতন্ত্র্য হয়ে ওঠে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। সমাজ এই স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এমন ব্যক্তিত্ব সমাজের অলংকার।
তিন
আমরা আজ যে সমাজে বাস করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সেখানে এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লেখকের অভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। আমরা যে আজ সে রকম লেখকের সাক্ষাৎ পাই না, তার এক প্রধান কারণ, আমাদের পলিটিকস। আমাদের এই পলিটিকসের প্রধান কথা দলাদলি। এই দলীয় পলিটিকস যত ভয়ংকরই হোক, এর সঙ্গে যুক্ত না হলে আজ আর কারো পক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভের আশা নেই। জীবনে প্রতিষ্ঠার আকাক্সক্ষায় আমাদের লেখকরা আজ পলিটিকসের মাঠ গরম করছেন। এখানে আমাদের লেখকরা প্রায় সবাই কপালে তিলক কেটে, দলীয় পলিটিকসের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে, লম্বা টিকি নেড়ে, মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা বলে প্রচার করছেন! এ প্রচারে যিনি যত পারদর্শী, বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য, তিনি তত বেশি প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান, প্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদাবান!
দলীয় পলিটিকসের সঙ্গে মিল আছে ফেরিওয়ালার ব্যবসার। পণ্যের মেকিত্ব চাপা পড়ে যেমন-ফেরিওয়ালার মুখের মিষ্টি কথায়, তেমনি দলের নষ্টত্ব আড়াল করতে চায় দলের সঙ্গে যুক্ত এই পলিটিশিয়ান। একজন লেখক এই দুইয়ের সম্পূর্ণ উল্টো। তার কাজ ফেরিওয়ালারও নয়, দলীয় পলিটিশিয়ানেরও নয়। সাহিত্য এক হাটে কিনে অন্য হাটে বিক্রি করবার জিনিস নয়, সাহিত্যের ফসল নিজের মনের জমিতে ফলিয়ে তুলতে হয়। দলীয় পলিটিকসের সুবিধা এই যে, কারো কোনো চিন্তা করতে হয় না, সেখানে সবার সঙ্গে সবার একমত হওয়াই নিয়ম। কারো কোনো দ্বিমত থাকলে চলবে না। দলপ্রধান যা বলছেন, সেটাই মান্য, সেটাই বেদবাক্য। যিনি দ্বিমত করবেন তিনি দলদ্রোহী হবেন। এই ঝুঁকি জ্ঞানত কেউ গ্রহণ করেন না। কেননা সেখানে সবার স্বার্থ এক। দ্বিমত করলে তিনি যে ঘি-মাখনের জন্যে প্রলুব্ধ হয়ে এ রকম দলে স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছেন, তা থেকে বঞ্চিত হবেন। তখন জীবন ব্যর্থ হবে! অতএব, দলের কথাই শ্রেয় ও মান্য। চিন্তামুক্তির জন্ম এখানে।
চার
একজন লেখকও কি এই শ্রেণিভুক্ত হতে পারেন? মিথ্যা নয় যে, আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একটা বড় অংশ, যারা লেখক হিসেবে পরিচিত, এই চিন্তামুক্ত দলের অন্যতম কর্মী। এই সংখ্যা অল্প নয়। ধরা যাক, এই ঢাকা শহরের কথা। এখানে প্রতিদিন অজস্র সভা সমিতি আয়োজিত অসংখ্য বক্তৃতামালা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিটি সভায় থাকেন সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, একক বক্তা, মঞ্চে প্রচণ্ড ভিড়! সেখানে অনেক লেখক-শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী! তাদের বক্তৃতায় মঞ্চ কম্পিত হয়ে ওঠে! এসবের যোগফল কী? শূন্য! কেননা এখানে কেউ নিজের কথা প্রাণ খুলে বলেন না। সবই বলেন বানানো, ফেনানো, অন্যের বুলি ও পরিত্যক্ত কথা। নিজের কথা না বললে সারবান চিন্তার প্রকাশ হয় না। ফলে তাদের কথায় কারো হৃদয় স্পর্শ করে না। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে তা বেরিয়ে যায়! বিকৃত ও বিক্রয় করা মনের কথা অমৃত সমান, এমনটা কোথাও শোনা যায়নি। উনিশ শতকে অক্ষয় দত্ত-বঙ্কিম চন্দ্র আমাদের চিত্তশুদ্ধির কথা বলেছিলেন। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের নেতারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্বাধীন সমাজের কথা শোনাতে ভুল করেনি। আজ আর আমাদের কেউ তেমন কথা শোনাতে পারেন না।
ঠিক এই কারণে আমাদের সমকালের কোনো সমস্যাই আজ আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় না। এক ঢাকা শহর থেকেই দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক অগণিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এসব পত্রপত্রিকায় প্রতিদিনের বৈষয়িক মানুষের ঝগড়াঝাটি, মারামারি, কাটাকাটি, খুনোখুনি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, গুম, দুর্নীতি, ধর্ষণ সমেত একান্ত ব্যক্তিগত অন্ধস্বার্থের জন্যে হাজারো অপকর্মের সংবাদ ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না। আজ আমাদের সাহিত্যে আমাদের যুগধর্মের এই বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার ব্যাখ্যার দেখা মেলে না! আজ আমরা সবাই যেন নীতিধর্ষক, নৈতিক দৃষ্টান্তের প্রতীক নই। প্রত্যেক কালের মৌল সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন রকম। উনিশ শতকে কতগুলো সমস্যা দেখা যায়। সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা, পরাধীনতা, মধ্যবিত্তের সংকট প্রভৃতি। বিশ শতকের সমস্যা আরো অন্য রকম। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা, ফ্যাসিবাদ, আধুনিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি সমস্যা ওই দুই শতকের সাহিত্যে প্রত্যক্ষ। বিশ শতকের শেষে মৌলবাদ, বিশ্বায়ন, উত্তরাধুনিকতা, নয়া উপনিবেশবাদ প্রভৃতি আমাদের চিন্তাজগতে নতুন উপসর্গ হয়ে দেখা দেয়। এই ধারণাগুলো অবশ্য গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভৃতি মূল্যবান আদর্শ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সুচিন্তিত ধারণা দুর্লভ হয়ে উঠেছে।
পাঁচ
বস্তুত, আমরা সুচিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারি, দুশ্চিন্তা থেকে নয়। ফলে দুর্নীতির মতো অনির্বাণ মানসিক রোগ আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী। রোগজীর্ণ ও নষ্ট রাজনীতি এসবের প্রতিকারে অক্ষম। কারণ যেখানে পলিটিকস ফ্যাসিস্ট রূপ নেয়, সেখানে তার পরিণতি এমন হতে বাধ্য। আমাদের আজকের সাহিত্যে এসব সমস্যার কোনোরূপ প্রতিফলন নেই! ব্রিটিশ আমলে, এমনকি পাকিস্তানপর্বেও আমাদের সাহিত্যে যে মহৎ সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় নাটকে, কবিতায়, সংগীতে, উপন্যাসে, গল্পেÑএমন কি চিন্তাধর্মী লেখার মধ্যেও, স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য সে তুলনায় যেন মরা নদীর মতো নিষ্প্রাণ! আজ নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, কিন্তু গবেষণাপত্রগুলো পড়লে বোঝা যায়, এগুলো কেবল ডিগ্রির জন্যে, চাকরির জন্যে রচিত হয়েছে। সত্যের সন্ধান চোখে পড়ে না।
সমকালের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা যে সাহিত্যে নেই, তা চিরকালের সাহিত্য হতে পারে না। কালের প্রভাব ও প্রত্যয়ই সাহিত্যের আলোকিত প্রাণ। সমকালের প্রত্যয় ও ধারণা উপেক্ষা করে সাহিত্য ও গবেষণা কিছুই মূল্যবান হয় না। সমকাল একজন লেখকের মনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তারই সমুন্নত রূপ প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। এমন সাহিত্যে লেখকের চিন্তাভাবনা, সত্যনিষ্ঠা, গভীর অধ্যয়ন, অনুসন্ধিৎসা, উৎকণ্ঠা ও আবেগের যে বিস্তার থাকে, তাতেই আমরা লেখকের ব্যক্তিত্বের উত্তাপ অনুভব করি এবং তারই ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টি দিয়ে আমরা সমকালীন জগৎকে দেখতে পাই।
ছয়
আজকের বাংলাদেশে দেখা যায় লেখকেরা পুরস্কারের পেছনে ছুটছেন। টাকা ধরার জন্যে অন্ধ হয়ে নিজেকে বিক্রি করছেন। তারা কোনো কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্যে, কোনো কমিটির সদস্যের জন্যে, প্রতিষ্ঠানের প্রধান হওয়ার জন্যে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে কর্তার চরণতলায় লুটিয়ে পড়ছেন।
এই অল্প কিছু দিন আগেও একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পুরস্কার নিতে এসে আমাদের একজন সুপরিচিত কবি বললেন যে, তিনি পুরস্কারের জন্যে লেখেন! তার কথাটির প্রতিবাদ কিংবা সমালোচনা কেউ করেননি। এর থেকে বোঝা যায়, কথাটি তিনি ঠিকই বলেছেন। কেননা তার কথাটি ছিল একালের লেখক-সাহিত্যিকদের মনের কথা। তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই মনোভাবের লেখক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র। এটাই একালের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিণতি।
সাধারণভাবে দেখা যায়, সমাজে কার কত টাকা, কে কত বিত্তশালী, কার বাড়ি-গাড়ি কয়টা, কার মাসিক বেতন কত, বেতন বৃদ্ধির হার কত, মাসে উপরি আয় কী-রকম, কে কোন পদে চাকরি করেন, এসব হিসাব-নিকাশ দিয়েই মানুষের মূল্য নির্ণয় করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। লেখকও সামাজিক জীব। তাই কি সামাজিক পরিস্থিতির তিনি অনুগত? দার্শনিক ব্র্যাডলে না কি বলেছিলেন, মানুষ মানুষই নয়, যদি সে সামাজিক না হয়, তবে সে মানুষ পশুর চেয়ে খুব একটা ঊর্ধ্বে ওঠে না, যদি সামাজিকের চেয়ে বেশি কিছু না হয়।
মানুষের জীবনে অর্থলিপ্সা আসে কখন? যখন কোনো মহৎ আকাকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের বিলুপ্তি ঘটে। কোনো মহৎ আদর্শ না থাকার ফল অর্থলিপ্সা। এর থেকে আসে অহংকার। এই অহংকার মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাত্মক স্পৃহাকে দমন করে, এখানেই হিংসার জন্ম। লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক এখানে নির্বিকার ও নীরব কেন? এই নীরবতা কিসের লক্ষণ? সত্য যে, আর্থিক ভিত্তি ছাড়া আত্মিক ভিত্তি দাঁড়াবার পথ পায় না। কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু আজ আমরা আত্মিক বিকাশের জন্যে আর্থিকতাকে মূল্য দিই না, আত্মবিক্রয় করেই আর্থিকতার পেছনে মরিয়া হয়ে উঠছি!
সাত
একজন লেখকের সঙ্গে একজন পলিটিশিয়ানের সহযোগ কল্যাণকর হতে পারে, কিন্তু পলিটিশিয়ানের কাছে লেখকের আত্মবিলোপ আত্মঘাতী। আমরা কি এই আত্মঘাতী পথ বেছে নিয়েছি?
আকাঙ্ক্ষা মহৎ হলে জীবন সরল হয়ে আসে। সরল জীবনের প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই, তিনি আর যাই হোন, লেখক নন। সত্যের প্রকাশ আমরা সবার কাছে আশা করি না। এটা আশা করি একজন লেখক, শিল্পী ও সাহিত্য-স্রষ্টার কাছে। তাই একজন লেখকের দায় কেবল সত্যের কাছে, জীবনের সারল্য প্রতিষ্ঠার কাছে। এটাই একজন লেখকের নিয়তি।
