নির্লোভ, সাহসী ও প্রতিবাদী ছিলেন বদরুদ্দীন উমর
ড. মাহবুব উল্লাহ্
প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৪
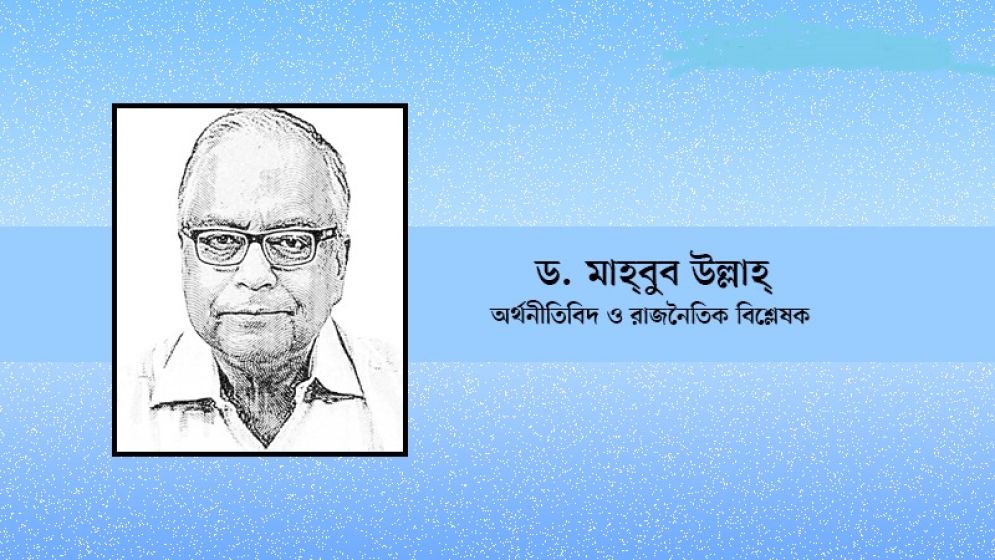
বাংলাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষী বদরুদ্দীন উমর ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা ৫ মিনিটে অনন্তলোকে যাত্রা করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। এদিক থেকে দেখলে, দেশের মানুষের গড় আয়ুর তুলনায় বেশি সময় তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন। তবুও আশা করেছিলাম, তিনি যেন শতায়ু হন। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় জ্ঞান ও মনীষায় আরো অবদান রাখতেন। মৃত্যু অবধি তার স্মৃতিশক্তি ও চিন্তা খুবই সক্রিয় ছিল। মস্তিষ্ক ছিল খুবই সজাগ। এমন একটি মানুষের অন্তর্ধানে দেশ ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। আকাশ থেকে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হলো।
বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। তখন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সে সময় কোনো একটি কাজে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে আমি এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের নেতা প্রয়াত মহিউদ্দীন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি কোনো রকম দ্বিমত পোষণ না করে আনন্দের সঙ্গে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সম্মেলনের দিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি পাকিস্তানের আইয়ুব সরকার, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার কঠোর সমালোচনা করলেন।
আমার ধারণা, এই ভাষণের মধ্য দিয়েই তিনি একজন বামপন্থি চিন্তানায়ক হিসেবে প্রথমবারের মতো আত্মপ্রকাশ করেন। তখনই জেনেছিলাম তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রয়াত আবুল হাশিমের সন্তান। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করা এই মানুষটির পূর্বপুরুষদের মধ্যে কয়েক পুরুষ জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষা-দীক্ষায় প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। বর্ধমানের গ্রামে কাটানো শৈশব-কৈশোরে অনেক নামিদামি বামপন্থি ও জাতীয় নেতাকে তাদের বাসভবনে দেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। খুব কম লোকেরই এরূপ সৌভাগ্য হয়।
এরপর বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময়। তখন গণ-অভ্যুত্থান অনেকটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হকের ওপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলেন, যাতে তিনি বদরুদ্দীন উমরকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য করেন। উপাচার্য শামসুল হক ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, সজ্জন ও অমায়িক মানুষ। মোনায়েম খানের চাপে তিনি ভয়ানক বিব্রত বোধ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত বদরুদ্দীন উমর তাকে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে পদত্যাগ করেন। ওই সময় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন। বদরুদ্দীন উমর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিপিই অনার্স ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। পিপিই মানে হলো পলিটিক্স, ফিলোসফি ও ইকোনমিক্সের অনার্স ডিগ্রি। এই ডিগ্রিটি অত্যন্ত সম্মানজনক।
১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের শেষ পর্যায়ে বদরুদ্দীন উমর সক্রিয় বামপন্থি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার লক্ষ্যে অন্য বামপন্থি নেতাদের সঙ্গে কথা বলার তাগিদ অনুভব করেন। ওই সময় চীনপন্থি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) জন্মের অল্প সময়ের মধ্যে ভাঙনের কবলে পড়ে। দেবেন সিকদার ও মতিন-আলাউদ্দিনরা এই পার্টি থেকে উপদলীয় চক্রান্ত করার দায়ে বহিষ্কৃত হন। তারা ভিন্ন একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির পরিচিতি হয়েছিল ‘পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি’ নামে। পার্টি ও নামের আগে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পূর্ব বাংলা যোগ করার ফলে একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এরা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।
বদরুদ্দীন উমর আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম রওনা হলেন। সেখানে তিনি আত্মগোপনরত কমিউনিস্ট নেতা দেবেন সিকদারের গোপন আস্তানায় তার সঙ্গে বৈঠক করেন। যতদূর মনে পড়ে বৈঠকটি হয়েছিল কাট্টলী গ্রামে, রাত ৯টা-১০টার দিকে। এই বৈঠকে আমিও উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু দেবেন সিকদার ও বদরুদ্দীন উমরের কথোপকথনে আমি অংশগ্রহণ করিনি। আমি ছিলাম নিছকই একজন স্রোতা। বৈঠকের একপর্যায়ে কমরেড দেবেন সিকদার বদরুদ্দীন উমরের উদ্দেশে তাচ্ছিল্যভরে উচ্চারণ করলেন, ‘আরে মিয়া’! বদরুদ্দীন উমর এতে বেশ বিরক্তবোধ করেন। বোঝা গেল, দেবেন সিকদারে বক্তব্যের প্রতি তিনি আস্থা রাখতে পারছেন না।
পরদিন তিনি চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের অফিসে জেলার বামপন্থি শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে গেলেন। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ছিল কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রিত অন্যতম শ্রমিক সংগঠন। এই সংগঠনে প্রকাশ্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড আবুল বাশার, কমরেড নিজামুদ্দিন, কমরেড মকবুল আহমদসহ আরো অনেকে। পার্টি সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন দেবেন সিকদার। সেদিন শ্রমিক ফেডারেশনের অফিসে বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে আমিও ছিলাম। শ্রমিক ফেডারেশনের অফিসে তখন জমজমাট অবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানের শাহীওয়ালে মওলানা ভাসানীর ওপর জামায়াতে ইসলামীর দৈহিক আক্রমণের বিরুদ্ধে হরতাল ও গণমিছিলের প্রস্তুতি চলছিল। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে শ্রমিক ফেডারেশন অফিসে টেলিফোন আসছিল। ফেডারেশনের অফিসটি জনসমাগমে গমগম করছিল।
পরদিন বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হলো মওলানা ভাসানীর ওপর হামলার প্রতিবাদে। এই মিছিলে অন্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন কৃষক নেতা বদিউল আলম। তিনি স্লোগান তুলে মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন। স্লোগান উঠল, ‘কৃষকের নয়ণ মনি-মওলানা ভাসানী’, ‘শ্রমিকের নয়ন মনি-মওলানা ভাসানী’, ‘আইয়ুবের আতঙ্ক-মওলানা ভাসানী’, জামায়াতের আতঙ্ক-মওলানা ভাসানী’, ‘আমেরিকার আতঙ্ক-মওলানা ভাসানী’, ‘এক মওদুদী-লাখো ইহুদি’। মিছিল খুবই সফল হলো। কিন্তু বদরুদ্দীন উমর শ্রমিক ফেডারেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পছন্দ করতে পারলেন না। তিনি আমাকে বললেন, ‘এখানকার শ্রমিক আন্দোলনে কোনো শৃঙ্খলা নেই, নেই কোনো চেইন অব কমান্ড।’ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ওপর রাজনীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে বিষয়টি নিছক অর্থনীতিবাদে আবদ্ধ থেকেছে।
এরপর বদরুদ্দীন উমরসহ আমি ঢাকায় ফিরে আসি। এ পর্যায়ে বদরুদ্দীন উমর কাদের সঙ্গে কি আলাপ করেছেন তা আমার জানার সুযোগ হয়নি। জানা গেল, তিনি কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা ও আব্দুল হকের নেতৃত্বাধীন মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তিনি এ পার্টির মুখপত্র ‘সাপ্তাহিক গণশক্তি’র সম্পাদক হিসেবে ১৯৭১-এর মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিকীটি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সাহিত্যে বামধারার শক্তিশালী সংযোজন ঘটায়। বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই পত্রিকাটি আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের অনন্য দলিল হয়ে আছে। বাংলাদেশোত্তরকালে গণশক্তি প্রকাশ্যে বের হলেও কয়েক সংখ্যার বেশি প্রকাশিত হতে পারেনি। সেই সময়কার আওয়ামী লীগ সরকারের দমননীতির ফলে বিশেষ করে শেখ ফজলুল হক মণির প্ররোচনায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সে সময় বদরুদ্দীন উমর এই পত্রিকার দায়িত্বে ছিলেন না। এক পর্যায়ে গণশক্তি গোপনে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ শুরু হয়। এর একটি সংখ্যা পড়ে জেনেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (এম-এল) সদস্য ও দরদিরা কীভাবে অকাতরে পাকিস্তানি সেনা ও রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন।
মুক্তিযুদ্ধের সময় বদরুদ্দীন উমর মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। তিনি যশোরে গিয়ে আব্দুল হকের অনুসারীদের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হক সাহেবরা তাকে সাফ জানিয়ে দেন তার দায়িত্ব গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। এরপর তার ইচ্ছা ছিল মোহাম্মদ তোয়াহার রামগতির এলাকায় যাওয়ার। মোহাম্মদ তোয়াহা সেখানে জনযুদ্ধ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তার পক্ষে মোহাম্মদ তোয়াহার এলাকায় যাওয়া সম্ভব হয়নি।
যশোরে কমিউনিস্ট নেতা নূর মোহাম্মদের লেখা থেকে জানা যায়, আব্দুল হক সাহেবের এলাকায় তার অনুসারীরা হিন্দু সংখ্যালঘুদের জীবন বাঁচানোর জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে অনেক লড়াই করেছেন। এ ছাড়া আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রিত মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতা করলেও তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং বন্দুকের নল আব্দুল হকের অনুসারীদের ওপর ঘুরিয়ে দেয়। এর আগেই পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার, কমরেড ত্বোয়াহা এবং কমরেড আব্দুল হকের মধ্যে ভাগাভাগী হয়ে যায়। কমরেড আব্দুল হক পরবর্তী সময়ে মাও জে দং-এর তিন বিশ্ব তত্ত্বের সমালোচনা করে আলবেনিয়ার পার্টি অব লেবারের নেতা আনভার হোক্সার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন।
বাংলাদেশোত্তরকালে বদরুদ্দীন উমর কমরেড অমল সেনের সঙ্গে কমিউনিস্ট ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগ বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। বদরুদ্দীন উমর এ পর্যায়ে লেখক শিবিরের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। তিনি প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগঠিত করার প্রয়াস নেন। তার এই প্রয়াস প্রশংসনীয় সফলতা অর্জন করেছে। তিনি মার্ক্সবাদী দর্শন তত্ত্ব ও রাজনীতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ‘সংস্কৃতি’র সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমৃত্যু। এই পত্রিকাটি বাংলাদেশে একটি উঁচুমানের সাময়িকী হিসেবে বোদ্ধাজনের স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৭২ সালে লেখক শিবিরের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অডিটরিয়ামে ‘বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির সমস্যা’ শিরোনামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে বদরুদ্দীন উমর, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, আহমদ ছফা ও চৌধুরী রফিকুল আবরারসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেন। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনিসুর রহমানও একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল ‘ধর্ম ও সমাজতন্ত্র’ প্রবন্ধটি বেশ বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। সেমিনারের পর পঠিত সব প্রবন্ধ নিয়ে ‘বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির সমস্যা’ শিরোনামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।
বদরুদ্দীন উমর তার সভাপতিত্বে গড়ে তোলেন ‘বাংলাদেশ মুক্তি কাউন্সিল’। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি মুক্তি কাউন্সিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ কথা সত্য যে, তিনি খুব বড় আকারের সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি। কমিউনিস্টদের এক ধরনের গোঁয়ারতুমির মধ্যেও বদরুদ্দীন উমর ছিলেন ভিন্নধর্মী কমিউনিস্ট। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি বাস্তববাদী। বিপ্লব নিয়ে আকাশকুসুম চিন্তাভাবনা তার ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন খাঁটি ও অকৃত্রিম বিপ্লবী। সত্য ভাষণে কখনো তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। সাহসী উচ্চারণের জন্য তিনি অনাদিকাল পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবেন। শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে তার দুঃসাহসী উচ্চারণ তাকে এ দেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে স্থান দেবে।
২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানের আগের মাসেই তিনি লিখেছিলেন, ‘আওয়ামী লীগকে পিটিয়ে উচ্ছেদ করতে হবে।’ আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের আমলে ক’জন এমন সাহসী উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন? কোনো প্রলোভন, পুরস্কার ও পদ-পদবির লোভে তিনি আদর্শচ্যুত হননি। পুরস্কার অনেক সময় হয়ে পড়ে ঊর্ধ্বতনদের প্রতি আনুগত্যের প্রতীক। সে কারণে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার এই প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ২০২৫ সালে তিনি স্বাধীনতা পদক প্রত্যাখ্যান করেন। এটা তার নীতি বোধের অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন ভদ্রতা ও শালীনতার সঙ্গে।
তিনি অগণিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এগুলোর সংখ্যা বিশাল। তার সেমিনাল গ্রন্থ হলো তিন খণ্ডে প্রকাশিত ‘পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’। এ ছাড়া লিখেছেন ‘সংস্কৃতির সংকট’, ‘সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা’, ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক’, ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ’ এবং ‘বাংলাদেশের মার্ক্সবাদ’, ‘বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন’সহ অনেক যুগান্তকারী গ্রন্থ।
মার্ক্সবাদী সাহিত্য রচনায় বদরুদ্দীন উমরের নিষ্ঠা ও অবদান অনন্য। তিনি বিরামহীনভাবে লিখে গেছেন। এর জন্য তাকে সীমাহীন পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং সেই পরিশ্রমের ক্ষমতা তার ছিল। টমাস কারলাইলের সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি একজন মহা প্রতিভাবান পুরুষ। একজন মার্ক্সবাদী সমাজচিন্তক, একজন ইতিহাসবিদ, একজন দার্শনিক এবং গণমানুষের জন্য সক্রিয়বাদী হিসেবে বদরুদ্দীন উমর প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
বদরুদ্দীন উমরকে পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবেও মানুষ শ্রদ্ধা করে। যে দেশে বুদ্ধিজীবীরা শতত বিপথগামী হয়, লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করে, শাসক-শোষকদের পদলেহন করে, সামান্য প্রাপ্তির জন্য আত্মমর্যাদা বিসর্জন করে, আত্মপ্রচারে নির্লজ্জভাবে লিপ্ত হয় এবং জীবনের পদে পদে প্রভুর অনুকম্পা কামনা করে, সে দেশে বদরুদ্দীন উমর একজন বিরল বিদ্রোহী। বদরুদ্দীন উমর সমকালীন ইতিহাসের একজন অধ্যাবসায়ী অনুসন্ধানী লেখক। তিনি বিরাগ বা অনুরাগের বসে ইতিহাসকে বিকৃত করেননি। তার সাহসী উচ্চারণ ছিল, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক-প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়নি। যেটা লেখা হয়েছে সেটা হলো সরকারি ভাষ্য, যা লেখা হয়েছে সেটা আশি থেকে নব্বই ভাগ মিথ্যা।’
বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে ১৯৪৭-কে মুছে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, ১৯৪৭-ও ছিল আমাদের মুক্তি সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বদরুদ্দীন উমর অনেক কথাই বলে গেছেন চর্চিত চিন্তাধারার ব্যতিক্রম হিসেবে। এই ব্যতিক্রমী পুরুষটিকে যুগের পর যুগ প্রতিবাদ ও সাহসের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করবে। মৃত্যুর মাঝেই তিনি অমর হয়েছেন।
