রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োজন
ড. মাহবুব হাসান
প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১১
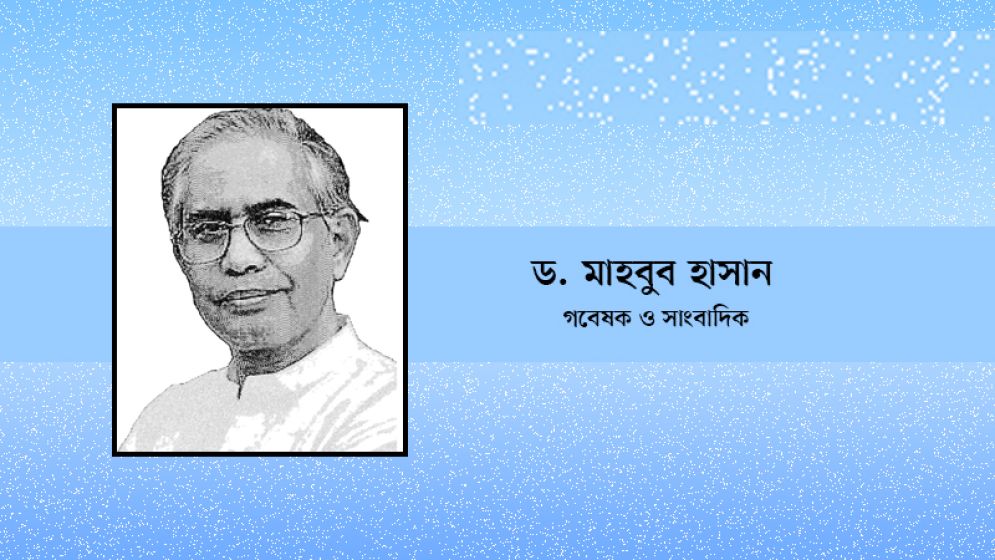
২৫ আগস্ট ২০২৫-কক্সবাজারে একটি বহুপক্ষীয় সম্মেলন হয়েছে আমাদের দেশে আশ্রিত মিয়ানমারের শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে। এ বছরের প্রথম দিকে, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে সঙ্গে নিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছিলেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এবারের বহুপক্ষীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য আসন্ন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এই বিষয়টিকে উপস্থাপন করা। লক্ষ্য পূরণে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন খুবই জরুরি ও কার্যকর। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিগুলোর মানবিক দৃষ্টি উন্মোচনের জন্য এ ধরনের সম্মেলন প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন বাংলাদেশের জনগণ উপলব্ধি করেছে এবং ড. ইউনূসও যে সেই জনগণের আকাক্সক্ষা পূরণে তৎপর তাও আমরা লক্ষ্য করেছি।
২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যে ঢল নামে বাংলাদেশের কক্সবাজার সীমান্তে, তাকে ফেরানোর চেয়ে রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে মানবিক দিক বিবেচনা করেই আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। আজও কোনো কোনো সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে ঢুকছে। এর মধ্যেই আবার ভারত কিছু রোহিঙ্গাকে পুশ ইন করেছে আমাদের দেশে। ভারত কেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় না দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে? তার কারণ নিহিত আছে ইন্দো-প্যাসিফিকের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। এই রাজনীতি ভূমি দখলের না, এই সংঘাতের পেছনে আছে সিভিলাইজড ইসলামের সঙ্গে বাকি বিশ্বের সাংস্কৃতিক সংঘাতের কল্পনা। যাকে আমি মিথিক্যাল অ্যালিগরি বলে চিত্রিত করি। ফলে আমাদের এই বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের জন্য মাত্রাতিরিক্ত ভারবাহী হয়ে পড়েছে রোহিঙ্গারা। আমাদের দেশটি ছোট, সম্পদ সীমিত, আমরা মানবিক দৃষ্টি দিয়ে আর কতকাল রোহিঙ্গাদের আশ্রিত রাখব? আবার আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও দেশ রোহিঙ্গাদের জন্য সহায়তা কমিয়ে দিয়েছে। এতে করে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে খাদ্যসংকট তীব্র আকার ধারণ করবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। এর সঙ্গে অনেক রোহিঙ্গা যুবক মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। গোটা পরিস্থিতি যে জটিল ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তা অনুমান করা কষ্টকর নয়। কিন্তু করণীয় কী?
এ নিয়ে দেশের সচেতন রাজনীতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তেমন কোনো দায় লক্ষ করা যাচ্ছে না। বর্তমান সরকার চাইছে অতি দ্রুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এর দায় ভার তুলে দিতে। কারণ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপ, আমাদের জীবনকে অনেকটাই দূষিত করে ফেলছে।
দুই
এবারকার সম্মেলনের শিরোনাম ছিল ‘স্টেকহোল্ডার্স ডায়ালগ : টেকওয়েজ টু দ্য হাইলেভেল কনফারেন্স অন রোহিঙ্গা সিচুয়েশন’। তিন দিনের এই সম্মেলনের অংশীজনরা কথা বলেছেন কীভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রাখাইনে প্রত্যাবাসন করা যায়। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাত দফা প্রত্যাবাসন পয়েন্ট উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, রোহিঙ্গা ক্রাইসিস সমাধানের দায়িত্ব কেবল বাংলাদেশের নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও। তাদের এই দায়িত্ব নিতে হবে।
আমরা মনে করি, বাংলাদেশ একা এই বার্ডেন বহন করবে কেন? যারা এই বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেই মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে, তাদের জনগণকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, না নিলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হবে তাদের ওপর রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ সৃষ্টি করা। কার্যকরভাবে সেই চাপ প্রয়োগ করা। বিশেষ করে এই সমস্যা সমাধানে ভালো ভূমিকা নিতে পারে চীন ও ভারত। তারা মিয়ানমারের প্রতিবেশী বড় ও শক্তিশালী দেশ। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বড় স্টেকহোল্ডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং গোটা ইউরোপ। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে উল্লিখিত দেশগুলোর ভূমিকা ছাড়া এর সত্যিকার স্থায়ী ও মানবিক রাখাইন প্রদেশ নির্মাণ করা যাবে না। তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে, সার্বিক অধিকার কায়েমের কোনো বিকল্প নেই।
অস্ত্রের জোরে অনেক অন্যায় করা যায়, তাতে সত্য লুকানো যায় না। শত শত বছর ধরে রোসাঙ্গের (আজকের রাখাইন প্রদেশ) ওই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভূমি। তাদের শেকড়চ্যুত করার পেছনে যে রাজনৈতিক হিংস্রতা আছে, বুড্ডিস্ট মিয়ানমারকে সেই মনোভঙ্গি পরিত্যাগ করতে হবে। ফিরে আসতে হবে বাস্তবে, সত্যে। আর সেটা জাতিসংঘের মাধ্যমেই হতে হবে, এটাই ভালো ও সুন্দর সমাধানের পথ। প্রফেসর ইউনূস যে সাতটি পয়েন্ট উপস্থাপন করেছেন, সেখানে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনই কেবল নয়, তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে মিয়ানমারকেই।
আমাদের দেশের তিনটি বড় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এতে করে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রাইসিস মোকাবিলায় জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তারাও এই সমস্যার সমাধানে সরকারের পাশে আছে।
তিন
তিন দিনের এই কনফারেন্সের একটি দিন ছিল আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের জন্য। তারা এই ক্রাইসিস সমাধানে তাদের মত প্রকাশ করেছেন। পথ দেখিয়েছেন যে, কারা এই সংকট থেকে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারে। জাতিসংঘের বিশেষ রেপোর্টিয়ার টম আড্রে স্থায়ী সমাধানের প্রধান অন্তরায় হিসেবে মিয়ানমারে অস্ত্র বিক্রিকে প্রধান প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন।
ইনভিজিবল ক্রাইসিসের ভেতরে বাস করছে আরেকটি ‘ইনভিজিবল ক্রাইসিস’ বলে মন্তব্য করেছেন টম আড্রে। এই যে অচিহ্নিত ও অচেনা অস্তিত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা যে রূপকার্থে তিনি বলেছেন, বোঝা যায়। তিনি সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া বা চীনের কথা বলেননি, কিন্তু মিনিংটা যায় সেই দিকেই। এই তিনটি রাষ্ট্র অস্ত্র উৎপাদক দেশ। এরা ছাড়াও ইউরোপিয়ান দেশগুলো অস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রির নেশায় আছে। মিয়ানমার কী করে সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে অস্ত্র কিনতে পারছে এবং সেই অস্ত্র কোন দেশ থেকে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে সিঙ্গাপুরে আসছে, বৈধ পথে নয় হয়তো, অবৈধ পথে, চোরাচালানের মাধ্যমে। সেখান থেকেই পাচার হচ্ছে মিয়ানমারের জান্তার কাছে। ওই সব অস্ত্রের জোরেই যে মিয়ানমারের সামরিক সরকার মুসলিম এথনিকদের উৎখাত করছে, আরাকান আর্মিসহ অনেক মুক্তিকামী উপজাতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, এই সত্য তো সহজেই বোঝা যায়। এ ব্যাপারে চীনের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। কারণ মিয়ানমার কেবল চীন থেকেই অর্থনৈতিক সহযোগিতা পায় না, চীনা অস্ত্রও যে তারা পাচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের পক্ষ থেকেও মিয়ানমার রাজনৈতিক ও সামরিক সাহস ও সহযোগিতা পাচ্ছে।
বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার বুদ্ধিজীবী কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশি প্রফেসর ড. ইশারফ হোসেন চিহ্নিত করেছেন চীনকেই। তিনি বলেছেন, চীন যদি রোহিঙ্গা ক্রাইসিস সমাধানে সক্রিয় হয়, তাহলে তাদের প্রত্যাবাসন সমস্যাটির সমাধান হবে। আন্তর্জাতিক সহযোতিার মাধ্যমে চীন এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে পারে।
তবে তার জন্য চাই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের পথ বের করতে চীনের মননগত সদিচ্ছা। তারা স্বীকার করুন আর নাই করুন, চীনা খুঁটির জোরেই মিয়ানমার মুসলিম রোহিঙ্গাদের বাস্তুচ্যুত করতে উৎসাহ পায়। দ্বিতীয়ত, মানসিকভাবে চীন, মিয়ানমার ও ভারত চায় বাংলাদেশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক গ্যাঁড়াকলে ফেলে সুবিধা আদায় করে নিতে। মুসলমানদের ওপর যে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখার অপপ্রয়াস চীনা সরকারের, তা কিন্তু কারো অজানা নয়। তৃতীয়ত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই বাংলাদেশেই কেবল উন্নত উর্বর ভূমির অধিকারী নয়, স্ট্র্যাটেজিক কারণেও বিশ্বের ক্ষমতাবানদের দৃষ্টি এখানে নিবদ্ধ। বড় সামরিক দিক থেকে বলিয়ান দেশগুলো পৃথিবীর ভূমিজ ও খনিজ সম্পদ ভোগের যে দখলদারির লোভ, তার কারণেই আসল বিরোধ। এই বিরোধের কেন্দ্রে পড়েছে বাংলাদেশ।
রোহিঙ্গা প্রতিনিধি কিন মঙ আবেদন জানিয়ে বলেছেন, এই পরিস্থিতিতে আমরা বেশিদিন বাঁচতে পারব না। আমরা চাই ফিরে যেতে আমাদের জন্মভূমিতে। তবে সেই জন্মগত অধিকার, ডিগনিটি এবং জাস্টিস দিলেই কেবল ফিরে যেতে পারব। গণহত্যার বিষয়ে অবশ্যই মিয়ানমারের জান্তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তার এই আবেদন তো সর্বজনীন। কারণ পৃথিবীর মানবিক মানুষেরা চায় কোনো রকম যুদ্ধ, হানাহানি এথনিক ক্লিনজিং নামক হত্যাযজ্ঞ যেন আর না ঘটে কোথাও। কিন্তু অস্ত্র উৎপাদক আর রাষ্ট্রশক্তি কি সেই মনোভাব পোষণ করে? করে না বলেই গাজা শহর ধ্বংস করছে জায়নবাদী ইহুদি সরকার। মানুষ হত্যার এই যে হিংস্রতা, তার পেছনে আছে মুসলিম বিশ্বের ওপর তাদের পরিকল্পনার নকশা কীভাবে পরিচালিত হবে, তারই রোডম্যাপ। আমরা যেমন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের একটি বাস্তব ও কার্যকর রোডম্যাপ চাই, যে কথা ড. ইশারফ হোসেন বলেছেন, বলেছেন অপরাপর আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডার, তেমনি আমরাও চাই নাগরিক অধিকার নিয়ে, নিরাপত্তার বেষ্টনীসহ খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও সার্বিক অধিকারভুক্ত হোক রোহিঙ্গাদের সামাজিক জীবনযাপন।
এ ব্যাপারে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ যেমন ভূমিকা রাখতে পারে, তেমনি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাও রাখতে পারে। অন্তত মানবিক এই প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা কোনো রকম ভেটো না দিয়ে মিয়ানমারের জান্তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। জাতিসংঘের আসন্ন অধিবেশনেই রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের রোডম্যাপটি আঁকা হোক, এটাই আমরা চাই।
