ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকেন্দ্রিক সংকট উত্তরণের পথ অনুসন্ধান
সাইফুল হক
প্রকাশ: ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫১
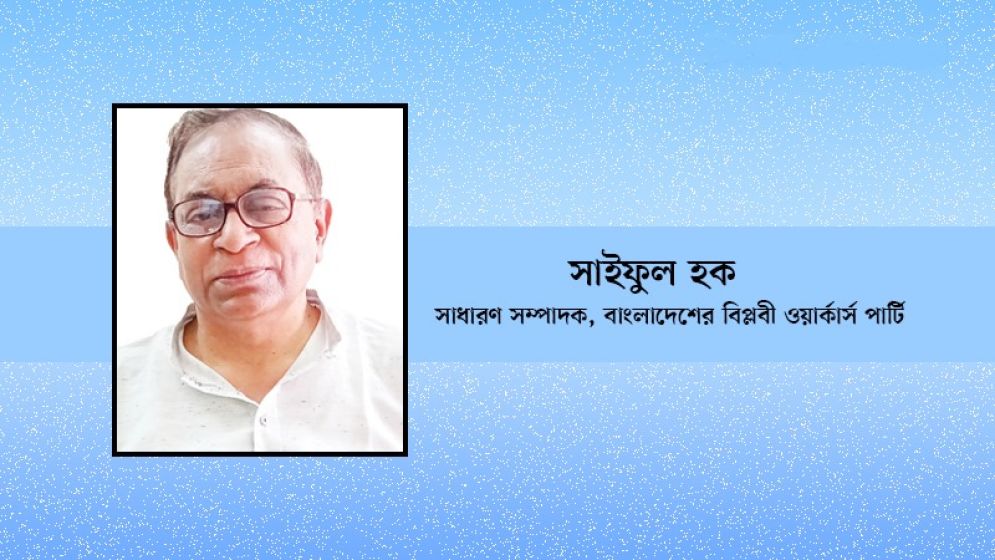
এই মুহূর্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খানিকটা জটিল। তবে মেঘ কেটে যাওয়ারও লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে-এমন একটি সম্ভাব্য ধারণা সরকারের তরফ থেকে পাওয়া গেছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশন সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে রাজনীতির মাঠে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা সমীকরণ ও মেরুকরণ সামনে আসছে। নির্বাচনের বিষয়ে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল নিজেদের শর্ত জুড়ে দিচ্ছে। এতে করে নির্বাচন নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হবে কিনা, এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারকে কোনো দোলাচলে ভুগলে চলবে না। দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই কর্মযজ্ঞের স্বচ্ছতা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। কোনো বিষয়ে শক্ত অবস্থান নেওয়ার প্রয়োজন পড়লে সরকারকে তা নিতে হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সংসদ নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে গণভোট আয়োজনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো মতৈক্যের প্রায় কাছাকাছি। তবে কিছু বিষয় নিয়েই মূলত সংশয় ও সংকট ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল গণপরিষদের বিষয়ে প্রায় অনড় অবস্থানে ছিল। একটি দেশে গণপরিষদ নির্বাচন তখনই হয় যখন সে দেশটির কোনো সংবিধান থাকে না। সংবিধান তৈরি করতেই মূলত গণপরিষদ নির্বাচন। কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে তো একটা সংবিধান রয়েছে। শত সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা এই সংবিধানের অধীনে রয়েছি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও প্রায় ১৪ মাস এই সংবিধানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে গণপরিষদ নির্বাচনের কোনো প্রয়োজনীয়তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল কিছুদিন আগে প্রস্তাব করেছিল, ‘সাংবিধানিক অর্ডার’-এর মাধ্যমে জুলাই সনদকে কার্যকর করার। আমরা বলেছি, কোনো সাংবিধানিক অর্ডার কিংবা নির্বাহী আদেশে জুলাই সনদ কার্যকর করাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। সংবিধান সংশোধনের একমাত্র ক্ষমতা রাখে সংসদ এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংসদ। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে বিপজ্জনক। ভবিষ্যতে দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বাঁক বদলের সময় এই অধ্যাদেশকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে। তাই এ বিষয়টি আমরা সমর্থন করতে পারি না। তা ছাড়া সংবিধান সংস্কারে এ ধরনের কোনো সাংবিধানিক আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ও এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। এটা করতে গেলে সরকার নিজেই অনেক অপ্রয়োজনীয় সাংবিধানিক বিতর্ক আনবে। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক দলগুলো যখন জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করবে, তখন আসলে নির্বাচনের পর সংসদে এটাকে সাংবিধানিক ভিত্তি দেওয়াই সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক ও নৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।
নির্বাচন সামনে রেখে পিআর পদ্ধতির দাবিতে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী ঘরানার কিছু দল সভা-সমাবেশ ও মিছিল করছে। পিআর পদ্ধতি ছাড়াও তাদের আরেকটি দাবি রয়েছে। সেটি হলো, নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদের বাস্তবায়ন। বাস্তবে পার্লামেন্টকে এড়িয়ে এমন কিছু করার সুযোগ নেই, যা করার নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই করবেন। যারা রাজনীতি করছেন তাদের সবারই এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার। পিআরের বিষয়টি খুবই বিভ্রান্তিকর। নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতির বিষয়টি ঐকমত্য কমিশনের এজেন্ডাতেই নেই। ফলে পিআরের দাবির যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। উচ্চকক্ষে পিআরের বিষয়ে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টিসহ ২৬টি রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে। নোট অব ডিসেন্টসহ ঐকমত্য কমিশনে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে।
আমরা বহু বছর ধরে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের কথা বলে আসছি সত্য। তবে আমাদের প্রক্রিয়া ভিন্ন। আমরা বলেছি, এটা ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করার বিষয়। প্রথমে উচ্চকক্ষ ও স্থানীয় নির্বাচন দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু জামায়াতসহ ইসলামি ঘরানার দলগুলো সরাসরি জাতীয় পর্যায়ে পিআর চাইছে। আমরা এটার পক্ষে নই। আমার মনে হয়, এটা তাদের নির্বাচনী কৌশল। বলার জন্যই বলা। অথবা সরকারকে চাপে রাখা বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটা কৌশল হতে পারে।
জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ তা হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে পুরোপুরি সক্রিয় করা। তারা এখনো পুরোপুরি সক্রিয় দায়িত্ব পালন করছে না। চাকরি বাঁচাতে যতটুকু দরকার ততটুকুই করছে। এই পুলিশ বাহিনী দিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তালিকায় সেনাবাহিনীকে যুক্ত করেছে। পুলিশ যদি নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে সেনাবাহিনী কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তাও ভাবার বিষয়।
আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারছে না, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। নির্বাচন কমিশন তাদের প্রতীক সরিয়ে ফেলেছে। দল হিসেবে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। একটা প্রশ্ন আসছে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সমর্থক ও ভোটারদের কি হবে? তাদের কাছে তো কোনো অপশন নেই। এই প্রশ্নের মীমাংসা কী? ভোটারদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে বাইরে রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে অদূর ভবিষ্যতে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠবে যে, এই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলো কিনা, এর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন হবে। ভবিষ্যতে এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না।
অন্তর্বর্তী সরকার দল নিরপেক্ষ হওয়ার কথা। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই দেখতে পাচ্ছি ছাত্র তরুণদের দলটির প্রতি তাদের এক ধরনের পক্ষপাত রয়েছে। বলতে গেলে সরকার এই দলটিকে কোলে পিঠে করে বড় করছে। ছাত্র প্রতিনিধিরা এখনো সরকারে রয়েছে। তারা যদি পদ থেকে সরে যায় তবুও তাদের প্রতি সরকারের একটা পক্ষপাতমূলক ভূমিকা থাকতেও পারে। অন্য কিছু দলের প্রতিও তাদের পক্ষপাতদুষ্টতা দেখা যাচ্ছে। নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করছে সরকারের ওপর। সরকারের উচিত রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থার জায়গাটি নিশ্চিত করা। সরকার যদি এটা নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে মানুষের মধ্য থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবি উঠতে পারে। তখন পরিস্থিতি জটিলতর হতে পারে। তাই সরকারের উচিত নিজের আস্থার জায়গাটি নিশ্চিত করা।
এদিকে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর জামানত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে নির্বাচনে কালো টাকার ছড়াছড়ি ঠেকানোর লক্ষ্যে কোনো রূপরেখা দেয়নি। কালো টাকা আটকানোর ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন যদি কোনো পদক্ষেপ না নেয় তবে পূর্বের নির্বাচনগুলোর মতোই একই ঘটনা ঘটবে। অর্থাৎ অতীতে যেমন ধনী ও কালো টাকার মালিকরা সংসদে গেছেন এবারও তাই হতে পারে। ঝুঁকিটা কিন্তু রয়েছে। নানামাত্রিক সংকটে নির্বাচন যদি পিছিয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশ বহুমাত্রিক ঝুঁকির মুখে পড়বে। সরকারের টিকে থাকাও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। মানুষ মূলত নির্বাচনের জন্যই অপেক্ষা করছে। মানুষ ভাবছে, এই সরকার তো অনেক দিন পর এমনিই চলে যাবে। কোন কারণে নির্বাচন পিছিয়ে গেলে মানুষের ভাবনারও পরিবর্তন ঘটবে।
এই মুহূর্তে দেশে একটি আধা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কথায় কথায় মাজারে হামলা হচ্ছে, লাশ তুলে পোড়ানো হচ্ছে, মানুষের ধরে চুল কেটে দেওয়া হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবাই নৈরাজ্যের একটা লাইসেন্স পেয়ে গেছে। নির্বাচন পিছিয়ে গেলে এই সংকটগুলো আরো বাড়বে। পরিস্থিতি যদি এমন চলতে থাকে তাহলে অভ্যুত্থানে অংশীজনদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হবে।
ফলে ফ্যাসিবাদী শক্তির ফিরে আসাটা সহজ হয়ে যাবে। এমনিতেই বাংলাদেশ গভীর এক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। একদিকে রোহিঙ্গা সংকট, অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট, সব মিলিয়ে দেশের নিরাপত্তার ঝুঁকি বহুমাত্রিক। বাংলাদেশের তিন দিক দিয়ে ভারতে ‘পুশ ইন’ করছে, এটা একটি বার্তা। এটি এমন ‘আমরা তোমাদের সরকারকে ভালোভাবে নিচ্ছি না।’
এত সব সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার আপাতত উপায় হলো নির্বাচন। জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল একটি সরকার এসব সমস্যার কিছুটা নিদান দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। নির্বাচন হলেই যে আমরা কোনো একটি স্বর্গরাজ্যে চলে যাব বিষয়টি এমন নয়। একটু আশা করা যায় যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং আমরা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাব, এই হলো বিষয়। অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি সরকার পরিবর্তনের ধারা ফিরে আসবে। এখন এইটুকুই অনেক বড় সফলতা। বর্তমানে দক্ষিণপন্থি শক্তির একটা উত্থান দেখা যাচ্ছে। এটা আরেক ধরনের ফ্যাসিবাদের জন্ম দিতে পারে। এই দক্ষিণপন্থা প্রতিরোধেও নির্বাচন, নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা গতিশীল করা প্রয়োজন।
রাজনীতি ও নির্বাচনের এই ডামাডোলে অর্থনীতির দিকে আমাদের নজর ঠিকঠাক যাচ্ছে না। ৩০ থেকে ৪০ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে এসেছে, গত এক বছরে বেকারত্ব আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে, বেড়েছে না খাওয়া মানুষের সংখ্যা, প্রকৃত আয় কমেছে অসংখ্য মানুষের। কর্ম সংস্থান ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি শোচনীয়।
এসব কিছু রাষ্ট্র ও সমাজে বড় বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। এটা ভবিষ্যতে বড় সংকট আকারে দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতিকে যদি আমরা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে মোকাবিলা করতে না পারি, তাহলে আমরা আফ্রিকার দেশগুলোর মতো একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারি। সেই আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যায়। এ রকমটা আমরা চাই না। আমরা চাই দেশের রাজনীতিবিদরা দূরদর্শিতার পরিচয় দেবেন, কিছুটা প্রজ্ঞার পরিচয় দেবেন। বাংলাদেশকে কোনোভাবেই ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে দেবেন না।
অনুলিখন : বখতিয়ার আবিদ চৌধুরী
