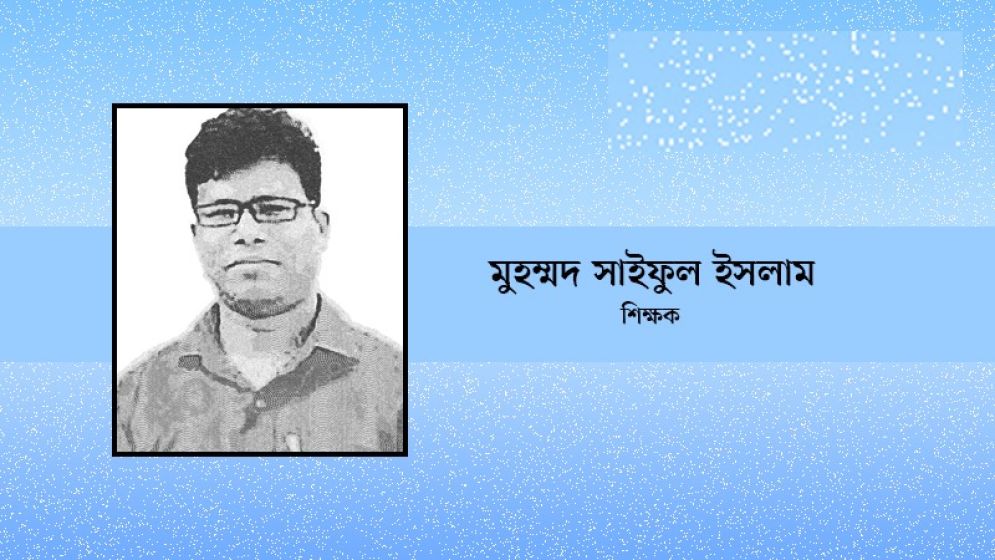
আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) একজন অনন্যসাধারণ মানবতাবাদী সাহিত্যিক, ভাবুক ও চিন্তাবিদ। তিনি নিছক বুুদ্ধিবৃত্তির মানুষ ছিলেন না-যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান-বুদ্ধি, সংস্কারমুক্ততা ও ধর্মপ্রভাব-মুক্তি তার স্বকীয় ভাবুকতাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল, আমাদের মানসিকভাবে দরিদ্র সমাজে। নিজের জীবন দিয়ে তিনি যে সত্য আমাদের শেখাতে চেয়েছিলেন তার পূর্ব দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রম। বুঝিয়ে বলা যাক কথাটি।
অতি বড় বিখ্যাত ব্যক্তিদেরও, কথায় ও কাজে গরমিল দেখলে, লোকে তাদের প্রতারক ও প্রবঞ্চক বলতে দ্বিধা করে না। এই স্তরে আছেন সাহিত্যিক, রাজনীতিক, চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও। দিন শেষে এদের চিন্তা ও কর্ম আমাদের অনুপ্রাণিত করবে কি না, বলা কঠিন। অশিক্ষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক অবস্থান বর্ণগত, সম্প্রদায়গত ও ভেদবুদ্ধি সমাচ্ছন্ন হতে পারে এবং তাদের মনের ওপর গোঁড়ামি, কুসংস্কারের প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যদি দুই নৌকায় পা দিয়ে চলেন, তবে তাদের সম্পর্কে উল্লিখিত শব্দ দুটির প্রয়োগ দেখা যায়! চিন্তার পরিচ্ছন্নতায় এবং ব্যক্তিজীবনে আবদুল হক ছিলেন এই অন্ধকার থেকে মুক্ত মানুষ। তিনি বিশ্বাসে ও মননে সৃষ্টিধর্মী ও গণতন্ত্রী। তিনি নিজের স্বরূপের কথায় বলেছিলেন, ‘সুখী জীবনের অর্থ শুধু আর্থিকভাবে সচ্ছল জীবন নয়, সূক্ষ্ম সুন্দর অনুভূতিময় মানসিক জীবনও। এই দুইয়ের সম্মিলন সব সময় সম্ভব নয় এবং এই দুইয়ের মধ্যে যেকোনো একটিকে যদি বেছে নিতে হয় তবে সূক্ষ্ম সুন্দর অনুভূতিময় আলোকময় নির্মল প্রশান্ত জীবনই আমি বেছে নেব। আর এই জীবনেরই সাধনা করেছি আমি আজীবন।’ তিনি এক বর্ণও মিথ্যা বলেননি, এখানে! এই কারণে তিনি অনন্য। ব্যতিক্রমও।
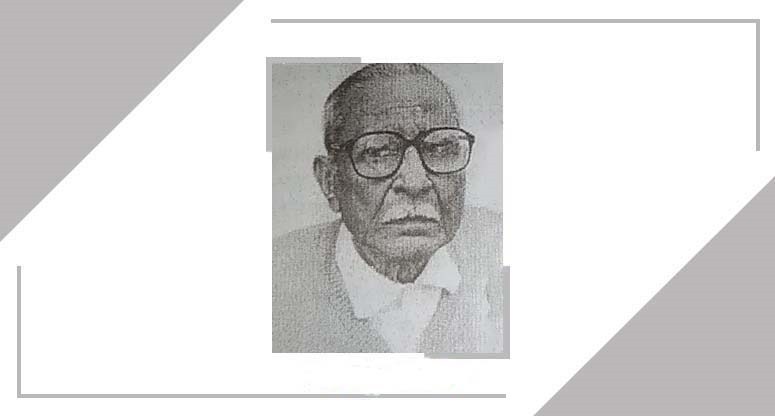 আবদুল হক
আবদুল হক
দুই
তিনি জন্মেছিলেন এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে-রাজশাহী বিভাগের নওয়াবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলায়। পিতা সহিমুদ্দিন বিশ্বাস, মা সায়েমা খাতুন। এগারো ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তৃতীয় শ্রেণি পেয়ে এমএ পাস করেন। অনন্যসাধারণ মানসিক শক্তি না থাকলে তিনি যে আর্থিক অবস্থার মধ্যে জন্মেছিলেন, সেটাকে অতিক্রম করে, অন্য কৃতিত্ব দূরে থাক, লৌকিক সাফল্যও লাভ করতে পারতেন না!
বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ‘বাঙালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙালীর বশীভূত হয় না।’-আবদুল হক নিজের শক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন, এই বাস্তব চিরন্তন নয়! তিনি অর্থের জন্যে, ভয়ে কিংবা প্রলোভনে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেননি। আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আত্মবিকাশ হয় না-এটা তিনি জানতেন। কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার অর্থ কেবল আর্থিক উন্নতি নয়, মূল্যবোধ-সূক্ষ্ম চেতনারও উন্নতি। যেখানে কেবল আর্থিক উন্নতি আছে, আত্মবিকাশ নেই, মনের স্ফুরণ নেই, মানবিক সূক্ষ্ম অনুভূতির বিকাশ নেই, তিনি তেমন আত্মপ্রতিষ্ঠা চাননি। তেমন প্রতিষ্ঠায় তিনি অনীহ ছিলেন। বাঙালি মুসলিম সমাজে এই চরিত্র দুর্লভ।
তিন
আবদুল হকের কর্মে ও চিন্তায় রাজনীতি ছিল। তিনি জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করতেন এবং সে বিশ্বাসে, ‘জাতীয়তাবাদের অর্থ সমগ্র জাতির কোনো লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের সকল অধিবাসীর একাত্মতাবোধ।’ কোনো জাতি কিংবা রাষ্ট্র যখন গড়ে উঠতে চায়, তখন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বহুবিধ হতে পারে। স্বাধীনতা ছাড়াও গণতন্ত্র, মানবিক মর্যাদা কিংবা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কাম্য হতে পারে। তিনি এ জন্যে বলেছেন, ‘দেশপ্রেম ব্যতীত দেশের শুধু উন্নতি নয়, অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। দেশপ্রেমের প্রকৃত অর্থ কিন্তু সেই দেশের মানুষের প্রতি প্রেম।’ মিথ্যা নয় যে, এই মূল্যবোধ গভীরভাবে অর্থবহ, প্রত্যয়দীপ্ত।
তিনি এগিয়ে গেলেন আরো আধুনিক অগ্রগতির লক্ষ্যে। একটা জাতির ভেতর বহু শ্রেণি-পেশা, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বাস। সেখানে গণতান্ত্রিক মনোভাব ও ধর্মনিরপেক্ষতা জরুরি। ইতিহাস আমাদের এই মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়, তিনি মনে করতেন। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র কথা এসেছে এই ভাব থেকে। ইতিহাসে দেখা যায়, ‘ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনেকটাই পশ্চাদমুখী এবং স্বপ্নাতুর থাকে, কেননা ধর্মের অনেকটাই স্বপ্ন দিয়ে গড়া। কিন্তু রাজনীতিক এই স্বপ্নকে রাজনৈতিক কারণে কূটনৈতিক কৌশলে ব্যবহার করে থাকেন।’ ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা থেকে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বললেন, ‘বাংলাদেশকেও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে হবে তার নিজেরই মঙ্গলের জন্য, যেন মুসলমান নয় এমন জনসমষ্টি এবং বাঙালি নয় এমন ক্ষুদ্র গোত্রগুলো বাংলাদেশকে নিজেদের দেশ মনে করতে সংকোচ অনুভব না করে।’ এই চিন্তা একজন সাধারণ ভাবুকের মনে করা ভুল। কেননা এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির একটি দুর্দান্ত সত্য। কীভাবে এই চিন্তা এলো?
বাংলাদেশ-পর্বে আবদুল হক দেখেছিলেন, ‘এত লোভ আর দুর্নীতি বুঝি দেশে আর কখনো ছিল না।’ ১৯৭৩ সালে লেখা এক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, ‘লুণ্ঠিত দেশবাসীর দুর্গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দুই হাতে পয়সা লুটতে কারো বিবেকে বাঁধছে বলে মনে হয় না।’ জীবনের মূল্য কমে গিয়ে ‘টাকা, টাকা, কিছু টাকা অথবা কিছু মালামাল দখলের জন্য বাঙালি এখন দুই-দশজন বাঙালিকে খুন করতে পারে যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে।’ আজও যত্রতত্র জনসাধারণ যে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিরীহ-নির্দোষ মানুষকেও মেরে ফেলছে, এর কারণ কী? ওই সময়ে আবদুল হক বলেছিলেন, ‘আইনের শাসন এ দেশ থেকে তিরোহিত প্রায়; আইনানুযায়ী দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির ভরসা স্বল্প বলেই জনতার এই ক্রোধ; বাঙালি আসলে ভয়াবহভাবে রক্তলোলুপ; মানবজীবনের মূল্য অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত।’ মনে হচ্ছে, এ কথা যেন এই এক-আধ মাসের মধ্যে লেখা, দেখে-বুঝে!
এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা ‘আত্মহত্যার আগে’ প্রবন্ধে তার জিজ্ঞাসা ছিল, ‘এর পরিণতি কি হবে, প্রতিকারের উপায় কি তা বলা কঠিন।’ কেন? ‘কোনো সমাজকে যদি আত্মহত্যার প্রবণতায় ধরে তবে তাকে বাঁচাবে কে। বাঙালি সমাজ বহুবার মরেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী মৃতপ্রায় থেকেছে, এখনো সেই ইতিহাসেই ফিরে যেতে পারে।’ তার এই দৃষ্টির তুলনা নেই, বলাবাহুল্য! সত্যি তো কোনো ব্যক্তি কিংবা জাতি যদি বাঁচতে না-চায়, তবে তাকে ‘বাঁচাবে কে?’ বাঁচার জন্যে মানুষের একটা নির্ভরতার জায়গা দরকার হয়; তার লক্ষ্য ও আত্মবিশ্বাস যেখানে আশ্রয় পেতে পারে! আবদুল হক একথা ভেবে বলছেন, ‘ভরসা শুধু এই, ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে জীবনের প্রতিশ্রুতি-বাঙালি-ইতিহাসে জীবনের প্রবলতম প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।’ এই শক্ত ভিত থেকে তিনি বলছেন, ‘সহসা বাঙালি মরতে চাইবে না।’ কিন্তু বাঁচবে সে কেমন করে? বাঁচাটা যে চিন্তা ও কর্মের বিষয়! তিনি মনে করতেন, ‘আত্মসমালোচনার, আত্মসংশোধনের, প্রায়শ্চিত্তের বিষয়। বিপ্লবোত্তর অথবা যেকোনো সমাজের জন্য দরকার প্রাজ্ঞ নিপুণ দৃঢ় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলি।’ এই ক্ষেত্রে যারা কাজ করবেন, তাদের হতে হবে পুরোপুরি সৎ। একই সঙ্গে চাই সমাজের বিভিন্ন তৎপরতার মধ্যে কাজ করার কর্তব্য-নিষ্ঠা-এই হতে পারে ‘আত্মহত্যাপ্রবণতা রোধের প্রথম শর্ত।’ প্রথম শর্ত, কিন্তু শেষ শর্ত নয়, অবশ্য।
চার
আবদুল হক মানুষটি কেমন ছিলেন, এবার সে নিয়ে দু-কথা বলা যাক। তাকে ‘নিভৃতচারী’ ও ‘নির্মোহ জীবন-দৃষ্টির মানুষ’ বলা হয়েছে। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা দিতেন না। আলাপি মানুষও তাকে বলা যায় না।
সভা-সমিতিতে তিনি বক্তৃতা করবার সুযোগ পাননি। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, বিশেষ আলোচনা ও সংগীতাদি অনুষ্ঠানে কমই যেতেন। সাহিত্য আলোচনায়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো বক্তৃতার আয়োজন-অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি মন্দ ছিল না যদিও, কিন্তু তার মধ্যে ছিল যে ‘সিরিয়াসনেস’, যেসব বিষয় নিয়ে তিনি ভাবতেন এবং লিখতেন, ব্যতিক্রম ছাড়া, আমাদের সমাজে সেসবের সমাদর ও সমঝদার মানুষ খুব কমই ছিল।
তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি ছিল না। তিনি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে যেসব চিন্তাভাবনা ও মতামত নামে-বেনামে প্রকাশ করতেন এবং নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তায় অনমনীয়তা দেখিয়েছেন, তার সমকালীন অন্য লেখকদের মধ্যে তা সুলভ নয়। তিনি এ ব্যাপারে ছিলেন নিঃসঙ্গ। তাকে বিরুদ্ধ ও অন্ধকার পথে একা হাঁটতে হয়েছিল। সেটা এমনই দুঃসময় ছিল যে, আত্মপ্রকাশের এবং বাঙালির সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে তিনি যেসব মতামত প্রকাশ করতে চাইতেন, সে সম্পর্কে কারো সঙ্গে মতবিনিময় করবার ভরসা পেতেন না। তিনি সাহিত্য জীবনে-কী পাকিস্তান, কী বাংলাদেশ-পর্বে, তার মৃত্যুর আগপর্যন্ত আমাদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, সভা-সমিতিতে কিংবা বাংলা একাডেমির কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ এই সময়ের মধ্যে এমন লোকের নামও পাওয়া যায়, যার বলবার কথা কিছু ছিল না! অথচ তিনি বক্তৃতামঞ্চের সভ্য! বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন আজও কি সে রকম নয়?
যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য সম্পর্কে আবদুল হকের বক্তব্য ছিল। এ দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তার লেখা আজ সব থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান। তবু তিনি এ সমাজে ছিলেন বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন। তিনি যে সমাজের জন্যে নিজেকে প্রায় বিপন্ন করে তুলেছিলেন, সেই সমাজের তিনি অনাত্মীয়! তার মতো প্রগতিলুব্ধ ও বিবেকী চিন্তকের পক্ষে বান্ধবহীন এই সমাজে নিভৃতচারী হওয়াই ছিল সহজ ও স্বাভাবিক।
পাঁচ
তার ওপর আরোপিত নির্মোহ জীবন-দৃষ্টি কথাটি খুবই আকর্ষণীয়। কথাটি সংবেদনশীল মানুষের মনে একটা সম্ভ্রমবোধ তৈরি করে, অবশ্য। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণির কতকগুলো শব্দ-যেমন ‘নিষ্কাম’, নির্লোভ’, ‘নিঃস্বার্থ’-তেমনি একটি শব্দ ‘নির্মোহ’। দুটি ক্ষেত্র থেকে এসব শব্দের উদ্ভব হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রটি ধর্মীয় অনুভূূতি; দ্বিতীয়টি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। আমরা যখন পীর-দরবেশ-ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শ্রেণিকে সমাজে বড় করে দেখতে ও দেখাতে চাই, তখন তাদের সম্পর্কে ধর্মীয় অনুভূতিময় শব্দগুলো ব্যবহার করি। ‘নির্লোভ’, ‘নিষ্কাম’-এই ধারার শব্দ। অন্যদিকে কবি-সাহিত্যিক-সমাজ দার্শনিক-বিজ্ঞানী প্রমুখ ব্যক্তিকে যখন উচ্চ আসনে ভাবতে ও ভাবাতে চাই, তখন তাদের প্রতি ‘নিঃস্বার্থ’, ‘নির্মোহ’ শব্দে পরিচিত করি।
অভিধানে এসব শব্দের যে অর্থ দেওয়া হয়েছে, তা সরাসরি উল্লিখিত ব্যক্তিদের ওপর প্রয়োগ করা বিপজ্জনক। কেননা মানুষের পক্ষে নির্মোহ কিংবা নিষ্কাম হওয়া অসম্ভব। মানুষ মোহবর্জিত নয়, লোভহীন মানুষ হয় না, কামের ঊর্ধ্বে মানুষ অকল্পনীয়। তবে কি এসব শব্দ অর্থহীন? না, তা নয়। লোভ, মোহ, স্বার্থ প্রভৃতি আমাদের চরিত্রে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়, মন্দও নয়-নয় নিন্দনীয়। কারণ এসব গুণ মানবিক। মানুষ ছাড়া অপর কোথাও এর প্রয়োগ নেই। তবে আমরা যখন লোভে, মোহে, স্বার্থে অন্ধ হয়ে পড়ি-কেবল তখনই সেটা মন্দ, নিন্দাযোগ্য অথবা অপরাধ। কেননা তখন সর্ব প্রকারের অন্ধতা আমাদের লোভী, মোহান্ধ, স্বার্থান্ধ, কামান্ধ করে তোলে। অন্ধতার অনুপস্থিতি হচ্ছে নির্লোভ, নির্মোহ, নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামের পূর্বশর্ত। কাজেই আমরা যখন কারো সম্পর্কে একথা বলি যে, তিনি নির্মোহ মানুষ, তখন আমরা এটা বুঝি না যে, তিনি মোহবর্জিত। এমন স্থলে আমরা বুঝি যে, তিনি মোহের কাছে পরাজিত নন, অর্থাৎ তিনি মোহান্ধ নন।
আবদুল হক নিঃস্বার্থ, নির্মোহ, নির্লোভ মানুষ ছিলেন না। লোভ, মোহ, স্বার্থ, কাম-এর সবই ছিল তার মধ্যে। তিনি যথারীতি বিয়ে করেছিলেন। পাঁচ সন্তানের তিনি জনক ছিলেন। তিনি দুর্বহ কষ্টে অর্জিত অর্থ দিয়ে উত্তরায় বাড়ি বানিয়েছিলেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে যত রকম পুরস্কার ছিল, সরকারি-বেসরকারি, যা তাকে দিতে চাওয়া হয়েছিল, ব্যতিক্রম ছাড়া, সবই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তাকে ‘নির্মোহ জীবন-দৃষ্টি’র মানুষ বলাটা অতিকথন। তার সম্পর্কে বলা যায়, যে লোভ, যে মোহ, যে স্বার্থ ক্ষতিকর-নিজের এবং অন্যের পক্ষে, তিনি সে-রকম অন্ধ ছিলেন না। তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন এবং কোলাহল এড়িয়ে চলতেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন নীরবতাও একটি অসামান্য শক্তি। তিনি স্বল্পবাক ছিলেন। কারণ তিনি বুঝতেন, অতি কথন মননের দুর্বলতা। মন চিন্তা করবার অবসর না পেলে, বৌদ্ধিক গভীরতা বিনষ্ট হয়। এমন বাস্তবতা ব্যক্তিত্বের পক্ষে, এমন কী চিন্তার পক্ষেও অনুকূল নয়। তার জীবন ও কর্মের ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, তার ব্যক্তিত্বের চেয়ে তার চিন্তা ছিল শক্তিসম্পন্ন। সমাজে তার প্রভাব ছিল অসামান্য। আনন্দের কথা এই যে, তিনি এই বড়ত্ব বহন করতে পেরেছিলেন নিজের ব্যক্তিত্বের গুণে।
তিনি আত্মপ্রচারণায় পটুত্ব অর্জন করতে পারেননি। তিনি মনে করতেন, আত্মপ্রচারণা আসলে আত্মপ্রতারণার শামিল! মনীষার সম্ভ্রম তাকে বাকসর্বস্ব হতে দেয়নি। দল-গ্রুপিং, আত্মপ্রচার, আমিত্ব, বাগবিতণ্ডায় তার মন-ওঠেনি। জীবনে সময় যে অমূল্য, এ জ্ঞান তিনি হারাননি। সময়ের অপচয় আর শুদ্ধবুদ্ধির অপব্যবহারে তার প্রবৃত্তি হয়নি। আসলে তিনি ছিলেন ধীর-মগ্ন, অচঞ্চল ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বাইরে থেকে এটা সহসা কারো পক্ষে বোঝার উপায় ছিল না। ভেতরটা ছিল তার দৃঢ় কঠিন, লক্ষ্যভেদী। কোনো মানুষের চেতনা-স্তর এমন হলে তাকে ভাব-উচ্ছ্বাস মুক্ত থাকতে দেখা যায়।
লেখায়, আচরণে, কথায়, সর্বত্র আবদুল হক ছিলেন রুচিশীল, মার্জিত ও সুভদ্র। বাঞ্ছিত পরম সাধনার ফল পেতে চাইলে, আত্মপ্রচারের শান্তি নষ্ট হলে, তথাকথিত দুঃসহ জনপ্রিয়তার আগুন নিভে গেলে, স্থির বুদ্ধি আর মার্জিত রুচির প্রয়োজন দেখা দিলে, তবেই সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এই মানুষের ডাক পড়বে।
