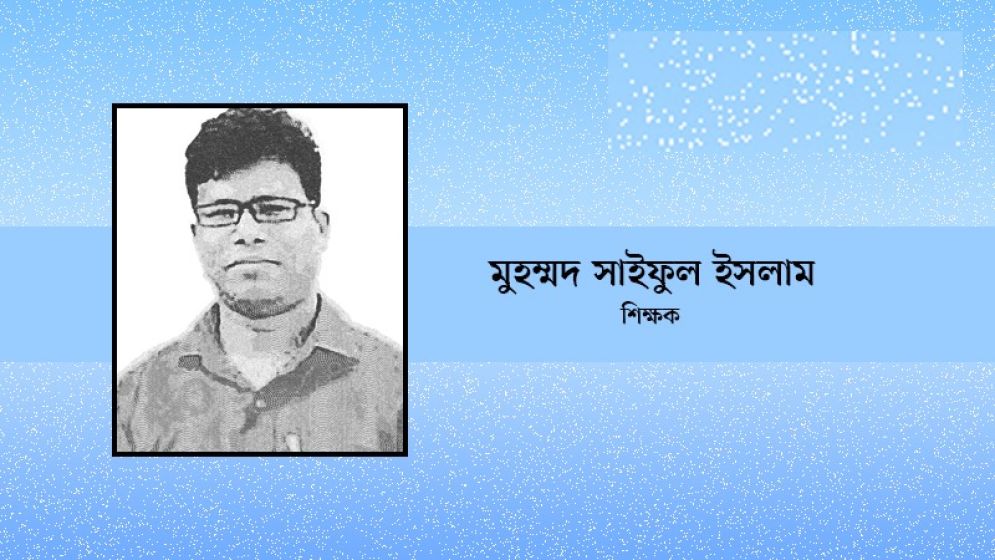
কবি অরুণকুমার সরকারের একটি কবিতা ‘শেষ খুঁটিগুলো’। এ কবিতার একটি পঙক্তি-‘শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত ক’রে ধ’রে রাখতে চাই।’ আজ সর্বত্র যেটাকে ‘খুঁটির জোর’ বলা হয়, কবি সেই খুঁটির কথা বলেননি তার কবিতায়। তিনি যে খুঁটির কথা বলেছেন, তার অর্থ বৃহৎ, গভীর, তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও বলা যায়, ‘এই পথে আলো জ্বেলে-এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।’ কবি চেয়েছেন সে রকম কিছু খুঁটি, যা সহজে পাওয়া যায় না, পেলে জীবনে সার্থকতা আসে। বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে, অনেক সংশয় ও দুর্ভোগ শেষে হয়তো তা পাওয়া সম্ভব। সে রকম দু-একটি খুঁটির নাম সত্য, সাহস, সাম্য, স্বাধীনতা, র্যাশনালিটি। রাষ্ট্রের প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের মধ্যে এসব আদর্শিক খুঁটি রক্ষা করবার কথা বলেছিলেন কবি।
মানুষ স্বভাবতই পৌত্তলিক, বলেছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ভাবুক কাজী আবদুল ওদুদ। এই পুতুলপূজা মানুষ সহসা ছাড়তে পারে না। কেননা মানুষ পুতুলপূজার অধিকার লাভ করে উত্তরাধিকারসূত্রে, পরম্পরাগতভাবে। শিক্ষা যদি বিবেক ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, তবে এই শিক্ষা মানুষকে বাধা দেয় নির্বিচার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে।
শিক্ষার ভেতর বিবেকের অনুশীলন এক অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষক ও পাঠক্রমের মধ্যে বিবেকের এই প্রতিচ্ছবি থাকা চাই। কেননা বিবেকের আছে সেই শক্তি, যে নির্বিচার সহ্য করতে পারে না। এই বিবেকের কথা শুনে এসেছি আমরা শ্রেণিকক্ষের অগণিত শিক্ষকের কাছে, পরিবার ও সমাজের মুরব্বিদের কাছে।
জিজ্ঞাসা এই : কাকে বলব বিবেক? নৈতিকতার নানা স্তর আছে। সেসব স্তরের মধ্যে আছে মানবিক বৃত্তির এক উচ্চায়ত রূপ, যার ক্রিয়াশীলতায় কোনো মিথ্যা দাঁড়াতে পারে না, তার নাম বিবেক। বিবেক একদিকে হিসাবি, সে সাবধানী। সতর্ক তার তর্জনী। অন্যদিকে সে নির্দেশ দেয়, শাসন করে। ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার শাসন সর্বত্রগামী। ব্যক্তি থেকে বিশ্বের দিকে বিবেকের গতি। কিন্তু শিক্ষা যেখানে কেবল লেখাপড়া শেখায়, বিচার দৃষ্টি অর্জন করতে দেয় না, সেখানে পুতুলপূজা বাধাহীন।
এই পূজার আছে নানা রূপ। রাজনীতির ক্ষেত্রে দলীয় পূজা, বাহাদুরি দেখানোর ক্ষেত্রে বীরপূজা, বড়লোকি ফলানোর ক্ষেত্রে টাকার পূজা, স্বদেশপ্রেমের নামে হিংসার পূজা, ক্ষুধা নিবৃত্তির নামে রসনাপূজা, ভালোবাসার নামে বাসনালুব্ধ কামের পূজা-এমন বিচিত্র পূজা-প্রার্থনায় আমরা সম্মোহিত। বাঙালি দার্শনিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী মনে করতেন, এই পূজক সম্প্রদায়ই হচ্ছেন আদেশপন্থি। এরা অন্যের আদেশ মেনে চলেন। আদেশপন্থি লোকের পক্ষে তাই নেতা হওয়া অসম্ভব। কারণ নেতৃত্ব নামের গুণের মধ্যে থাকে ‘না’ বলবার শক্তি। ‘না’ হচ্ছে নেতৃত্বের এক প্রধান গুণ। এই ‘না’ স্বয়ম্ভু, স্বয়ংজাত। কারো আদেশ সহ্য করা এর স্বভাব নয়। ন্যায় ও সত্যের যোগাত্মক গুণে তৈরি হয় বিবেক। ‘বিবেক’ ব্যক্তিগত হলেও তাই দিয়ে চলে নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব নৈতিক সংগ্রামের প্রতীক।
দুই
নজরুল তার একটি গানে বলেছিলেন, ‘চাই না তোমার বেহেশত খোদা, নামাজ রোজার বদলাতে।’ আল্লাহর ভয়ে কিংবা বেহেশতের লোভে নামাজ-রোজা করলে তার কোনো নৈতিক মূল্য নেই। যারা তা করেন, আল্লাহকে চেনেন না। একটা কিছুর বিনিময়ে তারা বুঝে নিতে চান কেবল লক্ষ্যভেদী ফল! আল্লাহর সঙ্গে এরা গড়তে চায় ব্যাবসায়িক সম্পর্ক, ভালোবাসা নয়।
কবি বলতে চেয়েছেন, আল্লাহর বিধান আমরা মান্য করি আমাদের অন্তরের শুদ্ধির জন্যে। তাঁর ভয়ে কিংবা তাঁর কাছে কিছু প্রাপ্তির লোভে নয়। কেননা আল্লাহর বিধান সব ভালো, আর ভালো বলেই তিনি আল্লাহ-এই উপলব্ধি থেকে মানুষ যখন আল্লাহর হুকুম পালন করে, তখনই কেবল শুদ্ধ বুদ্ধি মান্যতা পায়। এইখানে আল্লাহর বিধান আর মানুষের স্বাধীনতা এবং তার র্যাশনালিটি এক ও অভিন্ন মাত্রা লাভ করে। এর ব্যত্যয়ে আমরা মনুষ্যত্বের খুঁটিগুলো হারিয়ে ফেলি!
তিন
স্বাধীনতার পরে যে সংবিধান রচিত হয়, তাতে চারটি খুঁটির কথা বলা হয়েছে : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আজ এ কথা আমাদের মানতে হচ্ছে যে, এই খুঁটিগুলোর জোর আর নেই কোথাও! কেন? দীর্ঘকাল রাজনীতির মধ্যে চলে এসেছে ভিন্ন এক খুঁটির জোর-ক্ষমতা যার সর্বপ্রধান লক্ষ্য। লৌকিক ভাষায় এর নাম গায়ের জোর। দলীয় রাজনীতির শক্তির ওপর নির্ভর করে এই কেন্দ্র কার দখলে থাকবে! এই লড়াইয়ে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক খুঁটিগুলো হারিয়ে যায়! খুঁটিগুলো যে সংবিধানে ছিল কিংবা আছে, এই কথাটিও চলে যায় বিস্মরণে! অথচ আমাদের জাতীয় জীবনে বড় হওয়ার জন্যে এর যেকোনো একটি খুঁটির জোরই আমাদের পক্ষে ছিল যথেষ্ট।
একমাত্র সম্মোহিত ও বিবেকবর্জিত ব্যক্তি ছাড়া চারপাশে সবাই স্বীকার করছেন, খুঁটিগুলোর সযত্ন ব্যবহার নেই কোথাও। ধরা যাক সমাজতন্ত্রের কথা। এটা খুব বড় ব্যাপার নিঃসন্দেহে, কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্র সমাজতন্ত্রের উপযোগী নয়। এ ব্যাপারে আমাদের জাতীয় মনকে মানুষ করবার চেষ্টা করা হয়নি কোনো দিনই। আমাদের শিক্ষায় এর অনুকূল পাঠক্রম ও পরিবেশ নেই। আমাদের কাছে সমাজতন্ত্র যেন পড়ে পাওয়া চৌদ্দ-আনা গোছের বস্তুমাত্র! এর অর্থ-আমাদের সংবিধানে এ ছিল দুর্বল মুহূর্তের একটা আবেগমাত্র! মুসলমান কিংবা হিন্দু মন কখনো বিপ্লবী হতে পারে না। সংস্কারলুব্ধ মন ও ধর্মবিশ্বাসী মানুষের পক্ষে এটা অকল্পনীয়। বিপ্লব বিষয়ে এ মনের ভবিষ্যৎ নেই। বিপ্লবীর জীবনে হিন্দু কিংবা মুসলমানের রক্ত থাকলে সমাজে কোনো দিনই সাম্য-অবস্থা আসবে না। নিরাসক্ত র্যাশনাল মন তৈরি করা এ মাটির স্বভাববিরুদ্ধ। ধর্মনিরপেক্ষতাও এই কারণে কঠিন সত্য।
সম্প্রদায় থাকলে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে। ধর্মবিরহী মানুষের পক্ষে সেক্যুলারিজমের ভাবনা অসম্ভব। অন্যদিকে বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী রাজনীতি ধর্মের ব্যবহার ছাড়তে পারে না। কেননা সেটাই তার স্বরূপ। সেই স্বরূপ অতিক্রম করে যে রাজনীতি, এ অঞ্চলের অভিজ্ঞতায় অনুপস্থিত। অতীতে যা ছিল না, ভবিষ্যতে তা গঠন করা যাবে না, তা নয়। তবে তার জন্যে দরকার অন্য এক শুদ্ধতম বোধ।
আমাদের ভাষায় মানবতাবাদ, গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি এসেছে। কিন্তু এগুলো এসেছে তত্ত্ব হিসেবে, বিদেশি ভাষা থেকে তরজমা হয়ে। উচ্চশিক্ষায় গবেষণার বিষয় হিসেবে। আমাদের আধুনিক জীবনের একটা মৌল অবলম্বন ও অঙ্গ হিসেবে এগুলোর প্রবেশ সত্য হয়ে ওঠেনি! এসব আদর্শের জন্যে আমরা এতটুকু জায়গা তৈরি করে দিতে পারিনি! আমরা মুখে বড় হতে চেয়েছি, কিন্তু মনকে তার জন্যে প্রস্তুত করবার দুঃখ স্বীকার করিনি!
জাতীয়তাবাদ নামেও একটি স্তম্ভ স্বীকার করা হয়েছিল সংবিধানে। যার অর্থ জাতির প্রতি আসক্তি, অনুরাগ এবং অতীত গরিমার স্তুতি। আসলে জাতীয়তাবাদ যে মন্ত্র দেয়, সেটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আকর্ষণ, সমূহের আধিপত্য। এটাই এর প্রধান কথা। জাতীয়তাবাদ থেকে তাই আগ্রাসন ও হিংসা বাতিল করা যায় না। স্বদেশপ্রেম যেখানে অন্ধ, জাতীয়তাবাদ সেখানে প্রবল। সমাজতন্ত্রের একেবারে বিরুদ্ধ বিষয় এটি। রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ মনীষী দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের হিংস্রতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় অহিংস জাতীয়তাবাদের আবাদ করা হয়নি। অন্য দেশের প্রতি বৈরিতা না দেখিয়ে স্বদেশের সর্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টা যেখানে বিদ্যমান, স্বদেশপ্রেম সেখানে যথার্থ। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদকে আমাদের মানসিক স্তরে এমন উচ্চতায় দেখা হয়নি।
চার
অথচ মৌল সত্য, গত পঞ্চাশ বছরের অধিক সময়ে আমাদের রাজনীতিতে চর্চা করা হয়েছে স্বৈরতন্ত্রের। এর মাত্রাটা কখনো কম, কখনো-বা বেশি, এইমাত্র বলা যায়। এই তন্ত্রের ভালো পরিচিত নাম ফ্যাসিবাদ। গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে বারবার, কিন্তু বাংলাদেশে এ বস্তুর প্রবেশই সম্ভব হয়নি, একমাত্র সংবিধানে ছাড়া! গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌল অংশ। বাঙালির সমগ্র রাজনৈতিক ইতিহাসে কারচুপিহীন, অপ্রতিরোধ্য, অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে (১৯৭০)। এর পরিপ্রেক্ষিতটা মনে রাখা ভালো।
গণতান্ত্রিক সমাজে আদর্শের আর একটি বড় জায়গা হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। মানুষে মানুষে সহযোগের ভিত্তি তৈরি করতে হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভাগ করে নিয়ে। রাষ্ট্রে সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং অহিংস নীতি অবলম্বন সেই ভাগের প্রধান কথা। অহিংস নীতি কেন? অর্থনীতিবিদ ও সমাজদার্শনিক অম্লান দত্ত বলেন, ‘অহিংসা প্রধান কথা এই জন্য যে, হিংসার সাহায্যে একবার যখন আমরা ক্ষমতা দখল করি, সেই মুহূর্ত থেকে আমাদের মনে এই আশঙ্কা জেগে থাকে যে এরপর অন্য কোনো দল আবার হিংসার সাহায্যে আমাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে। আর সেই কারণেই আমরা তখন ক্ষমতা দখল করবার পর কী করে সেই ক্ষমতাকে রক্ষা করা যায়-এই চিন্তাটাকেই সবচেয়ে বড় বলে মনে করি।
আর তার ভেতর দিয়েই নতুন করে অত্যাচারী রাষ্ট্র, আমলাতন্ত্র, পুলিশবাহিনী, সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে।’ এ কথা যদি সত্য হয়, আমাদের ধারণা সত্য, তবে জিজ্ঞাসা-যাদের হাতে এত ক্ষমতা, পুরো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, তাদের মনে শান্তি, চোখে ঘুম থাকে না কেন? এর প্রধান কারণ একটি-ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা। এই আশঙ্কার অন্তরে থাকে অস্তিত্বের হুমকি। এ হচ্ছে নিরেট আত্মঘাতী লাইন। এই অলঙ্ঘনীয় মিথ্যাভীতি থেকে তৈরি হয় স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব ও নিরঙ্কুশ দলীয় রাজনীতি। এই প্রক্রিয়া কায়েম করে এককেন্দ্রিক ক্ষমতার প্রাচীর! পলিটিক্সের এমন ক্ষেত্রে গণতন্ত্র পুরোপুরি চরিত্র হারিয়ে ফেলে।
পাঁচ
ঠিক এই কারণে এক গভীর মৃত্যুঘন অন্ধকারের কথা শোনা যায় চারপাশে। শ্রমিকশ্রেণি থেকে নিয়ে উচ্চশিক্ষিত সকল স্তরের মানুষের মধ্যে তাই বুক-ভাঙা নৈরাশ্যের গরম নিঃশ্বাস এক অমোচনীয় সত্য। অধিকাংশ মানুষের ধারণা, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ফ্যাসিস্ট রাজনীতি এই অবস্থার জন্যে প্রধানভাবে দায়ী। এর থেকে মুক্তির উপায় আজ আর কোনো মানুষই শোনাতে পাচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষ আজ নিজ নিজ ধর্মানুসারে মসজিদ ও মন্দিরে আশ্রয় খুঁজছে! সেখানেও জীবনের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই! লেখাপড়া জানা মানুষের একটা বড় শ্রেণি ফ্যাসিস্ট রাজনীতির সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা! কেউ প্রত্যক্ষভাবে, কেউ পরোক্ষভাবে। এমন রাজনীতির ছায়ায় নিশ্চিন্তে থাকা ঘি-মাখন খাওয়া এই শ্রেণির কাছ থেকে মুক্তির কোনো ইশারা আসতে পারে না!
আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিদিন আমাদের শুনিয়ে চলেছে, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই! এ এক আত্মঘাতী প্রচারণা! এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে উল্লিখিত সাংবিধানিক খুঁটিগুলো ভেঙে গুঁড়া হয়ে যায়, এ জ্ঞান আজ প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে! অথচ খুঁটিগুলো রাজনীতির এক-একটা মূল্যবান স্তম্ভ! ও-গুলো যদি শেষ কথা না হয়, তাহলে অপর খুঁটিগুলো-একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করা কি আমাদের কাম্য?
ছয়
এই কিছুদিন আগেও রাষ্ট্রীয় হেফাজতে ক্রসফায়ারে, বন্দুকযুদ্ধে এবং গুম করে মানুষকে যে পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছে তা বর্ণনাতীত। তদন্তের নামে সে ছিল সীমাহীন মিথ্যাচার ও প্রহসন। নিরীহ-নির্দোষ লোকজনকে আসামি করে তাদের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের নামে রিমান্ডে নিয়ে চলেছে ঘৃণ্য-পাশবিক অত্যাচার। যেকোনো মানুষের পক্ষে এটা মনে করা সহজ যে, এর থেকে মৃত্যু শ্রেয়। কেননা মৃত্যুতে মানুষের জীবন অবসান দুঃখের হলেও তা সহনযোগ্য। কিন্তু মানুষের মৃত্যুর চেয়েও মানুষের শুদ্ধ চেতনার মৃত্যু গভীরভাবে শোকাবহ। এই কর্মকাণ্ডে কেবল মানুষ মরছে না, মরছে মানুষের শুদ্ধ চেতনা ও মনুষ্যত্ব।
এমন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তবু মানুষকে খুঁজে নিতে হয় এমন কিছু মূল্যবোধ, যার জ্যোতির্ময় আলো সত্যের কঠিন মানুষ ক্ষণস্থায়ী, কেননা মানুষের মৃত্যু হয়। ‘মানব’ মহাকাল, কেননা ‘মানব’-এর মৃত্যু নেই। মৃত্যুহীন গুণ আছে বলেই মানুষের মূল্য, অন্যথায় মানুষ প্রাণীমাত্র। ‘মনুষ্যত্বের জাগরণ’ নামের একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘মানুষই মানুষের প্রধানতম শত্রু। আমি ইহা অনুভব করিয়াছি ও বুঝিয়াছি। এ-চিন্তা সত্ত্বেও আমার হৃদয়ে একটি গভীর আশা ছিল,-তাহা এই যে, এমন স্থান আমি বাহির করিতে পারিব, এমন মন্দির-যেখানে মানুষে মৃত্যুহীন সত্তা মেঘাবৃত সূর্যের মতন গোপনে বাস করিতেছে।’
রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেমই ছিল মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য। তিনি মনে করতেন, সত্যই জীবনের পরিপূর্ণতা দান করে। কবি এই মূল্যের কথা বলেছিলেন তার শেষ জীবনের লেখা বিখ্যাত একটি অনবদ্য সুন্দর কবিতার দু-পঙক্তিতে, ‘সত্য যে কঠিন’। একই কথা বহুবার উচ্চারণের দরুন বিরক্তি জমে ওঠে মনে। তা সত্ত্বেও এবং বহু দার্শনিক ব্যাখ্যা হয়েও কবির ও-কথার মূল্য হারায় না। এর ইশারা জীবনের বহুব্যাপ্ত তুচ্ছতা ও গ্লানিকে শুধু সহনীয় নয়, বরণীয় করে তুলতে পারে। কীভাবে? আনন্দের সঙ্গে এই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা মনুষ্যত্বের লক্ষণ-কবি অরুণকুমার যেটাকে বলেছেন খুঁটির জোর।
