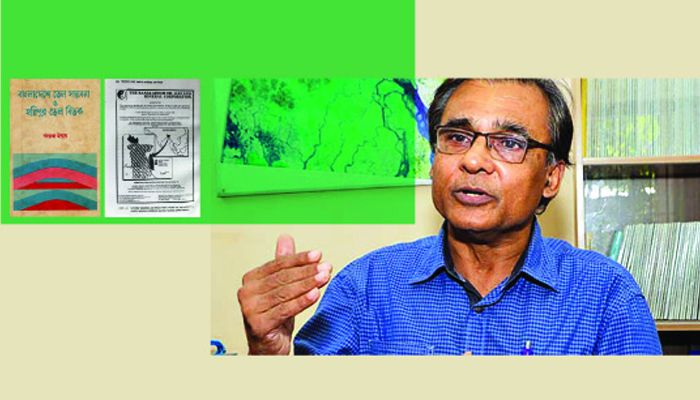
অধ্যাপক বদরুল ইমাম
এক
অধ্যাপক বদরুল ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিছক একজন ভূতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে জীবন কাটিয়ে দেননি, বাংলাদেশের খনিজসম্পদের রাজনীতিটিকে দেশের পক্ষে টেনে আনার লড়াইয়ের সঙ্গেও নিজের জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। উত্তর-উপনিবেশী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির ধারা বুঝতে গেলে অধ্যাপক বদরুল ইমামদের মতো কর্মযোগী মানুষদের সাফল্য আর ব্যর্থতার কারণগুলোকে অনুসন্ধান করতে হবে। আর আরও বেশি করে বুঝতে হবে, বিকাশের যে সম্ভাবনাগুলো তারা তৈরি করেছিলেন, এবং ওই উত্তর-উপনিবেশী বাস্তবতায় এই রাষ্ট্রের পক্ষে যে সম্ভাবনাগুলো অর্জন করাটা এই রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি, সেগুলোকেও। শিক্ষা-চিকিৎসা-নারীর অবস্থান-পরিবেশ-জাতীয় পরিকল্পনা ইত্যাদিসহ একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতিতে অগ্রগতির সামগ্রিক মূল্যায়নটা করতে গেলে যে খাতগুলোকে আলাদা আলাদা করে পর্যালোচনা করবার দরকার পড়ে, তার অন্যতম একটি হলো খনিজসম্পদ নীতি। অধ্যাপক বদরুল ইমামরা সেই নীতিটিকে জনস্বার্থের পক্ষে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন।
শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে, বিশ্লেষক হিসেবে অধ্যাপক বদরুল ইমাম শ্রেষ্ঠদের কাতারে থাকবেন, কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু একইসঙ্গে, রাষ্ট্রনীতিকে মেরামত করবার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাদের প্রচেষ্টার সাফল্য কতখানি, সেই প্রশ্ন বারবার উঠবে। তবু এটাও ঠিক যে, সেই ব্যর্থতার দায় ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীগতভাবে বাংলাদেশের সৎ, জনগণের পক্ষের বুদ্ধিজীবীদের একার নয়। বরং সেই দায়টা সামগ্রিক। এই সামগ্রিক হতাশাগ্রস্ত সূচকগুলোর দিকে তাকালেও আমরা দূর থেকে অধ্যাপক বদরুল ইমামকে একটা আশার বাতিঘর হিসেবে দেখতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, এই মানুষগুলোর হাতে শিক্ষা ব্যবস্থা মেরামত করবার দায়িত্ব থাকলে, এই মানুষগুলোর হাতে জ্বালানি নীতি তৈরি করবার দায়িত্ব থাকলে সীমিত সামর্থ্য দিয়েই আমরা আরও কত বিপুল অর্জন করতে সক্ষম হতাম। ভবিষ্যতে তেমন মানুষদের আগমনের পথ মসৃণ করতেই বদরুল ইমামদের মতো পূর্বসূরিদের বিষয়ে জানা থাকাটা দরকার। এই অর্থে খনিজ আকরিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বদরুল ইমামের নিজের জীবনটাও রাজনৈতিক-অর্থনীতির একটা আকরিক যেন, যার রাসয়নিক বিশ্লেষণে দেশটার ইতিহাসের একটা উল্লেখযোগ্য পর্ব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।
দুই
নিতান্তই কিশোর বয়েসে অধ্যাপক বদরুল ইমামের একটা বই এ হাত-সে হাত ঘুরে পাঠ করবার সুযোগ হয়েছিল। বহু বছর পরে সেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের একটি সংরক্ষিত নমুনা দেখেছি ইউপিএল এর কার্যালয়ে। বইটির নাম ‘বাংলাদেশে তেল সম্ভাবনা ও হরিপুর তেল বিতর্ক’। প্রকাশের দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর বইটিকে স্মরণ করবার কারণ একটাই- এই বইটি অন্য যে কোনো একটি বইমাত্র নয়, এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তের অংশ। বইটিকে উৎসর্গ করা হয়েছিল ‘নিরন্তর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে বাঙালি ভূতত্ত্ববিদরা বাংলাদেশে প্রথম তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করলেন।’
তেলক্ষেত্র! বাংলাদেশে! হরিপুর তেলক্ষেত্র বহু বছর ধরেই একটি অনালোচিত নাম। বাংলাপিডিয়ায় খুব ছোট একটি ভুক্তি এ নিয়ে মিলবে, উইকিপিডিয়াতে আরও ছোট। ফলে বিস্ময় জাগতেই পারে। অথচ হরিপুর তেলক্ষেত্র নিয়ে জাতীয় একটি ঝড় দৃশ্যমান হয়েছিল। এর একদিকে ছিলেন দেশের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী এবং পরিকল্পনাবিদরা, ছিল সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থন। আরেক দিকে ছিলেন সামরিক স্বৈরাচার হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং তার গুটিকয় মোসাহেবরা। একটা বুদ্ধিবৃত্তিক আলোড়ন জনগণের মাঝে কিভাবে একটা চেতনার শক্তি তৈরি করে, তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল হরিপুর তেলক্ষেত্র নিয়ে সেই বিতর্ক, এবং এই আলোড়নের ফলাফল সর্বদলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচি পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সেখানে বিক্ষোভ, গুলিবর্ষণ এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। অথচ এই যে হরিপুর তেলক্ষেত্রটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বড় বাঁক হিসেবে চিহ্নিত, যে হরিপুর তেলক্ষেত্রটি বাংলাদেশের জ্বালানি নীতিতে একটা বড় বাঁকবদল আনতে পারতো, সেই হরিপুরবিষয়ক আলোড়নের স্মৃতি এখন পুরোটাই ঝাপসা। আজকাল মানুষ অন্তর্জ্বাল থেকেই প্রয়োজনীয় রসদের একটা বড় অংশ সংগ্রহ করেন। ঘটনা চলাকালীন মানুষ ভাবেন তাদের স্মৃতি অক্ষয় এবং নিজে থেকেই প্রবহমান থাকবে, জারি থাকবে; কিন্তু আস্ত এই হরিপুর তেলক্ষেত্রবিষয়ক বিতর্কটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতি ও উন্নয়ন নীতি যে একটা ঝাঁকুনি খেয়েছিল, সেই স্মৃতিটিই তো প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। আনু মুহাম্মদের একটা লেখা ছাড়া অন্তর্জ্বালে তার বিন্দুমাত্র আঁচ পেলাম না! অধ্যাপক বদরুল ইমাম দেশের স্বার্থ বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকে সেই ঘটনাটির বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ নিয়ে একটা আস্ত বই লেখেন। যেটির দু-দুটি সংস্করণ অন্তত বাজারে এসেছিল। এত বছর পর সমগ্র ঘটনাটির পুনর্মূল্যয়নের একটা সুযোগ তৈরি করে রেখেছেন। এবং এই যোগ্যতা যে অল্প কয়েকজন মানুষের ছিল, তারা সকলে যেমন সেই ঘটনায় একত্রিত হয়ে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছেন, তাদের মাঝেও শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বদরুল ইমাম ছিলেন নেতৃস্থানীয়।
তিন
বদরুল ইমাম তার ওই গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন পাকিস্তান আমলে খনিজসম্পদ অনুসন্ধানে সীমিত সাফল্য এলেও বৈষম্য ছিল বিপুল। তখন অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ওজিডিসি) দশ বছরে পূর্ব বাংলায় মাত্র দুটি কূপ খনন করেছিল, একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে খননকৃত কূপের সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশি (পৃষ্ঠা ৪০)। তবে ৬০ দশকে শেল অয়েল এদেশে ৫টি গ্যাসকূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, এবং বাংলাদেশকে তারা একটি গ্যাস সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে।
এই পশ্চাদপদটিকে স্মরণে রাখলে অধ্যাপক বদরুল ইমামের গ্রন্থটির ‘বাংলাদেশের অভ্যুদয়, পেট্রোবাংলার জন্ম ও সাফল্য’ অধ্যায়টির তাৎপর্য সহজে উপলব্ধি করা যাবে। বদরুল ইমাম লিখেছেন, ‘এদেশের তেল অনুসন্ধানের ইতিহাসে পেট্রোবাংলার অভ্যুদয় একটি বিশেষ ঘটনা, কারণ এই প্রথম দেশীয় বাঙালি ভূতত্ত্ববিদরা ও কারিগরিবিদরা সর্বোতভাবে তাদের কর্ম উদ্যমকে বাস্তবায়িত করবার সুযোগ পান। পেট্রোবাংলা তার প্রথম অনুসন্ধানী কূপটি ১৯৭৫ সানে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে খনন করে। বাঙালি ভূতত্ত্ববিদদের কর্মদক্ষতা নিঃসন্দেহে সাফল্যজনকভাবে প্রমাণিত হয়, পেট্রোবাংলার জন্মের প্রথম প্রায় এক দশক সময়েই যখন এই সংস্থা এদেশের ভূখণ্ডে মোট পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে। ...উপরোক্ত গাসক্ষেত্রসমূহ আবিষ্কার ছাড়াও এই সংস্থা এদেশের তেল অনুসন্ধানের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটি ঘটায় তা হলো ১৯৮৬ সনের ডিসেম্বর মাসে সিলেটের হরিপুরে বাংলাদেশের প্রথম তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কার। বাংলাদেশে তেল অনুসন্ধানের কার্যক্রমের ওপর একাধিক বিদেশি বিশেষজ্ঞের বিরূপ মন্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করে পেট্রোবাংলার ভূবিজ্ঞানিরা তেল আবিষ্কারের মাধ্যমে এদেশের অনুসন্ধান কার্যক্রমে বিশেষ চাঞ্চল্য বয়ে আনেন।’’ (পৃষ্ঠা ৪০)
হরিপুর তেলক্ষেত্রের সাফল্যের বিশেষ দিকটি এখানেই, এই ভূখণ্ডে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ব্রিটিশ আমলে শুরু হলেও ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টিতে তারা তেলক্ষেত্রের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু খুব কম সময়, অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং প্রতিকূলতা নিয়েও অনেক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভূবিজ্ঞানীরা একটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে শুধু বাংলাদেশের বিজ্ঞানী মহলে নতুন আশাবাদ ও আলোড়নের জন্ম দেননি, দেশবাসীর প্রত্যাশ্যা আর আত্মবিশ্বাসকেও জাগিয়ে তুলেছিলেন। এই ঘটনাটির একটা দীর্ঘ তাৎপর্যবাহী সম্ভাবনা সেই অর্থে ছিল।
অন্যদিকে, গরিব দেশগুলোর খনিজসম্পদ বিষয়ে বহুজাতিক জ্বালানি প্রতিষ্ঠানগুলোর নানান দীর্ঘমেয়াদি ছক কীভাবে কাজ করত, সেটার একটা আভাসও বদরুল ইমামের সেই আলাপেই মিলবে। হরিপুরে সিলেট-৭ গ্যাসকূপটির উন্নয়নের কাজটি যখন চলছিল, অধ্যাপক বদরুল ইমাম থেকেই উদ্ধৃত করা যাক-
‘এই কূপে একাধিক গ্যাসস্তর এবং একটি তেলস্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কূপটি উল্লিখিত চূড়ান্ত গভীরতায় পৌঁছবার আগেই সেখানে নিয়োজিত বিদেশি কনসালট্যান্ট খননে কারিগরি জটিলতার অজুহাতে খনন শেষ করবার পরামর্শ দেন এবং কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করতে প্রয়াস পান। তাদের নাকি যুক্তি ছিল যে, উপরে ইতিমধ্যে প্রাপ্ত গ্যাসের স্তর হতে তারা পরিকল্পনা মাফিক গ্যাস উত্তোলন নিশ্চিত করে দেবেন এবং আরও গভীরে খননের অতিরিক্ত ব্যয়ভারের দায়িত্ব তারা নেবেন না; কিন্তু সেখানে নিয়োজিত বাংলাদেশ তেল গ্যাস ও খনিজসম্পদ করপোরেশন (জিওজিএমসি- এটি পেট্রোবাংলার একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ছিল) এর দেশীয় ভূতত্ত্ববিদ বিশেষজ্ঞরা এর প্রতিবাদ করেন এবং আরও গভীরে ইঙ্গিতবহ তেলস্তরের সম্ভাব্যতা যাচাই করবার জন্য দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেন।’
এত বছর পর এই অনীহার স্পষ্ট কারণ বলা মুশকিল। খুবই সম্ভাবনা থাকে এই আনুমানিক উপাত্তগুলোকে সম্ভাব্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া, যারা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের সম্ভাবনা যাচাই করতে এই ধরনের তথ্যগুলোকে উচ্চমূলে ক্রয় করত; কিন্তু দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দৃঢ়তায় কূপটিতে তেলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবার পর শুরু হলো আসল খেলা। স্বার্থান্বেষী মহল তো শুধু বিদেশি বেনিয়ারই ছিল না, ছিল তাদের স্থানীয় সহচররাও!
চার
দেশীয় ভূতত্ত্ববিদদের আবিষ্কৃত হরিপুরের তেল উত্তোলনের জন্য এরশাদ সরকার সিমিটার নামের কোম্পানিটির সঙ্গে ‘উৎপাদন অংশীদারিত্ব’ চুক্তিবদ্ধ হয়। বাংলাদেশে গ্যাসক্ষেত্রগুলোকে যেভাবে ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে বিদেশি কোম্পানিগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে যারা খোঁজখবর রাখেন, তারা সকলেই উৎপাদন অংশীদারিত্ব কথাটির সঙ্গে পরিচিত। গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ। সম্ভাবনাপূর্ণ কোনো জায়গাতেও আদৌ খনিজের দেখা নাও মিলতে পারে। এ কারণে বহু প্রতিষ্ঠান ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলোতে উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যেখানে উৎপাদন থেকে খরচ মেটাবার পর বাকিটা উত্তোলক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মাঝে ভাগাভাগি হয়। কোনো বুদ্ধিমান ও সৎ সরকার কখনোই নিশ্চিত খনিজ মিলবে এমন জায়গাতে উৎপাদন অংশীদারিত্বের চুক্তিতে যায় না, বরং সেগুলোকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ রেখে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্বান করে। আর হরিপুরের বেলায় তেলের উপস্থিতি ইতিমধ্যেই প্রমাণিত ছিল। অন্যদিকে একটা সফল খনিজক্ষেত্র থেকে বিপুল মুনাফা হয় বলেই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন নতুন এলাকাতে ঝুঁকি নিয়েও অনুসন্ধান চালায়। এই আলাপগুলো আমার ব্যক্তিগত নতুন কোনো উপলব্ধি নয়, সেই ১৯৮৯ সালে এই কথাগুলো লিখেছিলেন অধ্যাপক বদরুল ইমাম তার হরিপুর তেল উত্তোলন বিতর্কবিষয়ক গ্রন্থটিতে। অথচ এই একই দেশবিরোধী কাজ বাংলাদেশে ’৯০-পরবর্তী সরকারগুলোও নির্বিবাদে করে এসেছে, এবং পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে দেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলোকে তুলে দিয়ে পেট্রোবাংলার মতো সুদক্ষ প্রতিষ্ঠানকে প্রায় দেউলিয়া ও সম্ভাবনাহীন সংস্থায় পরিণত করেছে।
হরিপুরের উৎপাদন অংশীদারিত্বের চুক্তিটি আসলে কতটা দেশের স্বার্থবিরোধী ছিল, সেটা বাংলাদেশেরই অন্য একটি উদাহরণে বোঝা যাবে। ১৯৭২ সালে দেশের বিদ্যুৎ-প্রাকৃতিক সম্পদ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা-আনবিক শক্তিবিষয়ক মন্ত্রী প্রয়াত মফিজ চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, বঙ্গোপসাগরে খনিজ অনুসন্ধানে বিদেশি কোম্পানিগুলোর আগ্রহের কথা, অনুসন্ধানে যদি বড় কোনো ক্ষেত্র মেলে এই আশায় তারা প্রতি বর্গমাইল ১০০০ ডলার দস্তখতী নজরানা দিয়েছিল, সেই হিসেবে ১৯৭৩ সালের জাতীয় বাজেটে এইভাবে ৩০ মিলিয়ন ডলার বিদেশি মুদ্রা যুক্ত হয়েছিল অধ্যাপক মফিজ চৌধুরীর ভাষায়। ‘শুধুমাত্র বঙ্গোপাগরের ঢেউগুনে’ [মফিজ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়, ইউপিএল, পৃষ্ঠা ৮৭]। জ্বালানির মতো প্রশ্নগুলোতে নগদ অর্থের বিনিময়ে কীভাবে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া হয়, তার আলোচনাও মফিজ চৌধুরী ওই একই গ্রন্থে করেছেন, ৮২ পৃষ্ঠায়। সেখানে তিনি বলেছেন মন্ত্রী হিসেবে তিনি সাত/আটটি দেশকে বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধানে যুক্ত করতে চাইলেও তার সহকর্মীদের কেউ কেউ আগ্রহী ছিলেন একটি মাত্র নির্দিষ্ট দেশের হাতে গোটা উপকূলের অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়ে দিতে, স্পষ্টতই এতে তাদের ব্যক্তিগত মুনাফা হতো, যদিও দেশ বঞ্চিত হতো আর্থিক দিক দিয়ে, একইসঙ্গে একটি মাত্র দেশের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতো। মফিজ চৌধুরীর ভাষ্যমতে তাঁর তৎপরতায় এটি তখনকার মতো বন্ধ করা গেলেও শেষ পর্যন্ত তার মন্ত্রণালয়টিকেই ছেঁটে জ্বালানি বিভাগকে অন্য একটি মন্ত্রণালয়ে যুক্ত করা হয়। এইভাবে, বাংলাদেশের মতো সামান্য প্রাকৃতিক সম্পদের দেশও বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর শ্যেন দৃষ্টি, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তভাবে চলতে সক্ষম হয়নি একবারে প্রথম থেকেই। এমনকি সেই সময়েই বাংলাদেশের সীমিত গ্যাসের মজুদেরও একটা অংশ ভারতে রফতানির আয়োজন চলেছিল। সরকার সমর্থক দৈনিক বাংলার বাণীতে লেখা হয়েছিল: গ্যাস রফতানি করার সক্রিয় বিবেচনা যেন তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হয়। সে জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক খাতে গ্যাস ব্যবহার ও রফতানি করার ব্যাপারে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে... আমরা গ্যাস সম্পদকে যক্ষের মতো পাহারা দিতে চাই না। তাই বিনিয়োগের ক্ষেত্র যত দ্রুত সম্ভব প্রসারিত করা যায় ততই মঙ্গল”। একই রকম রফতানির উদ্যোগ আমরা দেখেছি তার চল্লিশ বছর পর ২০০২-৩ সালে বিবিয়ানার গ্যাস নিয়েও। উভয়টিই ঠেকাতে জনগণের সক্রিয় উদ্যোগের প্রয়োজন পড়েছিল।
যা হোক, সিমিটার কোম্পানির সঙ্গে কেন উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি অবৈধ ছিল, তার কারণ বলতে গিয়ে বদরুল ইমাম লিখেছেন: “অথচ হরিপুর তেলক্ষেত্রের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত ব্যতিক্রম ঘটে। এখানে ভূতাত্ত্বিক জরিপ, কূপ খনন- এই সকল কিছুর খরচ ও শ্রম বাংলাদেশ সরকার নিজে বহন করেন এবং তেল আবিষ্কার করেন এবং তারপর উৎপাদন পর্যায়ে সিমিটার কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারিত্বের চুক্তি করা হয়। অন্য কথায়, সিমিটার তেল কোম্পানি এই আবিষ্কারের কোন খরচের অংশ বহন করলো না অথচ নিশ্চিত তেলখনি হরিপুরের তেলের অংশীদার হরো এই চুক্তির মাধ্যমে।’’ এই চুক্তির পেছনে আর্থিক ও অন্যান্য যে সকল অজুহাত সরকার দিয়েছিল, সেগুলোও বদরুল ইমাম খণ্ডন করেন। ১৯৮৯ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিমিষেই শেষ হয়ে যায়, সেটি প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডন থেকে, বদরুল ইমাম সেখানে তখন বাংলাদেশের খনিজ বিষয়ে একটি গবেষণা করছিলেন। হরিপুর গণতদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনেও এই গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে ইউপিএল।
পাঁচ
অধ্যাপক বদরুল ইমামের এই গ্রন্থটিতে বিপুল বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত ব্যবহৃত হলেও তা একেবারে বিদ্যায়তনিক গ্রন্থ নয়, সেখানে হরিপুর বিষয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা ও অঙ্গীকারের কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তখনকার বাংলাদেশের অন্য একটি পরিচয়ও মিলবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর বিরুদ্ধে সেমিনারের আয়োজন করেছিল, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, উপাচার্য প্রভৃতি প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিবর্গ সেখানে সাহসের সঙ্গেই তাদের মত ব্যক্ত করেছিলেন। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার এই প্রতিশ্রুতি পরবর্তীতে রক্ষা করেননি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো, অন্যদিকে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের স্বাধীন মতো প্রকাশের এই স্বকীয়তা হারিয়েছে বহুকাল। অধ্যাপক বদরুল ইমাম, প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ জনগণের কাতারের মানুষগুলোকে সেই তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমরা মানুষের আশার আশ্রয়স্থল হিসেবে পাচ্ছি, বহু নতুন মুখও যুক্ত হয়েছেন সেখানে।
বদরুল ইমাম তার এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আরও উল্লেখ করেছেন যে, সরকারের উচ্চতরফ থেকে পেট্রোবাংলাকে ফোন করে সিলেট এলাকার সব ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত ও মানচিত্র সিমিটার কোম্পানির হাতে তুলে দিতে বলা হয় (পৃষ্ঠা ১৩৫); কিন্তু ‘বিওজিএমি সংস্থাটির ‘ডাটা সেন্টার’ নামে যে বিভাগটিতে যাবতীয় ভূতাত্ত্বিক তথ্য, রিপোর্ট ও ম্যাপ থাকে তা প্রায় সবই ক্লাসিফাইড বা গোপনীয় হিসেবে রক্ষিত থাকে”। এটাও লক্ষ্য করবার মতো যে, পেট্রোবাংলার পক্ষ থেকে এই বেআইনি প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিল। অবশেষে সরকারের চাপে তারা বাধ্য হলেও এই বিরোধিতা করবার সৎসাহস আজকের দিনে দেখানো প্রায় অসম্ভব। অচিরেই অবশ্য সিমিটার তার অদক্ষতা, অনভিজ্ঞতা আর মুনাফা সর্বোচ্চীকরণ ও খরচ বাঁচাবার মনোবৃত্তির মাধ্যমে তেলক্ষেত্রটির যথাযথ উন্নয়নে ব্যর্থ হয়। এটা বাংলাদেশের জন্যও ভালো হয়নি, বিপুল অপচয় আর সম্ভাবনার বিনষ্টি ঘটে এভাবে।
যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত একটি সরকার বিদেশি একটা সংস্থাকে ডেকে এনে দেশের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করা প্রথম তেলক্ষেত্রটিকে কেড়ে নিয়েছিল পেট্রোবাংলার কাছ থেকে, সেটা গোটা দেশে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। স্থানীয় মানুষজনের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, গণতদন্ত কমিশনে দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ মানুষের অংশগ্রহণ এটিকে একটি জাতীয় প্রতিরোধের চেহারা দিয়েছিল। কিশোর বয়েসের দৈনিক পত্রিকা পাঠের স্মৃতি এবং আমার পিতার পেট্রোবাংলার তখন ব্যবস্থাপক পদে চাকরির সুবাদে ঘটনাবলির আলোড়নটার আঁচ বেশ খানিকটা মনে করতে পারলেও এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এই আন্দোলনটাকে ঘিরে কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সংবাদ আজ আর মেলে না। অধ্যাপক বদরুল ইমামের গ্রন্থটি এই অভাবটিকে অনেকাংশে পূরণ করেছে।
ছয়
খনিজসম্পদ ও তার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যাপক বদরুল ইমামের সাম্প্রতিক লেখালেখিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু দেশের জ্বালানি নীতিকে বদরুল ইমাম যে জায়গা থেকে পর্যালোচনা করেন, যে গ্রহণযোগ্য জ্বালানি নীতি তিনি দেখতে চান, সেটা সেই হরিপুর তেলক্ষেত্র নিয়ে বিতর্কের পথ ধরেই এগিয়েছে, এবং সেইখানে তিনি একটি মাত্র নীতি ধরে রেখেছেন, সেটা দেশের স্বার্থ রক্ষায় আপোষহীন বিশেষজ্ঞের নীতি। অধ্যাপক বদরুল ইমামের অন্যান্য নানান ভূমিকা থেকে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি তার অনুরাগ সম্পর্কে অনেকেই অনুমান করলেও এই কথাটি জোর দিয়ে বলা যেতেই পারে যে, অধ্যাপক বদরুল ইমাম পণ্ডিত হিসেবে তার অর্জিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সঙ্গে কোনো দলীয় অবস্থানকেই গুলিয়ে ফেলেননি, মিশ্রিত করেননি, বা দেশের জন্য ক্ষতিকর মনে হলেও নীরব থাকেননি। একজন বিশেষজ্ঞের কাছে মানুষের এটিই তো চাওয়া, রাজনৈতিক অবস্থান ও মতাদর্শ নিরপেক্ষভাবে নিজের বিশেষজ্ঞতার জায়গাতে দশকের পর দশক ধরে অধ্যাপক বদরুল ইমাম সেই চাওয়াটা পূরণ করে এসেছেন।
কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক বদরুল ইমামের এই প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো থেকেই আমরা দেখতে পারি দেশের খনিজ ও জ্বালানি খাতের সামগ্রিক চিত্রটি হতাশাব্যঞ্জক, সেগুলো দুর্নীতি, অদক্ষতা, অপচয় এবং ভবিষ্যতের দিকে না তাকানো, লুটেরাদের উদরপূর্তি তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বড়পুকুরিয়ার কয়লা চুরি বা গ্রানাইট খনির ক্ষয়ক্ষতি নয়; সুন্দরবনের মতো প্রাকৃতিক সম্পদকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলা বা উপকূলে বিদ্যুৎকেন্দ্র বসাবার মত বিপর্যয়কর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বদরুল ইমামের লেখা পাই, লেখা পাই বিদ্যুৎ এর মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পকলকারখানাকে বিপর্যস্ত করার বিরুদ্ধে। তিনি খুব পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানি করা হয়েছে নিছক বাণিজ্যিক স্বার্থে, এবং সেটাকে পরিপূর্ণ করার জন্যই দেশীয় নতুন গ্যাসক্ষেত্রের অনুসন্ধানকে স্থবির রাখা হয়েছে, সমুদ্রে অনুসন্ধানে চলছে ঢিলেমি। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে বাপেক্সকে বসিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে, কীভাবে বিদেশি কোম্পানিগুলোর ভুল উত্তোলন নীতি সাঙ্গুর মতো সম্ভাবনাময় একটি গ্যাসক্ষেত্রকে ধ্বংস করেছে, কীভাবে নাইকো এই দেশের খনিজ আহরণে খলনায়কের ভূমিকা পালন করেছে। ভবিষ্যতের কোনো অর্থনীতিবিদ বা জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের জ্বালানি নীতির নির্মোহ একটা সারসংকলন করতে চাইলে অধ্যাপক বদরুল ইমামের এই লেখাগুলো হবে তার প্রধান উপকরণ। আপাতদৃষ্টে হতাশাব্যাঞ্জক মনে হতে পারে, কিন্তু বিশেষজ্ঞের যে ভূমিকাটি পালন করা দরকার, সেটি সদাসর্বদা পালন করে অধ্যাপক বদরুল ইমাম গোটা দেশের তরুণ সমাজের সামনে আশার সলতেটিও বাঁচিয়ে রেখেছেন, এটুকু বলতেই হবে।
লেখার পাশাপাশি অধ্যাপক বদরুল ইমাম দেশের খনিজসম্পদ রক্ষার আন্দোলনে বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। বিদ্যুৎ ও জ্বালানিবিষয়ক গণশুনানিগুলোতে তিনি নিয়মিত বক্তব্য রেখে সরকার ও সরকারি নানান সংস্থার গণবিরোধী নীতির পর্যালোচনা করেছেন, বিকল্প বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। কখনো দেখিনি তার মতামতের কোনো সত্যিকারের মোকাবেলা করবার মতো সৎসাহস উপস্থিত সরকারি প্রতিনিধিদের হয়েছে, এর কারণ আসলে একটাই, তারা জানেন যে বদরুল ইমাম এবং তার সমমতাবলম্বী বিশেষজ্ঞদের তথ্যে ভ্রান্তি নেই, এবং তারা আর্থিক বা অন্য কোনো প্রণোদনার ওপর ভিত্তি করে মৌসুমি মতামত দেন না।
সাত
যে মূলনীতিগুলোকে বদরুল ইমাম তার দীর্ঘদিনের লেখালেখির মাঝে গ্রন্থিত করেছেন, সংক্ষেপে সেগুলো হবে এরকম : ১. দেশীয় সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা, সেজন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা; ২. নিশ্চিত গ্যাসক্ষেত্রগুলোকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে না দেওয়া; ৩. সমুদ্রের মতো এলাকায় অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বিনিয়োগ ও কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি হলে প্রয়োজনে বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসা, অথবা দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেগুলোকে কারিগরি জ্ঞান ভাগাভাগির চুক্তিতে যেতে বাধ্য করা যাতে ধীরে ধীরে দেশীয় প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলাও একাজে যোগ্য ও দক্ষ হয়ে উঠতে পারে; ৪. দ্রুত মুনাফা তুলবার জন্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত আহরণ করে গ্যাসক্ষেত্রের ক্ষতিসাধন করলে বা দুর্ঘটনা ঘটালে তার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত রাখা; ৫. জনগণকে জ্বালানি বিষয়ে যা ঘটছে এবং যা করণীয়, সেগুলোকে অবহিত করা; এবং শেষতক, ৬. ভবিষ্যৎমুখী একটি জ্বালানি নীতি নির্ধারণ যেখানে বাংলাদেশের বর্তমানের জ্বালানি নিরাপত্তার পাশাপাশি সম্ভাবনাময় বিকল্প জ্বালানির উৎসগুলোকেও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য দেশকে ভবিষ্যতের সংকটগুলো মোকাবেলাতেও প্রস্তুত করা হবে।
অধ্যাপক বদরুল ইমামের জ্বালানিবিষয়ক চিন্তাধারার প্রয়োগযোগ্যতা বিষয়ে একটা মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হতে পারে। মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত খনিজসম্পদ আহরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান পেট্রোনাস ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাদের বিজ্ঞান শিক্ষার মান তখন গভীরতা ও বিস্তারে আমাদের চাইতে দুর্বল ছিল; কিন্তু পেট্রোনাস এখন একটা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান, সফল আর্থিক দিক দিয়ে, জ্ঞানগত ও কারিগরি দিক দিয়েও তাদের অর্জন দর্শনীয়। আর বাংলাদেশে পেট্রোবাংলাকে ধারাবাহিকভাবে শুকিয়ে মারা হয়েছে পুঁজি থেকে বঞ্চিত করে, তেল ও গ্যাসক্ষেত্রগুলোকে কেড়ে নিয়ে, এবং নিজেদেরই আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারের অবমাননাকর ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করে। এই দুই রাষ্ট্রের দুটি প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথকে তুলনা করলেই মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় যাত্রাপথকে আলাদা করে বোঝাটা সহজ হয়ে যায়। মনে পড়ছে একটা গোলটেবিল বৈঠকে বদরুল ইমামকে এভাবে উদ্ধৃত করেছিল প্রথম আলো: “বাপেক্সের আবিষ্কার করা গ্যাসক্ষেত্র বিদেশিদের হাতে দেওয়ায় সংস্থাটির সব পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে চরম হতাশা কাজ করছে। বাপেক্সকে বাঁচাতে হলে তাদের আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রে কূপ খনন ও উত্তোলনের কাজ তাদেরই দিতে হবে।’’
আট
১৯৫২ সালে জন্ম নেওয়া অধ্যাপক বদরুল ইমামের বিদ্যায়তনিক অন্যান্য পরিচয়ের ওপরও আলো ফেলা যাক! ১৯৭৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে যোগ দেন। কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে ১৯৭৯ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেট্রোলিয়াম জিওলজিতে ডিআইসি ও এমএসসি এবং ১৯৮৩ সালে পিএইচডি অর্জন করেন। তার পিএইচডির অংশ হিসেবে তিনি বাংলাদেশের স্থলভাগ এবং সমুদ্রে খোঁড়া অনুসন্ধান কূপসমূহ থেকে আহরিত শিলার নমুনা বিশ্লেষণ করেন। ১৯৮৮ সালে ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটির বৃত্তি নিয়ে পুনরায় বাংলাদেশের শিলার নমুনা নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ব্রিটেনের উত্তর সাগরে অবস্থিত একটি তেলক্ষেত্রের ওপর গবেষণা করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই ভূতত্ত্ব বিভাগের অনারারি অধ্যাপক পদে নিয়োজিত আছেন। হরিপুর তেল ক্ষেত্রটি থেকে অবশিষ্ট তেল- যেটির পরিমাণ বাংলাদেশের বাস্তবতায় বেশ উল্লেখযোগ্য, সাম্প্রতিক একটি হিসেবে প্রায় ৫ কোটি ব্যারেল- আহরণের সম্ভাব্য সাশ্রয়ী উপায় নিয়ে একটি গবেষণা তার সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, আরও বহু গবেষণা ও প্রকাশনায় তার নামটি যুক্ত রয়েছে।
খুব সম্ভবত বাংলা ভাষায় ভূতত্ব বিষয়েও বাংলাদেশের প্রথম বই ‘বাংলাদেশে তেল সম্ভাবনা ও হরিপুর তেল বিতর্ক’; সেদিক দিয়েও অধ্যাপক বদরুল ইমামের এই বইটি ভবিষ্যতের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বইটির প্রাঞ্জলতা থেকেও যে কেউ বুঝতে পারবেন অধ্যাপক বদরুল ইমামের মত পণ্ডিত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ভূতত্ত্ব, ভূগোল এবং খনিজ সম্পদ সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে বাংলা ভাষায় উচ্চস্তর পর্যন্ত পাঠদানের বাস্তবতা আসলে তৈরি হয়েই আছে। বাংলাদেশের খনিজসম্পদবিষয়ক তার অন্য একটি ইংরেজি গ্রন্থও সম্ভবত এখন আর মুদ্রিত অবস্থায় নেই।
অধ্যাপক বদরুল ইমাম তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান দিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের মতোই দিশা দেখিয়ে যাবেন, এই আশাবাদের পাশাপাশি তার কাছ থেকে অন্তত দুটি ধরনের বাংলা বই আমরা দাবি করতেই পারি। প্রথমত, আশা করব তিনি ভূতত্ত্ব, জ্বালানি, জ্বালানি নীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যায়তনিক গ্রন্থ রচনা করবেন; এবং দ্বিতীয়ত, পত্রিকায় প্রকাশিত তার সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলোকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবেন। অধ্যাপক বদরুল ইমাম পরম আয়ু নিয়ে বাংলাদেশকে সেবা দিয়ে চলবেন, এবং ভবিষ্যতের তরুণদের প্রেরণার উৎসস্থল হিসেবে থেকে যাবেন, এই কামনা করছি।
লেখক: সদস্য, রাজনৈতিক পরিষদ
গণসংহতি আন্দোলন
