বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেভাবে গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠবে
ড. মো. আবুল হোসেন
প্রকাশ: ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৪
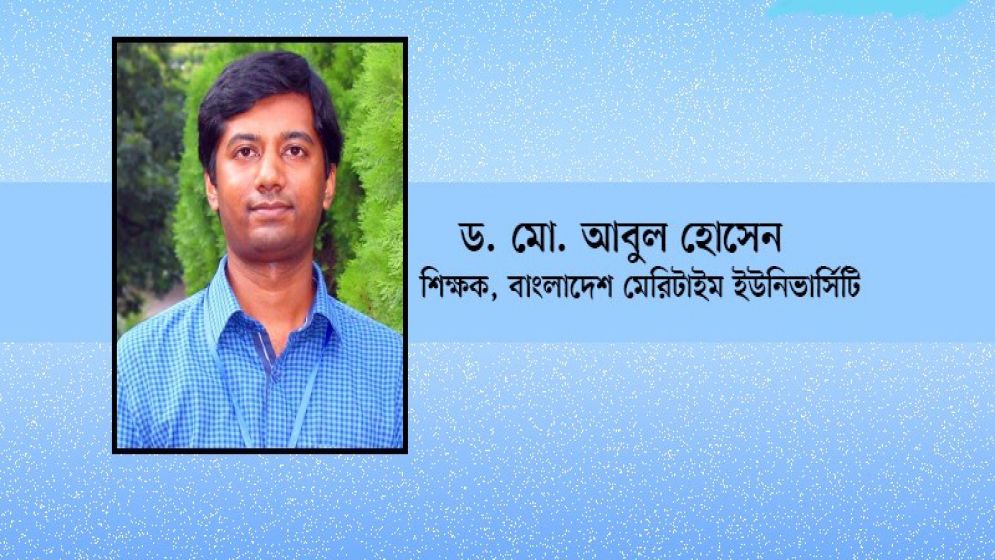
সাধারণভাবে আমাদের দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত। এই পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে সিনেটের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তার পর থাকে সিন্ডিকেট, রিজেন্ট বোর্ড অথবা বোর্ড অব ট্রাস্টিস ও ইনস্টিটিউট পর্যায়ে আছে বোর্ড অব গভর্নরস। ট্রেজারার দপ্তর বাজেট ও অর্থসংক্রান্ত কাজ করে অর্থ কমিটির মাধ্যমে। একাডেমিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয় একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে। আর সব শেষে বিভাগ পর্যায়ে আছে একাডেমিক কমিটি ও প্ল্যানিং কমিটি। একাডেমিক কাউন্সিল শিক্ষাসংক্রান্ত কাজটি করে থাকে, যার ফলাফলস্বরূপ প্রতি বছর লাখো শিক্ষার্থী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে।
শুরুর দিকে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল জোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাত্রা করে। গত ৫০ বছরে এই ব্যবস্থায় আমরা দক্ষতা অর্জন করেছি। আমাদের দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশ্বমানের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী তৈরি হচ্ছে, যারা বৈশ্বিকভাবে দেশের জন্যে সুনাম বয়ে আনছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ‘উন্নত মানের গবেষণা কেন্দ্র’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষণা ফলাফলের জোগানের মধ্যে আমাদের দেশের বিস্তর ফারাক রয়েছে। এর বড় কারণ হলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে উঠছে ‘শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক’। যার পুরোটাই ‘শিক্ষক’ নির্ভর। বর্তমানে দেশের ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষক আছেন, যাদের চাকরিতে গবেষণা ও প্রকাশনা প্রায় বাধ্যতামূলক। কিন্তু সঠিক কর্ম পরিকল্পনার অভাবে এই কর্ম ক্ষমতার অনেক বড় একটা অংশ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কাজে যুক্ত থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের মতো করে একটা গবেষণা কাঠামো গড়ে তুলেছে। সরকারের পক্ষ থেকেও অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে এসব গবেষণার জন্যে অর্থের সংকুলান করা হচ্ছে। আনুমানিকভাবে বছরে গবেষণা খাতে এই অর্থের পরিমাণ কমপক্ষে পাঁচশ কোটি টাকা। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার ফলে এই পুরা ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম আর্থিক ও গবেষণা মূল্যায়ন থাকে। যার ফলে এসব গবেষণার সম্মিলিত কোনো ফলাফল নেই। এই একই কারণে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনেক গর্ব করে, কিন্তু গবেষণা থাকা সত্ত্বেও ফলাফল নিয়ে গর্ব করতে সংকোচ করে। তাই আমাদের এখন এমন বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন, যা হবে ‘গবেষণাভিত্তিক’ ও ‘গবেষক’ নির্ভর।
যদি বৈশ্বিক ও সামাজিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ‘উন্নতমানের গবেষণা কেন্দ্র’ হিসেবে দেখতে চাই, তাহলে আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলের পাশাপাশি সমান ক্ষমতাসম্পন্ন ‘রিসার্চ কাউন্সিল’ গঠন করতে হবে। এই রিসার্চ কাউন্সিলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের গবেষণা সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করতে হবে। এই পদ্ধতিতে কাজের ফলাফল সাধারণভাবে দুটি সূচকে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক. গবেষণা বাজেটের পরিমাণ এবং দুই. গবেষণা ফলাফল যেমন প্রকাশনা, প্যাটেন্ট, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিকীকরণ ইত্যাদির সংখ্যা।
গবেষণা বাজেটের জন্যে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থের জোগান দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাজেট, মঞ্জুরি কমিশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বিচ্ছিন্নভাবে গবেষকদের থেকে গবেষণা প্রকল্প আহ্বান করে অর্থ প্রদান করে থাকে। এসব মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে অর্থের প্রাথমিক জোগান করা যেতে পারে। এ ছাড়া প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থা, ইন্ডাস্ট্রি ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এসব যৌথ গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের দক্ষ জনবলকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। যৌথ গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক সংশ্লেষ থাকবে না ধরেই কাজ করতে হবে। তবে নতুন গবেষণাগার স্থাপন, যন্ত্রপাতির জোগান, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়, ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা নিতে হবে।
রিসার্চ কাউন্সিলের কাজের ফলাফলের দ্বিতীয় সূচক হিসেবে গবেষণা ফলাফল যেমন প্রকাশনা, প্যাটেন্ট, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিকীকরণ ইত্যাদির সংখ্যাকে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। এই সূচকে ভালো করতে হলে সঠিকভাবে গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে হবে। গবেষণার বিষয় এবং ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্যে সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। এর জন্যে দরকার মাঠ পর্যায়ের ব্যবহারকারী বা সেবা গ্রহণকারীদের চাহিদার ওপরে তথ্য সংগ্রহ।
রিসার্চ কাউন্সিল অংশগ্রহণমূলক সার্ভে, সেমিনার বা কর্মশালা করে এসব চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করবে। সেই অনুযায়ী গবেষকরা গবেষণা শিরোনাম এবং সম্ভাব্য ফলাফল নির্ধারণ করবে। রিসার্চ কাউন্সিল এসব চলমান গবেষণা কার্যক্রমের নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। বর্তমানে এক বা দুজন রিভিউয়ার দ্বারা গবেষণার চলমান মূল্যায়ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে রিভিউয়ারের ভূমিকা ফলাফল পর্যালোচনায় সীমাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল নিয়ে সবার অংশগ্রহণমূলক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। এসব ইভেন্ট নিয়ে জাতীয় দৈনিকে খবর প্রকাশ করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আর্থিক জোগানদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে গবেষকদের উৎসাহ প্রদান করতে প্রকাশিত গবেষণার জন্যে আর্থিক পুরস্কার এবং সম্মাননার ব্যবস্থা করতে হবে। এর মাধ্যমেই আমাদের সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে গবেষণার মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।
