রাষ্ট্র সংস্কার ও নারী : অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কেন অপরিহার্য
মো. মোজাহিদুল ইসলাম নয়ন
প্রকাশ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৫
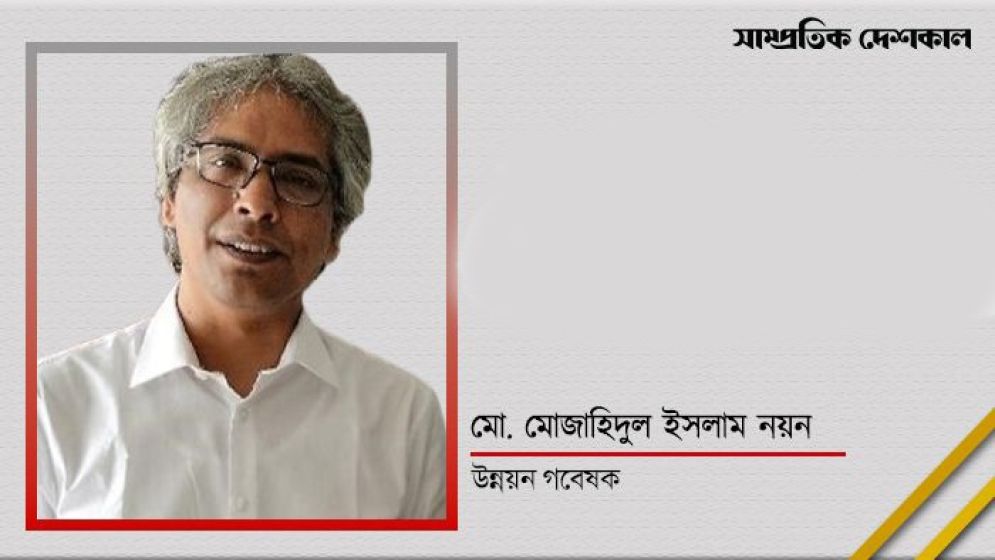
জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান কেবল একটি সরকারের পতন নয়, বরং একটি বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার গভীর আকাক্সক্ষারই প্রকাশ ছিল। এই আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য ও গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল নারীদের ব্যাপক, সক্রিয় ও সাহসী অংশগ্রহণ। শিক্ষার্থী, কর্মজীবী, এমনকি গৃহিণীরা পর্যন্ত রাজপথে নেমে বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অথচ আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও নীতিমালা পুনর্গঠনের যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল, তাতে নারীদের সেই সক্রিয় উপস্থিতি ও নেতৃত্ব প্রায় অদৃশ্যই বলা যায়। এটি শুধু হতাশাজনকই নয়, বরং গণতান্ত্রিক চেতনা ও বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক নীতির সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রকৃত অর্থ নারী-পুরুষের সমতা ও সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই কেবল হতে পারে, এর অন্যথা হওয়ার সুযোগ তো নেই।
আন্দোলনে নারীর ভূমিকা ও পরবর্তী প্রান্তিকীকরণ
কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনটি অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে রূপান্তরিত হয় বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের একটি সামগ্রিক সংগ্রামে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে শুরু করে গ্রামীণ-প্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্ত নারী শিক্ষার্থী, কর্মজীবী নারী ও সাধারণ গৃহিণীরা অসাধারণ সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে রাজপথে নেমেছিলেন। সে সময়ে যে চিত্র দেখা গেছে সেটি অকস্মাৎ কিছু নয়; বরং এটি ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন লড়াই-সংগ্রামে নারীদের ওতপ্রোত সম্পৃক্ততারই বিস্তৃত ও সাম্প্রতিক রূপ, যা এ দেশের ইতিহাসেরই এক কাক্সিক্ষত ও স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা।
কিন্তু আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে যখন ছাত্রনেতাদের স্থান হলো, তখন একই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা নারী নেতৃত্বকে একপাশে সরিয়ে রাখা হলো। বিশ্লেষকদের ধারণা, নারীনেতৃত্বকে পরিকল্পিতভাবেই আড়াল করা হয়েছে। উপরন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছাত্রীনেতৃত্বের দুঃসাহী ভূমিকার স্বীকৃতির পরিবর্তে নারীর শরীর, পোশাক নিয়ে বিদ্রুপ ও সমালোচনার ঝড় চলছে। এ প্রসঙ্গে লেখক নিশাত সুলতানা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন, এগুলো কি কেবল ভুল বা দুর্ঘটনাবশত, নাকি
ইচ্ছাকৃতভাবেই নারীদের নেতৃত্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার একটি সুপরিকল্পিত কৌশল? বাস্তবতা হলো, এটি আমাদের সমাজের গভীরে প্রোথিত পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। যেখানে নারীকে ‘অংশগ্রহণকারী’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও ‘সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী’ হিসেবে তাদের অবস্থানকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়।
সংবিধান, পারিবারিক আইন ও সিডও : একটি অমীমাংসিত ইস্যু বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে (১৯(১), ১৯(৩), ২৮(১), ২৮(২)) নারী-পুরুষের সমতা ও সকল প্রকার বৈষম্যহীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু একই সংবিধান পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইনকে স্বীকৃতি দিয়ে নারীর মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বৈষম্যকেই বরং বৈধতা দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী নারীর বিবাহ, তালাক, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারের অধিকারে নারী-পুরুষ সমতার প্রশ্নে এখনো অনেক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে, যা সংবিধানের ২৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত অঙ্গীকারের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।
এ ছাড়া বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপবিষয়ক সনদ (সিডও) অনুসমর্থন করলেও ধারা ২ এবং ধারা ১৬(১)(গ)-এ এখনো সংরক্ষণ বহাল রয়েছে। ধারা ২ রাষ্ট্রকে বৈষম্যমূলক আইন ও প্রথা বাতিল করে নারী-পুরুষের সমতার নীতি কার্যকর করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, আর ধারা ১৬(১)(প) বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে। যদিও সংবিধানের ২৭ ও ২৮ ধারায় সমতার নীতি ঘোষিত, বাস্তবে ব্যক্তিগত আইনগুলোতে বৈষম্য রয়ে গেছে; যেমন-মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১-তে তালাক, ভরণ-পোষণ ও উত্তরাধিকারে অসমতা বিদ্যমান, হিন্দু ব্যক্তিগত আইনে বিবাহবিচ্ছেদ স্বীকৃত নয় এবং সম্পত্তি বণ্টনে বৈষম্য রয়েছে, আর বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২ ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প দিলেও তা অনেক সময়ই কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয় না। ফলে নারীরা বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তি বণ্টন ও সন্তানের হেফাজতের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে সংরক্ষণ প্রত্যাহার, ব্যক্তিগত আইন সংস্কার এবং সংবিধানসম্মত সমতার নীতি বাস্তবায়ন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণ ও নারীর অধিকার সুরক্ষায় অপরিহার্য।
বাংলাদেশে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতার বাস্তবতা পূর্বের অন্যান্য বছরের ন্যায় বাংলাদেশে গত পাঁচ বছরে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পরও পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে নারীরা বহুমাত্রিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে অন্তত চার হাজার ৮২২ জন নারী বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে এক হাজার ৬৯ জন ধর্ষণের শিকার এবং ২১০ জন স্বামীর নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২২ সময়ে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা বিশেষভাবে বেড়েছে, বিশেষত কোভিড-১৯ লকডাউনের সময়, যখন নারীরা ঘরবন্দি অবস্থায় মানসিক ও শারীরিক সহিংসতার সম্মুখীন হন। ইউনিসেফের ২০২১ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার এখনো বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে, যেখানে প্রায় ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছরের আগেই। কর্মক্ষেত্রে নারীরা এখনো মজুরিবৈষম্য, যৌন হয়রানি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সীমিত অংশগ্রহণের সমস্যায় ভুগছেন, যদিও তারা গার্মেন্টস ও কৃষি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। পাশাপাশি জমি ও সম্পত্তির অধিকার, সাইবার হয়রানি এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈষম্য নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদাকে ব্যাহত করছে।
নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ২০২২ সালে ৪২.৭ শতাংশে দাঁড়ালেও এর একটি বিশাল অংশ, প্রায় ৯২ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, যেখানে কোনো ধরনের শোভন কর্মপরিবেশ বা আইনি সুরক্ষা নেই। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ অর্জনে পোশাকশিল্পে নারীর অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু ‘কোভিড-পরবর্তী সময়ে এই খাতে নারী কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতে, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে পারলে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এটি শুধু ন্যায়বিচারের প্রশ্নেই নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমান কাজে সমান মজুরি, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কার্যকর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবি।
রাজনীতিতে নারী : প্রতিনিধিত্বের তীব্র অসাম্য
জাতীয় সংসদে নারীর জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন থাকলেও এই আসনগুলো পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ হয়। ফলে নারীর প্রকৃত ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় না। সাধারণ আসনে নারীর অংশগ্রহণ এখনো অতি সীমিত। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নারীর নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিতান্তই কম।
প্রায় সব রাজনৈতিক দলই তাদের সংবিধানে ৩৩ শতাংশ নারী কোটা রাখার কথা বললেও বাস্তবে দলীয় কমিটিতে এই কোটার কোনো স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা নেই। জুলাই আন্দোলনে নারীরা তাদের নেতৃত্ব ও সংগঠন দক্ষতার অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রমাণ দিয়েছেন। এখন প্রয়োজন তাদের ‘সংকটকালীন অংশগ্রহণকারী’ নয়, বরং ‘সমান অংশীদার’ হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া। এ জন্য সংসদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দলীয় কোটাকে কার্যকর ও স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়ন করা জরুরি।
নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন : কমিশন প্রতিবেদন
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর একটি ১০ সদস্যবিশিষ্ট নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীর সমতা, অধিকার ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্য ও সহিংসতা হ্রাসে কার্যকর সুপারিশ প্রদান করা। কমিশন সরকার, স্থানীয় প্রশাসন এবং সামাজিক অংশীদারদের জন্য নীতিনির্দেশনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। কমিশন প্রতিবেদন প্রস্তুতির জন্য ৪৩টি নিয়মিত সভা ও ৩৯টি পরামর্শমূলক সভা আয়োজন করে। সভাগুলোতে নারীবাদী আন্দোলন, উন্নয়ন সংস্থা, শ্রমিক ইউনিয়ন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও পিছিয়ে পড়া জনগণের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া ৯টি যৌথ সভা অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেছে যে নারীর বাস্তব অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এবং প্রয়োজনগুলো সরাসরি প্রতিবেদনভুক্ত হয়েছে।
প্রতিবেদনটি ৪৩৩টি ঘটনার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করে এবং মূল সুপারিশগুলো তুলে ধরেছে। যদিও কমিশনের সুপারিশগুলো গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। ধর্মভিত্তিক ও প্রথাগত বিশ্বাসের কারণে কিছু রাজনৈতিক নেতা পরিবর্তনের বিরোধিতা করেন। স্থানীয় সামাজিক গোষ্ঠীগুলো বিদ্যমান কাঠামোর রক্ষণশীলতার কারণে নারীর সামাজিক নেতৃত্ব ও দৃশ্যমানতা সীমিত রাখতে চায়। স্থানীয় প্রশাসনও ক্ষমতা শেয়ারিংয়ের ভয়বোধের কারণে কার্যকর বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দৃশ্যমান ভূমিকা গ্রহণে সীমাবদ্ধতা তৈরি করছে।
সুতরাং নীতিনির্ভর সুপারিশ হলো কমিশনের সুপারিশ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা, ব্যক্তিগত আইন ও প্রথার সমতা নিশ্চিত করতে মুসলিম পরিবার আইন, হিন্দু আইন ও অন্যান্য প্রথাগত আইন সংস্কার করা, মিডিয়া, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশীদারদের সংলাপ ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় আনা। এ ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সুযোগ তৈরি করে নারীদের দৃশ্যমান নেতৃত্ব গ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এই সুপারিশগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সীমিত থাকবে এবং বাংলাদেশের লিঙ্গ সমতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন হয়ে যাবে। কমিশনের প্রতিবেদন ও সুপারিশগুলো শুধু নীতিনির্ভর নির্দেশনার জন্য নয়, বরং বাস্তবিকভাবে নারীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর একটি রোডম্যাপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন
স্বাধীনতার দীর্ঘ পাঁচ দশক পেরিয়েও বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এখনো মূলধারার রাজনৈতিক দল এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় অত্যন্ত সীমিতই রয়ে গেছে। সংবিধানের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীর অংশগ্রহণ ৩৩ শতাংশ নিশ্চিত করতে হয়, তবে বাস্তবে অনেক দল কেবল লোক দেখানোভাবে এটি পালন করে চলেছে। নির্বাচিত বা দল অন্তর্ভুক্ত নারীদের রাজনৈতিক দলের মধ্যে কার্যকর কোনো ভয়েস নেই। যারা কিছু পদ-পদবি অর্জন করেছে, প্রায়ই তা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতাসীন পুরুষ নেতাদের কৃপায় পাওয়া বলে অনেকেই মনে করেন।
সংরক্ষিত আসন প্রাপ্ত নারীর ক্ষেত্রে একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। সংসদ বা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে সংরক্ষিত আসন দেওয়া হয় অনেকাংশে তা দয়া-করুণা বা দলের অভ্যন্তরীণ প্রভাবশক্তির সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। অনেক সময়ে দেখা যায়, অর্থশালী পুরুষ এমপি দলীয় ফান্ডে বিপুল অর্থ দিয়ে সংরক্ষিত আসনে তার স্ত্রী অথবা আত্মীয়ের জন্য এমপি পদ কিনে নেন। যদিও নারীরা সংসদ বা দলের আলোচনায় অংশ নেন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বাধ্যবাধকতার কারণে তারা দলের বিপক্ষে যৌক্তিক অবস্থান নিতে বা বিরোধিতা করতে পারেন না।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা
নারীরা এখনো পরিবারের চৌহদ্দি ও পুনঃ উৎপাদনমূলক কাজে (রিপ্রোডাকটিভ) ব্যস্ত থাকেন গার্হস্থ্য কাজ, সন্তানদের যত্ন, গবাদিপশু পালন, রান্না-পরিচ্ছন্নতা, স্বামী ও বয়স্কদের সেবার কাজে। চাকরি বা ব্যবসার সঙ্গে এসব দায়িত্ব যুক্ত নারীদের ক্ষেত্রে ‘কেয়ার বারডেন’ দ্বিগুণ হয়ে যায়। সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাঠামোয় নারীর অবস্থান আরো বেশি প্রান্তিক। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও নারী শিক্ষার্থীদের সুযোগ সীমিত, সেটা যেমন খেলার মাঠ হোক আর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার বিষয় হোক। এহেন বাস্তবতায় নারীদের মধ্যে নেতৃত্ব গঠনের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে।
প্রান্তিক নারীর সীমাবদ্ধতা
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, নদীভাঙনকবলিত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আরো পিছিয়ে আছেন। সামাজিক বৈষম্য, সীমিত কর্মসংস্থান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সীমিত করে। নারীদের বিপুলসংখ্যক এখনো রাজনীতির মূলধারা থেকে বাইরে থাকলেও এর মানে এই নয় যে তারা রাজনীতিবিমুখ। উদাহরণস্বরূপ জুলাই আন্দোলনের সময় নারী শিক্ষার্থীরা সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে তাদের জন্য প্রয়োজন কার্যকর, স্থায়ী রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম।
উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ ও সীমাবদ্ধতা
এনজিওভিত্তিক উদ্যোগ যেমন উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট (ওমেন ইন ডেভেলপমেন্ট) গ্রামীণ পর্যায়ে নারীদের সংগঠন গড়ে তুলেছে, তবে তা প্রায়ই প্রকল্প নির্ভর এবং সময়সীমাবদ্ধ। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নারী সংগঠন করে ঋণ ও সঞ্চয় পরিচালনা করলেও নেতৃত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা স্থানীয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর তেমন মনোযোগ নেই। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও প্রকল্পগুলো মূলত নিজস্ব সদস্য সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে গড়ে ওঠা নারী নেতৃত্ব দীর্ঘ মেয়াদে নার্চার করা হয় না।
ন্যাশনাল ও স্থানীয় স্তরে নারীর নেতৃত্বে বিভিন্ন ফোরাম/নেটওয়ার্ক (যেমন : দুর্বার নেটওয়ার্ক, নারীপক্ষ, উইকেন, নারী শ্রমিক কেন্দ্র, আদিবাসী নারী ফোরাম) গড়ে উঠলেও প্রকল্পভিত্তিক ও সময়সীমাবদ্ধ হওয়ায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের চর্চা যথাযথভাবে করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া এনজিওগুলো আইনগতভাবে রাজনীতি বা লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে না, যা নারীর উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও নতুন রাজনৈতিক এজেন্সি
নারীদের জন্য এখন প্রয়োজন নারীর নেতৃত্বে, নারীর স্বনির্ভর রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এখানে নারীরা স্বনেতৃত্বে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান প্রণয়ন এবং নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এটি কেবল ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন নয়, বরং সমাজে নারীর রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং মূলধারার পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি গড়ে তুলবে।
এ ধরনের নতুন রাজনৈতিক এজেন্সি নারীর অধিকারের নতুন মেনিফেস্টো তৈরি করবে, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে তাদের উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়নের সুযোগ দেবে, এবং প্রচলিত রাজনীতিতে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। শিক্ষা, নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক সচেতনতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে নারীরা দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, কর্মসংস্থান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।
